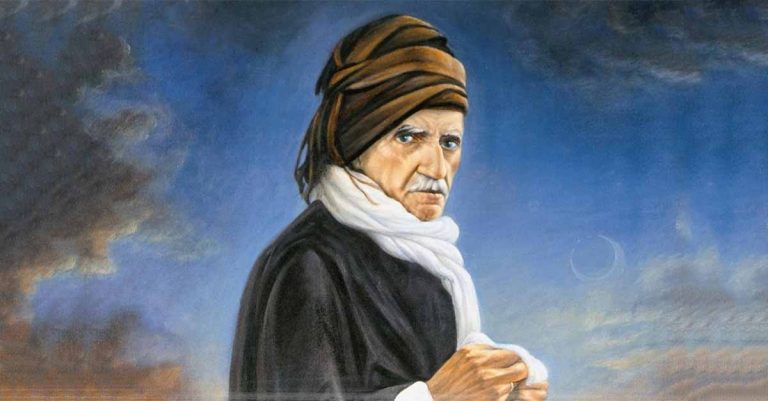আগামী দিনের ইসলাম
এডিটর’স নোট: ২০০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষার্থীদের এক প্রোগ্রামে ‘দ্যা ফিউচার অব ইসলাম’ শিরোনামে তারেক আল সোয়াইদান একটি বক্তৃতা করেন। বলা যায়, ইসলাম সম্পর্কে এটি একটি কম্প্রেহেনসিভ আলোচনা। প্রথমে তিনি বিশ্বসভ্যতাগুলোর উত্থান-পতনের কারণগুলো আলোচনা করেছেন। তারপর ইসলামের আগমন, উত্থান ও পরবর্তীতে খেলাফতের পতনের কারণ আলোচনা করেছেন। সবশেষে, আগামী দিনে ইসলাম কীভাবে পুনরায় বিশ্বসভ্যতা হিসেবে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে, তার রূপরেখা ব্যক্ত করেছেন। সিএসসিএস-এর পাঠকদের জন্য লেকচারটি ইংরেজিতে অনুলিখন ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন মো: হাবিবুর রহমান হাবীব।
*****
ভূমিকা
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍنِالنَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، وَعَلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَه، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه. وَبَعْدُ
প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
আজ রাতে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক Federation of Australian Muslim Students & Youth (FAMSY), একটি লেবানিজ সংগঠন এবং আপনারা যারা এই চমৎকার মসজিদে উপস্থিত আছেন– সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাশাআল্লাহ, অস্ট্রেলিয়ায় এত বড় মসজিদ রয়েছে, তা কল্পনাও করিনি।
চারদিন ধরে আমি অস্ট্রেলিয়ায় আছি। গত কয়েকদিন মেলবোর্নে ছিলাম, সিডনিতে আজকেই প্রথম। এটাই আমার প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। এ দেশে ইসলামী কার্যক্রম এবং ইসলামের প্রতি কমিটেড মুসলমানের সংখ্যা দেখে আমি অভিভূত, আলহামদুলিল্লাহ। আজ রাতে আপনাদের এই উপস্থিতিও তা প্রমাণ করছে।
রাসূলের (সা) একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে,
وَاللهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْلُغَ هذَا الدِّيْنُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
“আল্লাহর শপথ! ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না, যতদিন পর্যন্ত না এই দ্বীনের ব্যাপ্তি দিন ও রাতের দূরত্বে পৌছবে।”
আপনারা মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরত্বে অবস্থান করছেন। যা এতটাই দূরে যে, সেখানে যেতে একদিন এক রাত সময় লেগে যায়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরও বেশ কয়েকবার আমি সেখানে গিয়েছি। মক্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া যেদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ঠিক তার বিপরীত দিকে অবস্থিত। এমনকি হাওয়াই স্টেটে পর্যন্ত কিছু মুসলমান রয়েছেন। রাসূলের (সা) ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে।
যা হোক, আমি আগামী দিনের ইসলামের প্রকৃত অবস্থা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। বিশেষ করে, ৯/১১-র পর ইসলাম ও মুসলিমরা একটা চাপে পড়েছে। ওই ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমদেরকে এই চাপের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এসব ঘটনা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এই দ্বীনের ভবিষ্যৎ কী?
এ সম্পর্কে জানতে গিয়ে ইতিহাস নিয়ে আমি ব্যাপক গবেষণা করেছি। যদিও আমি পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর পিএইচডি করেছি। এর পাশাপাশি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছি। তবে শরীয়াহ এবং ইতিহাস হচ্ছে আমার অন্যতম পছন্দের বিষয়।
গবেষণা করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক গতিধারা আছে এবং সময়ের ব্যবধানে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ বিষয়ে আমার চিন্তাভাবনাগুলো এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।
যে কোনো সভ্যতা তার নিজস্ব ধারায় গড়ে ওঠে। প্রতিটি সভ্যতাই শুরুতে দুর্বল থাকে। তারপর বছরের পর বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এটি বিকশিত হতে থাকে। উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে সাধারণত শত শত বছর লেগে যায়।
উদাহরণ হিসেবে ইসলামের অব্যবহিত আগের পারস্য সভ্যতার কথা বলা যায়। শুরুতে তারা দুর্বল ছিল। তারপর ক্রমাগত বিকশিত হতে হতে দুই হাজার বছর পর তারা সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। বাইজেন্টাইন বা রোমান সভ্যতাকে এ পর্যায়ে পৌঁছতে সময় লেগেছে প্রায় ১২’শ বছর। খেয়াল করলে দেখা যায়, আরো অনেক সভ্যতার বিকাশ লাভের জন্য একই ধরনের সময় লেগেছে। তবে একটা সভ্যতা গড়ে উঠতে অনেক সময় লাগলেও এর পতন যে খুব দ্রুতই হয়ে থাকে, এটি অনেকেই মানতে চান না। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টাই আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো।
সমসাময়িক সভ্যতাগুলোর উপর ইসলামের বিজয়
আক্রমণের মুখে পারস্য সভ্যতা
সীমানা
পারস্য সভ্যতার উদাহরণ দিয়েই শুরু করি। আমরা জানি, বৈশ্বিক পরাশক্তি হয়ে ওঠতে তাদের দুই হাজার বছর সময় লেগেছিল। তৎকালীন বিশ্বে শুধুমাত্র রোমানরা তাদের সমকক্ষ সভ্যতা ছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড ছিল বিশাল। ভারত থেকে শুরু করে তুরস্ক, ইরাক ও আরব বিশ্বের অংশবিশেষ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। আরব উপদ্বীপের অংশবিশেষ ছিল তাদের মিত্র। ইরাকের মাদায়েন ছিল এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী।
সামরিক শক্তি
পারস্যের সেনাবাহিনী ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী। মুসলমানদের সাথে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাধারণত আড়াই, তিন কিংবা সাড়ে তিন লক্ষ। আমরা ১৪’শ বছর আগের কথা বলছি! বর্তমানকালেও এই সংখ্যাটা বিশাল! বর্তমানে বিশ্বের কয়টা সেনাবাহিনীর এত বিপুল সৈন্য আছে? তাছাড়া এটা তাদের সেনাবাহিনীর পুরোটা নয়, একটা অংশ মাত্র। কী বিশাল সেনাবাহিনী ছিল তাদের! অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সভ্যতা!
তাদের সেনারা ছিল তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তাদের ছিল সর্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধ সরঞ্জাম। তারা শুধু পারস্যের প্রযুক্তিই ব্যবহার করত না, রোমান ও ভারতীয় প্রযুক্তিও ব্যবহার করত। সমসাময়িক সব প্রযুক্তিই তাদের আয়ত্বে ছিল। আমরা বিজ্ঞান, দর্শন বা কলা – যে বিষয় নিয়েই কথা বলি না কেন, তারা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা শুধু রোমানদের সাথে তুলনীয় ছিল।
তারমানে, মুসলমানরা যখন তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে তখন তারা মোটেও দুর্বল ছিল না। তাদের মধ্যে কোনো অন্তর্কোন্দলও ছিল না। একজন মাত্র সম্রাটের অধীনে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য ছিল খুবই শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। এক কথায় পরাশক্তি।
ক্র্যাকডাউন
পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে কত সময় লেগেছিল? ১২ হিজরীতে আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খেলাফতকালে মুসলমানরা পারস্যে প্রথম অভিযান পরিচালনা করে। তিনি দুইটি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা) নেতৃত্বে একটি দল ইরাকের দক্ষিণাংশে এবং মুসান্না ইবনে হারিসার (রা) নেতৃত্বে আরেকটি দল ইরাকের উত্তরাংশে অভিযান চালায়।
উভয় সেনাদল ১২ হিজরীতে অভিযান শুরু করে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) দুর্বার গতিতে দক্ষিণ ইরাক হয়ে রাজধানী মাদায়েনের দিকে এগুতে থাকেন। মুসান্না ইবনে হারিসা (রা) খালিদের মত এগুতে পারছিলেন না। তিনি তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সামরিক দিক থেকেও তিনি খালিদের মতো সক্ষম ছিলেন না। তাই খালিদ (রা) উত্তর দিক থেকে এগুতে থাকলেও মুসান্না (রা) দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে যেতে পারছিলেন না।
অভিযান চলাকালেই আবু বকর সিদ্দিক (রা) খালিদকে (রা) ফিলিস্তিনে পাঠানোর প্রয়োজনবোধ করলেন। তাই খলিফা তাঁকে ইরাক ত্যাগ করে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে বলবো। যাইহোক, খলিফা চলমান অভিযানের নেতৃত্বের জন্যে রাসূলের (সা) চাচা সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে (রা) নিয়োগ দেন। তিনি অভিযান চালিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁর নেতৃত্বে উভয় সেনাদল একত্রিত হয় এবং বিখ্যাত কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানরা পারস্য বাহিনীর মোকাবেলা করে। কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। ১৫ হিজরীতে তারা পারস্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সক্ষম হন।
পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে মাত্র তিন বছর সময় লেগেছিল। দুই হাজার বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা একটা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে তিন বছরেরও কম সময়ে! কিন্তু কেন? কীভাবে এটি সম্ভব হয়েছিল? তারা তো দুর্বল ছিল না। তাদের ছিল শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি ও সেনাবাহিনী। রাজনৈতিকভাবে ছিল শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ। কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, কাব্য– সকল ক্ষেত্রে তারা ছিল এগিয়ে। তারা ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা সভ্যতা। তাহলে কী জন্যে তাদের পতন ঘটে? এই প্রশ্নটি সমাধানের আগে চলুন আমরা আরেকটি সভ্যতা নিয়ে কিছু কথা বলি।
রোমান সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান
বিশাল সাম্রাজ্য
রোমান সভ্যতার তৎকালীন সম্রাট ছিলেন সিজার। তারা ছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পরাশক্তি। পারস্যের সাথে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। রোমানদের তিনটি রাজধানী ছিল: সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের জন্যে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল), পূর্বাংশের জন্যে জেরুসালেম (আল কুদস) এবং উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, তুরস্ক ও আশপাশের অঞ্চলের জন্যে আলেকজান্দ্রিয়া। কী বিশাল সাম্রাজ্য!
শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব
পুরো সাম্রাজ্য ছিল একজন নেতার কর্তৃত্বে। তিনি হলেন সিজার। তিনি সাধারণত ইস্তাম্বুলে থাকতেন। তবে মাঝেমধ্যে জেরুসালেমে থেকেও সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাসূল (সা) যখন সিজারের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তখন সিজার জেরুসালেমে ছিলেন। যাইহোক, আবারো শক্তিশালী অদম্য এক সভ্যতা, বিশাল সেনাবাহিনী। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার। এটা ছিল রোমান সেনাবাহিনীর একটা অংশ মাত্র।
চিন্তা করে দেখুন, কত শক্তিশালী একটা সভ্যতা ছিল! দর্শন, কাব্য, যুক্তিবিদ্যা– এসব ক্ষেত্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। কী বিশাল সভ্যতা! পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। সামরিক, রাজনৈতিকসহ সবদিক থেকেই তারা ছিল শক্তিশালী সাম্রাজ্য।
অভিযানের শুরু
আবু বক্কর সিদ্দিকের (রা) খেলাফতকালে ১২ হিজরীতে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা সর্বপ্রথম অভিযান পরিচালনা করে। খলিফা সে অঞ্চলে চারটি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন। ফিলিস্তিন ও জর্ডান অঞ্চলে আমর ইবনুল আস (রা), সিরিয়ায় জিহাদ ইবনে আবি (রা), ফিলিস্তিন ও লেবাননে সারাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা) এবং ফিলিস্তিনের উত্তরাংশ ও সিরিয়ার বাকি অংশে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর (রা) নেতৃত্বে সেনাদল পাঠানো হয়। এই চারটি সেনাদল মিলে সৈন্য সংখ্যা ছিল মোটের উপর চৌত্রিশ হাজার। অন্যদিকে, রোমান সেনাবাহিনীর মাত্র একটি অংশের সৈন্য সংখ্যাই ছিল তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার।
যাই হোক, মুসলিম বাহিনীর আগমনের কথা জানতে পেরে সিজার তৎক্ষণাৎ জেরুসালেম ত্যাগ করে দামেস্কে পালিয়ে যান। মুসলিম বাহিনী আরো এগিয়ে গেলে তিনি দামেস্ক ছেড়ে ইস্তাম্বুলে পালিয়ে যান। এই নয়া শক্তি সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। তিনি বেশ চালাক ছিলেন। সিরিয়া ত্যাগের সময় তার স্বগোতোক্তি ছিল, ‘চির বিদায় সিরিয়া’। অর্থাৎ, তিনি জানতেন…!
মুসলিম বাহিনীর রণকৌশল
মুসলিম বাহিনী একে একে ফিলিস্তিন ও আশপাশের এলাকা জয় করতে থাকে। এ অবস্থায় সিজার তার সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠালেন। অন্যদিকে, মুসলিম বাহিনীর এক একটি দলে মাত্র আট থেকে দশ হাজার করে সৈন্য ছিল। এই অবস্থায় আবু উবাইদা (রা) চারটি সেনাদলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা একত্রিত হলো, তবে চারটি দলই স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান গ্রহণ করল।
আবু বকর সিদ্দিক (রা) বিশাল শত্রুবাহিনী আগমনের সংবাদ পেয়ে বুঝতে পারলেন অনেক বড় বিপদ আসছে। মুসলমানরা এর আগে এত বিশাল শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়নি। তাই তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে (রা) ইরাক ছেড়ে দ্রুত ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খালিদ (রা) ঝড়ের গতিতে ফিলিস্তিনের ইয়ারমুকে পৌঁছলেন।
খালিদের (রা) নেতৃত্ব
তিনি ইয়ারমুকে গিয়ে দেখতে পেলেন চারজনের নেতৃত্বে চারটি সেনাদল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান নিয়েছে। তিনি বললেন, “এভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপনাদেরকে অবশ্যই একজন সেনাপতির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।” তিনি আশংকা করছিলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা দিতে পারে। বর্তমানে মুসলমানরা যেমন সব জায়গায় নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে লিপ্ত।
এটা বুঝতে পেরে তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, “আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রতিদিন আমাদের মধ্য থেকে একজন করে নেতা হবেন।” সবাই বললো, “ঠিক আছে, তাই হবে।” এভাবে চারটি সেনাদল ঐক্যবদ্ধ হলো। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) যুদ্ধের প্রথম দিন নেতৃত্ব দেন। সবার সিদ্ধান্তক্রমে পরদিন থেকে খালিদই (রা) নেতৃত্বে বহাল থাকেন। কারণ, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না।
১৪ হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মাত্র দুই বছরের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের পতন ঘটে। মুসলিম বাহিনী বাকি অঞ্চল খুব সহজেই জয় করে। সত্যিকার অর্থে, ইয়ারমুকে তেমন বড় কোনো যুদ্ধ হয়নি। একটি মহা প্রতাপশালী সভ্যতার পতন ঘটলো মাত্র দুই বছরে। কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল?
ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় সংবাদ এলো আবু বকর সিদ্দিক (রা) ইন্তেকাল করেছেন এবং ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মদীনা থেকে তখন পারস্য এবং রোমে অভিযানরত সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন।
মিশর বিজয়
এদিকে, আমর ইবনুল আস (রা) ওমরকে (রা) একটি পরামর্শ বার্তা পাঠালেন। বার্তায় তিনি বললেন, আমাকে মিশর জয় করার অনুমতি দিন। ওমর (রা) এ নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি জবাব পাঠালেন, আপনি সেনাবাহিনী নিয়ে মিশরের দিকে অগ্রসর হতে থাকুন। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনাকে যথাসময়ে জানিয়ে দেবো। আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানদের একজন। তাই তিনি মিশরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এটা ১৮ হিজরীর ঘটনা।
মিশরে প্রবেশের পূর্বে ওমরের (রা) নির্দেশনা সংক্রান্ত চিঠি নিয়ে একজন দূত এলো। আমর ইবনুল আস (রা) এটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি দূতকে বললেন, “অপেক্ষা করুন। আমি চিঠিটি পরে নেবো।” দূত বললেন, “এ চিঠি স্বয়ং খলিফা পাঠিয়েছেন।” আমর (রা) জবাব দিলেন, “আমি জানি, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি আপনার সাথে পরে দেখা করবো।”
আমর ইবনুল আসের (রা) কৌশল ও নেতৃত্ব
আমর (রা) এগিয়ে যেতে থাকলেন। দূত তাঁর সাথে আবার দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু আমর (রা) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে মিশর সীমান্ত অতিক্রম করার পর তিনি দূতকে ডেকে বললেন, “আমাকে খলিফার চিঠিটা দিন।” তারপর তিনি খলিফার চিঠি পড়লেন। ওমর (রা) তাঁকে লিখেছেন, “আপনি মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করে থাকলে এগিয়ে যান, আর না করে থাকলে ফিরে আসুন।”
আমর ইবনুল আস (রা) তাঁকে ফিরতি চিঠিতে লিখলেন, “আমরা সীমান্ত অতিক্রম করেছি।… আমরা মিশর জয় করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার সাথে মাত্র চার হাজার সৈন্য আছে।”
চারহাজার সৈন্যের বিপরীতে চারজন!
তৎকালে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকের সংখ্যা পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। এতো আগের পরিসংখ্যান কীভাবে জানা যাবে? জিযিয়া সংক্রান্ত হিসাব থেকে এটা জানা সম্ভব। জাকাতের (ধনী মুসলিমদের জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ) পরিবর্তে অমুসলিমদেরকে জিযিয়া দিতে হয়। জিযিয়া নেয়া হয় শুধু যুদ্ধ করতে সক্ষম অমুসলিম পুরুষদের কাছ থেকে। নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা জিযিয়ার আওতার বাইরে।
আমর ইবনুল আসের (রা) কাছে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) জানতে চেয়েছিলেন, কয়জনের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। আমর (রা) জানালেন, দশ লক্ষ। অর্থাৎ তখন যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ।
আমর ইবনুল আস (রা) মাত্র চার হাজার সৈন্য নিয়ে দশ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তিনি ওমরের (রা) নিকট পত্র পাঠালেন, আমার সৈন্য সংখ্যা মাত্র চার হাজার। আমার প্রচুর সৈন্য দরকার। তখন ওমর (রা) কিছু সৈন্য পাঠালেন।
তবে ওমরের (রা) কাছে যথেষ্ট সৈন্য ছিল না। তখনো মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল অনেক কম। তাছাড়া মুসলিম বাহিনী তখন সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে মোতায়েন ছিল এবং নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে যাচ্ছিল। সেনাবাহিনী প্রায় ভারতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এই পুরো অঞ্চল ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। সব মিলিয়ে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ষাট হাজার।
তাই আমর ইবনুল আসের (রা) জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করা নিয়ে ওমর (রা) চিন্তিত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বেদুঈনসহ যাদেরকেই পেয়েছেন, তাদেরকেই একত্রিত করলেন। এরা আগে কখনো জিহাদ করেনি। তাদেরকে তিনি মিশরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর আমর ইবনুল আসকে (রা) পত্র মারফত জানালেন, আপনার জন্যে আট হাজার সৈন্য পাঠালাম।
আমার ইবনুল আস (রা) মদীনা থেকে আসা মুসলমানদের সংখ্যা গুনে দেখলেন মাত্র চার হাজার। তাই ফিরতি চিঠিতে তিনি ওমরের (রা) কাছে জানতে চাইলেন, বাকি সৈন্যরা কোথায়? আপনি তো বলেছেন আট হাজার সৈন্য পাঠিয়েছেন। ওমর (রা) জবাব দিলেন, এই চার হাজার সৈন্যের মাঝে চারজন ব্যক্তি আছেন যারা প্রত্যেকে এক হাজার সৈন্যের সমকক্ষ। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা), জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা), উবাদা ইবনুস সামিত (রা) এবং মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা)।
বর্তমানে কি আমরা এমন কাউকে দেখি, যিনি এক হাজার লোকের সমকক্ষ? এখনকার অধিকাংশ লোক একজনের সাথেই কুলিয়ে ওঠতে পারে না। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই এক হাজার লোকের সমকক্ষ ছিলেন!
ইসলামই ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি
সর্বসাকুল্যে মাত্র আট হাজার সৈন্য মিশরের মুখোমুখি হয়েছিল। মিশর তখন সুবিশাল রোমান সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। রোমান সেনাবাহিনী তখন যুদ্ধজাহাজসহ আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিল। এই বন্দরের সাথে তখন রোমান সাম্রাজ্যের মূল রাজধানী ইস্তাম্বুলের নৌপথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল। সভ্যতা, সামরিক শক্তিসহ সবদিক থেকেই তারা তখন শক্তিশালী।
তারমানে হচ্ছে, আমর ইবনুল আস (রা) কোনো দুর্বল শক্তির মোকাবেলা করেননি। মিশর জয় করে দেশটির রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করতে তাঁর কত সময় লেগেছিল? চার বছর? না, মাত্র চার মাস!
কীভাবে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হলো? যে পরাশক্তিটি ভাবতো পুরো বিশ্ব তাদের হাতে মুঠোয়, সেই সভ্যতার কী এমন হলো? তারাই তো গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতো। যে কোনো সময়, যে কোনো অঞ্চলে আক্রমণ করতো। তাদের হঠাৎ কী হলো যে, এত দ্রুত তাদের পতন ঘটলো? কেন? আপনারা অনেকে হয়ত বলবেন, তাঁরা তো রাসূলের (সা) সাহাবী ছিলেন, তাই এটা সম্ভব হয়েছে। না! শুধু এ কারণেই তাদের পতন হয়নি।
ইউরোপে মুসলিম অভিযান
এসব ঘটনার অনেক বছর পরের আরেকটি ঘটনা পর্যালোচনা করা যাক। ৯২ হিজরীতে মুসলমানরা সর্বপ্রথম স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। তখন কোনো সাহাবী ছিলেন না। এমনকি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ছিলেন একজন অনারব। তিনি যে সাহাবী ছিলেন না, তা নিশ্চিত।
৯২ হিজরীতে অভিযান শুরু করে ৯৫ হিজরীতেই তারা স্পেন ও পর্তুগাল দখল করেন এবং ফ্রান্সে আক্রমণ শুরু করেন। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মুসলমানরা প্যারিসের ষাট কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছিল।
এমন কী হলো, যাতে মাত্র তিন বছরেই এ সভ্যতার পতন ঘটলো? ফরাসিরা কেন মুসলমানদের থামাতে পারলো না? মুসলমানরা প্রায় তাদের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিল?
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা কয়েকশ বছরের ইতিহাস বলছি না। মাত্র এক কি দুই বছর, সর্বোচ্চ তিন বছরের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছি! এই অল্প সময়ে এত বড় পরিবর্তনের রহস্যটা কী?
সভ্যতার পতনের মূল কারণ
এই সবগুলো সভ্যতার পতনের পেছনে নির্দিষ্ট কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে। এগুলোর পতন হয়েছে মূলত দুটি কারণে। যে কোনো সভ্যতার পতনের ক্ষেত্রেই এই দুটি কারণ সমভাবে প্রযোজ্য।
১। নৈতিক সংকট:
প্রথম কারণটি হলো তাদের নৈতিক অধঃপতন। তাদের কোনো নীতি-নৈতিকতা ছিল না। ভেতরে ভেতরে তারা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছিল। তারা যে বস্তুবাদী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, সেখানে ছিল অবাধ যৌনাচার। এতে তাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। সবাই হয়ে পড়েছিল আত্মকেন্দ্রিক।
বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে এর বেশ মিল রয়েছে। তবে এসব সভ্যতার পতনের পেছনে শুধু এগুলোই যথেষ্ট কারণ ছিল না। তারা তো অনেক বছর ধরেই অধঃপতিত ছিল। তাই পতনের জন্যে এটাই যথেষ্ট কারণ নয়। অবশ্যই আরো কোনো কারণ রয়েছে।
২। আরো উন্নত বা শক্তিশালী সভ্যতা কর্তৃক আক্রমণ:
অন্য কারণটি হলো, এই পরিস্থিতিতে আরো উন্নত কিংবা শক্তিশালী কোনো সভ্যতা তাদেরকে আক্রমণ বা চ্যালেঞ্জ করেছে। নতুন সভ্যতাটি হয় নৈতিকতার মানদণ্ডে তাদের চেয়ে ভালো, নয়তো বস্তুগতভাবে শক্তিশালী।
এ কারণেই আমরা দেখি, মঙ্গোলিয়ানরা ইউরোপ জয় করতে পেরেছিল। তারা নৈতিকভাবে ইউরোপের চেয়ে উন্নত ছিল না। তারাও মন্দ প্রকৃতির ছিল। তবে সামরিকভাবে তারা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। এই একই ঘটনা ইতিহাসে বার বার ঘটেছে।
তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ – مَتَاعٌ قَلِيلٌ
পৃথিবীতে অবিশ্বাসীদের ক্ষমতা দেখে বেকুব বনে যেও না। তা ক্ষণস্থায়ী, বেশিদিন টিকে না। (সূরা আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭)
ইসলামী সভ্যতার গতিধারা
অন্যান্য সভ্যতা নিয়ে তো একটা ধারণা পাওয়া গেল। এবার ইসলামী সভ্যতাকে জানার চেষ্টা করা যাক।
ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হওয়া, সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো, বহিঃশক্তির চ্যালেঞ্জ এবং অতি দ্রুত পতন– বিশ্বের সকল সভ্যতাই এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। ইসলামই একমাত্র সভ্যতা, যা এর ব্যতিক্রম। আমি আপনাদের সামনে ইসলামী সভ্যতার গতিধারা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। অবশ্য এ জন্য লম্বা সময়ের প্রয়োজন। তবে আমি অল্প কথায় বিষয়টি তুলে ধরবো।
সভ্যতা ও সীমানা
ইসলামের সূচনা হয় মক্কা থেকে। সভ্যতা সংক্রান্ত প্রথাগত বিবেচনায়, কোনো একটি দেশ শাসনের মাধ্যমে সাধারণত সভ্যতার সূচনা হয়। শাসন করার মতো কোনো দেশ বা অঞ্চল ছাড়া কোনো পরিপূর্ণ সভ্যতা হতে পারে না। তত্ত্ব, পদ্ধতি এবং আদর্শ থাকা সত্ত্বেও এগুলো কোনো অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা পর্যন্ত তা পরিপূর্ণ সভ্যতা হিসেবে গণ্য হবে না।
কনসেপ্টের গুরুত্ব
মক্কায় ইসলামের প্রথম ১৩ বছর ছিল মুসলমানদের আদর্শ, ঈমান ও নৈতিকতা গঠনের সময়। ফলে এই সময়ে ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, বিচার ব্যবস্থা কিংবা অন্য কিছুই ছিল না। এমনকি নামাজ ছাড়া অন্য কোনো ইবাদতও ছিল না। রোজা, জাকাত, হজ্জ ইত্যাদি সবকিছুই মদীনা থেকে শুরু হয়। মক্কী জীবন ছিল আদর্শ ও নৈতিকতা (ঈমান ও আখলাক) গঠনের সময়।
ইসলামী সভ্যতার সূচনা
মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার সূচনা হয়। ওমর (রা) কর্তৃক হিজরতের বছরকে ইসলামী ক্যালেন্ডারের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করা তাই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ হিজরত ছিল ইসলামী সভ্যতার সূচনা। একই সাথে এটি একটি রাষ্ট্রের সূচনাও বটে।
কোরআন নাজিলের বিষয়বস্তুগত ভিন্নতা
তারপর সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেলো। এমনকি কোরআনও! মক্কী সূরাগুলো পড়লে বুঝা যায়, এগুলোর বিষয়বস্তু মাদানী সূরাগুলো থেকে আলাদা। মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পর কোরআনের বিষয়বস্তু পর্যন্ত পাল্টে গেছে। তাই হিজরতের বছর হলো এমন একটা সময়, যেখান থেকে আমরা ইসলামী সভ্যতার আলোচনা শুরু করতে পারি।
মদীনায় নগর রাষ্ট্রের পত্তন
সেই ইসলামী রাষ্ট্রটি কত বড় ছিল? আয়তনে প্রায় সিডনি শহরের মতোই একটি ছোট শহর, যার নাম ছিল ইয়াসরিব। পরবর্তীতে ‘মদীনা মোনাওয়ারা’ হিসেবে এর নামকরণ করা হয়। খুবই ছোট একটি নগর রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ নাগরিক ছিল না। বড় জোর হাজার ত্রিশেক মানুষ বাস করতো। মুসলিম, ইহুদী, মুশরেক এবং অন্যান্যরা মিলে ছিল জনসংখ্যার এই পরিমাণ।
ইতিহাসের পট পরিবর্তন হচ্ছিল খুব দ্রুত। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই ফাঁকে আপনাদের জানিয়ে রাখি, ‘আস-সীরাহ আন-নবুবিয়্যাহ’ গ্রন্থে আমি বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি।
ইসলামের যুদ্ধসমূহ
বদর যুদ্ধ
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন’শ চৌদ্দ জন। আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল নয়’শ পঞ্চাশ জন। এ যুদ্ধে কাফেরদের ছিল দু’শ ঘোড়া। অন্যদিকে মুসলমানদের ছিল মাত্র দুইটি ঘোড়া। অর্থাৎ সংখ্যা, শক্তি ইত্যাদিতে আমরা তাদের চেয়ে বেশি ছিলাম না। সাড়ে নয়শ মানুষের বিরুদ্ধে তিনশ মানুষের এই যুদ্ধও খুব সংক্ষিপ্ত ছিল।
যে কোনো বিবেচনায় এই যুদ্ধ এখন পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ। আপনারা কি জানেন, যুদ্ধটি কত সময় ধরে স্থায়ী ছিল? মাত্র দুই ঘণ্টা! জ্বি, দুই দিন নয়, মাত্র দুই ঘণ্টা!
ইবনে আসেমের গল্প
একজন কাফের বদর যুদ্ধ দেখতে পাহাড়ের চূড়ায় বসেছিল। তিনি কোরাইশ কিংবা মুসলিম– কোনো পক্ষেই ছিলেন না। তাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি লাইভ সিনেমা দেখার মতোই তা উপভোগ করছিলেন। তার নাম ইবনে আসেম।
ঘণ্টা দুই পর হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল! ইন্ডিয়ান সিনেমা কিংবা যে কোনো লম্বা সিনেমায় যেমন অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে, এ যুদ্ধও তেমন হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু এ যেন মাত্র ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি। এ দেখে তিনি তখন স্বগতোক্তি করলেন– “হায় আল্লাহ! এমন ঘটনা তো আমি জীবনেও দেখিনি, তারা (কাফেররা) নারীদের মতো পালিয়ে গেলো!”
পাঁচ বছর পরের ঘটনা। এই ব্যক্তি মদীনায় আসলেন। তখনো তিনি অমুসলিম ছিলেন। রাসূল (সা) তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইবনে আসেম? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বদরের যুদ্ধ দেখোনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখেছি। রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তুমি কী বলেছিলে? তিনি বললেন, কিছুই তো বলিনি। রাসূল (সা) তখন বললেন, তুমি কি মনে মনে এ কথা বলোনি, “হায় আল্লাহ! এমন ঘটনা তো আমি জীবনেও দেখিনি, তারা (কাফেররা) নারীদের মতো পালিয়ে গেলো”? এ কথা শুনে ইবনে আসেম সাথে সাথে ঘোষণা করলেন– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। তারপর মনে মনে বললেন, এই কথাগুলো তো আমি কখনো কাউকে বলিনি!
এটাই হচ্ছে নবুওয়াতের শক্তি।
ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ
বদর যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দি হয়েছিল। মাত্র ৭০ জন! অথচ এখন বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলায় এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ নিহত হয়। এটি ছিল ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। নগণ্য সৈন্য সংখ্যা, ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ, সংকীর্ণ যুদ্ধ ময়দান, এমনকি এর ফলে মক্কা বিজয়ও সাধিত হয়নি; তারপরেও এর তাৎপর্য এত বেশি কেন? আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে কোরআনে বলেছেন,
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
এটি হলো হক ও বাতিলের মীমাংসার দিন এবং একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার দিন। (সূরা আনফাল: ৪১)
এক তরুণ মুসলিম যোদ্ধার মন্তব্য
মদীনার একজন তরুণের মন্তব্য থেকে এ বিষয়টি আমরা সহজে বুঝতে পারবো। তিনি ছিলেন আনসার এবং মুসলিম বাহিনীর সদস্য। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর তার পরিবার তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, “তোমরা কেন আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছো? আমরা তো কিছু জীর্ণ নিষ্প্রাণ মানুষের মোকাবেলা করেছি মাত্র। ভেড়া জবাইয়ের মতো করে তাদেরকে হত্যা করেছি।”
তার কথার মর্মার্থ হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এটা কোনো কঠিন যুদ্ধ ছিল না। তখন রাসূল (সা) কথাগুলো শুনে তাকে শুধরে দিলেন, “ভাতিজা! এমন করে বলো না। আমরা তো তাদের নেতৃবৃন্দকেই হত্যা করেছি।”
মাত্র দুইজন কোরাইশ নেতা জীবিত ছিল
বদরের যুদ্ধে মাত্র দুইজন কোরাইশ নেতা বেঁচে গিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন আবু সুফিয়ান। তিনি কাফেলা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অপরজন রাসূলের (সা) চাচা আবু লাহাব। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। পরাজয়ের খবর শুনে আবু লাহাব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়েছিলেন। এর মাত্র তিনদিন পর তিনি মারা যান। সুতরাং বাকি থাকল একমাত্র আবু সুফিয়ান।
একটি দেশ হঠাৎ করে তার সকল শাসককে হারালো এবং সকল সংসদ সদস্য এক ধাক্কায় নিহত হয়ে গেলো– এমনটা কল্পনা করা যায়! বদর যুদ্ধে ঠিক এ ব্যাপারটিই ঘটেছিল।
উহুদ যুদ্ধ
বদর যুদ্ধের ফলে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কুরাইশরা বুঝতে পেরেছিল এই পরাজয় তাদের জন্যে মহাবিপদের কারণ। তাই তারা সৈন্য সংগ্রহ শুরু করল এবং অন্যান্য আরবদের সাহায্য নিতে থাকল। এভাবে তারা উহুদ যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়। তৃতীয় হিজরীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা এতে পরাজিত হয়।
শক্তিমত্তা নয়, আনুগত্যই মূলকথা
এ পরাজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বুঝাতে চাইলেন, যুদ্ধ জয়ের জন্যে শক্তিমত্তা চূড়ান্ত নিয়ামক নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যই হলো মূল ব্যাপার। অর্থাৎ, উহুদের প্রান্তরে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে তোমরা পরাজিত হয়েছো। যখন তোমরা সঠিক পথে থাকবে, তখন আর পরাজিত হবে না।
আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ
হিজরী পঞ্চম সাল। ইহুদী, বনু গাতফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর সহায়তা নিয়ে কোরাইশরা একটি শক্তিশালী যৌথ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আহযাব অর্থ যৌথ বা সম্মিলিত। এই যৌথ বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার জন্য এগুতে থাকে। দশ হাজার আরব সৈন্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী! ওই অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে এটা ছিল ব্যাপক শক্তিশালী একটি বাহিনী।
রাসূল (সা) অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। মদীনাকে রক্ষা করতে শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা হলো। এই কারণে আহযাবের যুদ্ধকে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধও বলা হয়।
কোরাইশরা এক মাস ধরে মুসলমানদের অবরোধ করে রেখেছিল। মদীনার পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা ছিল রুক্ষ পাথুরে অঞ্চল। ফলে শত্রুবাহিনী সেদিকে যেতে পারেনি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ছিল পাহাড়-পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত। উত্তর দিকে খনন করা হয় পরিখা। আর দক্ষিণ-পূর্ব দিক সুরক্ষিত রাখতে রাসূল (সা) ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যার সাথে চুক্তি করেন।
ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা
যুদ্ধকালীন সময়ে ইহুদীরা যথারীতি চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা গোপনে কাফেরদেরকে সহায়তা করতে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির অংশ হিসেবে দক্ষিণ দিক থেকে তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মুসলমানরা যখন উত্তরে দশ হাজার সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনীকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, ঠিক তখনই মদীনার অভ্যন্তরে মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর আক্রমণ করতে ইহুদীরা উদ্যত হয়। সেখানে তখন কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। কী ভয়ানক ব্যাপার! আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–
إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّـهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
যখন তারা তোমাদের উচ্চ ও নিম্ন অঞ্চল থেকে তোমাদের উপর চড়াও হতে আসছিল, যখন ভয়ে তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং (আল্লাহর সাহায্যের বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকম বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে। সেই (কঠিন) সময়ে মুমিনদেরকে চরমভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। (সূরা আহযাব: ১০-১১)
প্রচণ্ড ভীতিকর পরিস্থিতি
বর্তমানে অনেক মুসলমান এ রকম প্রচণ্ড ভয়ে থাকে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানাচ্ছেন, ভয়ে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল! এটা হচ্ছে প্রচণ্ড ভীতির একটা একটা উদাহরণ। এটা ছিল পরীক্ষা।
যারা খুব বেশি ভয় পায় তারা মসজিদ, ইসলামী কার্যক্রম ও সংগঠন থেকে দূরে থাকতে চায়। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন বা অন্য কোনো কারণে তারা এমন আতঙ্কিত থাকে, যেন তাকে এখুনি ধরে ফেলবে!
আপনারা কি জানেন, ভয়ে রাসূলকে (সা) ছেড়ে চলে যাওয়া লোকের সংখ্যা কত ছিল? মাত্র তিন’শ জন রাসূলের (সা) সাথে ছিল। বাকি সবাই পালিয়ে যায়। তারপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা একদল ফেরেশতা ও ঝড়ো বাতাস পাঠালেন। এতে কাফেরদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং তারা পালিয়ে গেল।
এর পর পরই রাসূল (সা) ইহুদীদের বিরুদ্ধে বনু কোরায়যার যুদ্ধ পরিচালনা করলেন এবং প্রায় সাত’শ বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করলেন। তারপর মদীনা থেকে অবশিষ্ট ইহুদীদেরকে চিরদিনের মতো বিতাড়িত করা হয়। তারা খাইবারে চলে যায়। এটা ছিল হিজরী পঞ্চম সালের ঘটনা।
ইসলামী সভ্যতার অনন্যতা
তখন পর্যন্ত ইসলাম কি কোনো শক্তিশালী সভ্যতা ছিল? না। বিজ্ঞান ও গণিতে অগ্রগতি? না। অট্টালিকা? না। মসজিদ? খুবই সাধারণ একটি মসজিদ ছিল, যার কোনো কার্পেট ছিল না, চালার নিচে কোনো সিলিং ছিল না। শুধু কিছু খেজুর পাতা ছাউনি হিসেবে বিছানো ছিল। বৃষ্টি হলে স্বয়ং রাসূল (সা) কর্দমাক্ত মাটিতেই সিজদা করতেন।
বস্তুগত দিক থেকে একে কোনো বিশাল সভ্যতা বলা যায় কি? মোটেও না। কোনো শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল? না। কোনো যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল? না। তাহলে সেই সভ্যতা কোন শক্তিবলে গোটা পৃথিবী জয় করতে পেরেছে? ভাবতে থাকুন, ভাই ও বোনেরা, ভাবতে থাকুন।
খাইবার যুদ্ধ
সপ্তম হিজরীতে রাসূল (সা) জানতে পারলেন, ইহুদীরা খাইবারে আরেকটি সম্মিলিত বাহিনীর সমাবেশ করতে যাচ্ছে। এ খবর শুনে রাসূল (সা) তখুনি খাইবার আক্রমণ করলেন এবং দখল করে নিলেন। এর মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে ইহুদী অবস্থানের অবসান ঘটে। স্মরণ রাখা দরকার, তারপরও ইহুদীরা রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে।
খাইবার যুদ্ধ শেষে (ইহুদীদের শহর ত্যাগের পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছিল– অনুবাদক) একজন ইহুদী মহিলা রাসূলের (সা) কাছে কিছু খাবার নিয়ে আসে। রাসূল (সা) তার পরিবারকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অবশ্য খাইবারের সবাইকেই তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের কাউকে হত্যা করা হয়নি। অথচ ইহুদীরা বর্তমানে আমাদের সাথে তার বিপরীত আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা) অনেক শান্তিপ্রিয় ছিলেন।
যাইহোক, মহিলাটি রাসূলের (সা) প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কিছু ভেড়ার মাংস নিয়ে আসলো। এই মাংসের সাথে মেশানো ছিল বিষ! রাসূল (সা) ও সাহাবীরা খাওয়া শুরু করলেন। বিশর নামে একজন সাহাবী খাওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (সা) একটু মাংস খেয়ে থেমে গেলেন। উপস্থিত সকলকে বললেন, থামো! খেয়ো না। এই রান্না করা মাংস জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটা বিষাক্ত। কিন্তু বিশর ততক্ষণে খেয়ে ফেলেছেন। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (সা) পরবর্তীতে বলেছেন,
مَا زِلْتُ أَجِدُ مِن أَكْلَةِ الشَّاةِ فِيْ خَيْبَرَ حَتَّى قَطَعَتْ الْأَبْهَرَ مِنِّىْ
খাইবারের আক্রান্ত বিষক্রিয়ার ব্যথা আমাকে জীবনভর বইতে হবে, যতদিন পর্যন্ত না আমার শিরা-উপশিরাগুলো থেমে যাবে।
ইমাম ইবনুল কাইয়ুম বলেছেন, ওই বিষক্রিয়ার কারণেই রাসূল (সা) ইন্তেকাল করেছেন। তাই তিনি একজন শহীদ। কোনো যুদ্ধে আহত হয়ে কেউ দশ বছর পরেও সেই আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করলে তিনি যে শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন, এ ব্যাপারে সমস্ত স্কলারের ঐক্যমত্য রয়েছে। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইবনুল কাইয়ুম বলেছেন, কারা আপনার রাসূলকে (সা) হত্যা করেছিল, সে কথা কখনো ভুলে যাবেন না।
মক্কা বিজয় এবং হোনায়েনের যুদ্ধ
অষ্টম হিজরীতে মুসলমানরা মক্কা জয় করেন। মক্কা বিজয়ের সেই মহান অভিযানের পর পর হাওয়াজিন গোত্র রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র। এমনকি কোরাইশদের থেকেও শক্তিশালী। ইতিহাসে এটি হোনায়েনের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। মক্কা বিজয়ের দুই মাস পর তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। হাওয়াজিন গোত্র সে যুদ্ধ পর্যন্তও অপেক্ষা করেনি। তায়েফবাসীর সহযোগিতায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাওয়াজিনদের যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানরা প্রায় পরাজিত হয়ে পড়ে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন –
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا
এবং হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। (সূরা তওবা: ২৫)
হোনায়েনের যুদ্ধেই মুসলমানরা প্রথমবারের মতো শত্রুবাহিনী থেকে সংখ্যায় বেশি ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছিল। কারণ তারা ভাবছিল– আমরা যখন সংখ্যায় খুব নগণ্য ছিলাম তখনই কাফেরদের পরাজিত করেছি। আর এখন তো আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সুতরাং আমরাই বিজয়ী হবো।
অথচ মুসলমানরা কখনো সংখ্যাধিক্য বা শক্তিশালী সেনাবাহিনীর জোরে কাফেরদের পরাজিত করেনি। বরং আল্লাহর সৈনিক হওয়ার কারণেই তাদেরকে পরাজিত করতে পেরেছিল। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যই ছিল আসল ব্যাপার।
যাই হোক, হোনায়েনের যুদ্ধের প্রতিকূল মুহূর্তে মাত্র শ’খানেক সাহাবী রাসূলের (সা) সাথে ছিলেন। মাত্র শ’খানেক! এই ক্ষুদ্র দল নিয়েই মহানবী (সা) ১০ হাজার হাওয়াজিন সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এমতাবস্থায় পালিয়ে যাওয়া লোকেরা জানতে পারলো– রাসূল (সা) তখনো যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেননি। এ খবর পেয়ে তারা ফিরে আসতে শুরু করল। তবে তারা ফিরে আসার আগেই একশ জনের ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ১০ হাজার কাফের সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনা হচ্ছে,
وَاللهِ مَا وَصَلَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَجْمَعُوْنَ الْغَنَائِمَ
আমরা পৌঁছার আগেই দেখি মুসলমানরা গণিমতের মাল সংগ্রহ করছে।
খেয়াল করে দেখুন, কোথায় আমাদের শক্তির উৎস! যাই হোক, নবম হিজরীতে আরবরা দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।
তাবুক যুদ্ধ
দশম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোহাম্মদের (সা) নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো মুসলমানরা রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। শুধু আরবই নয়, গোটা বিশ্বের জন্যেই এটি ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা।
মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে সিজার জানতে পারলেন। এ বাহিনীর নেতৃত্বে যে স্বয়ং মহানবী (সা) রয়েছেন, তাও তিনি জেনেছেন। সিজার একজন যাজকও ছিলেন। ফলে তিনি আসমানী কিতাবগুলো সম্পর্কে জানতেন। তিনি দরবার আহ্বান করে সভাষদবর্গকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি আমার উপদেশ গ্রহণ করবে?
তারা বললো– আপনি আমাদের নেতা, আমাদের ধর্মযাজক এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। দয়া করে বলুন, আমাদের জন্য আপনার কী উপদেশ।
তিনি বললেন– চলো আমরা ইসলাম গ্রহণ করি। কারণ এই ধর্ম গোটা বিশ্ব জয় করবে। এই ব্যক্তি একজন নবী। পবিত্র গ্রন্থেও তা বলা আছে।
তারা বললো– না। আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করবো না।
তখন তিনি বললেন– যদি তা না করো, তাহলে আমার আরেকটি উপদেশ শোনো।
তারা জানতে চাইল– কী আপনার উপদেশ?
তিনি বললেন– তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ো না। সেক্ষেত্রে তিনি তোমাদের হত্যা করবেন। তোমাদের সেনাবাহিনী যত বড়ই হোক না কেন, তা কোনো ব্যাপার নয়।
তারা বলল– ঠিক আছে, আপনার এই উপদেশ আমরা মেনে চলবো।
এ কারণে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হওয়াকে রোমান বাহিনী এড়িয়ে চললো। মুসলিম বাহিনী তাবুক প্রান্তরে রোমান বাহিনীর জন্য এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। কিন্তু তারা আসেনি।
আকস্মিক আমূল পরিবর্তন, নাকি ধারাবাহিক পরিবর্তন?
পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম ছিল মদীনায় সীমাবদ্ধ একটি ছোট্ট সভ্যতা। আমি আপনাদের বলেছিলাম, সেখানে সভ্যতার কোনো নিদর্শন ছিল না। ছিল না কোনো অট্টালিকা ইত্যাদি ইত্যাদি।
অথচ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে দশম হিজরীর মধ্যে মুসলমানরা পুরো আরব জয় করে ফেললেন। তারপর রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা শুরু করলে, মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়া থেকে রোমানরা নিজেদের এড়িয়ে চলে। ইসলাম কীভাবে এত প্রভাবশালী হয়ে উঠলো? এটা কি কোনো ধারাবাহিক অগ্রগতি, নাকি দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো? গভীর অন্তদৃষ্টি দিয়ে এসব নিয়ে ভাবুন।
ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
একাদশ হিজরীর শুরুতে রাসূল (সা) ইন্তেকাল করলেন। তারপর আরবরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকল। আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রা) মতো দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষও এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি বললেন, কীভাবে আপনি সমগ্র আরবের মোকাবেলা করবেন!
মদীনা, মক্কা ও তায়েফ– মাত্র এই তিনটি শহর মুসলমানদের সাথে ছিল। এরমধ্যে মক্কা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছিল। তায়েফ নগরী মাত্র কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই প্রকৃতপক্ষে মদীনা ছাড়া অন্য কারো উপর আস্থা রাখা সম্ভব ছিল না। এভাবে সবাই ত্যাগ করায় ইসলাম আবার মদীনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো।
আবু বকর সিদ্দিক (রা) ঘোষণা করলেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। এমনকি আমাকে সবাই ছেড়ে চলে গেলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো। তখনো সমগ্র আরব জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তিনি তাদেরকে মদীনায় আসতে আহ্বাবান জানালেন। যখনই কয়েক’শ মুসলমান সংগঠিত হতেন, তখনই তিনি তাদেরকে কোনো একটি গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠিয়ে দিতেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ১২টি সেনাদল গঠন করলেন। তবে এগুলো কোনো বিশাল সেনাদল ছিল না। এই সেনাদলগুলোর সম্মিলিত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজার। অর্থাৎ কোনো কোনো সেনাদলে এক হাজারেরও কম সেনা ছিল। এই ক্ষুদ্র দলগুলোই সমগ্র আরবের মোকাবেলা করেছে। কিছু কিছু সেনাদলকে তো প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছে।
ইয়ামামার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)। এ যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। অন্যদিকে মুসাইলামা কাজ্জাবের ছিল এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী।
মাত্র এক বছরের মাঝে সমগ্র আরব আবার ইসলামে ফিরে আসে। বিশ্ব ইতিহাসে আর কোথায় কি এমনটা ঘটেছে? পতনের মাত্র এক বছরের মাঝে একটি সভ্যতা আবার দাঁড়িয়ে গেছে, এমন কোনো নজির কি ইতিহাসে আর একটা আছে?
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা যা নিয়ে কথা বলছি তা অনন্য ও ব্যতিক্রম একটা বিষয়। তা হলো ইসলাম। এটা কোনো সাধারণ জীবনব্যবস্থা, সেনাবাহিনী কিংবা মামুলি কোনো সভ্যতা নয়। এটা হচ্ছে ইসলাম।
ইউরোপ অভিযান
তারপরের বছর অর্থাৎ দ্বাদশ হিজরীতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতির বিরুদ্ধে মুসলমানরা অভিযান শুরু করে। ব্যাপারটা যেন এমন– দুই বছরের ব্যবধানে মদীনার মতো ছোট একটি শহর মস্কো এবং ওয়াশিংটনকে আক্রমণ করছে। আমরা যে ঘটনা নিয়ে কথা বলছি, তা ঠিক এমনই। এটাই বাস্তব ইতিহাস। সবাই এগুলো জানে।
হিজরী ১২ সালে মুসলমানরা অভিযান শুরু করে। ১৪ হিজরীতে পারস্যের পতন হয়। ১৫ হিজরীতে রোমানদের পতন ঘটে। এভাবে ৯২ হিজরীতে স্পেন মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। ৯৫ হিজরীতে মুসলমানরা ফ্রান্সের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।
ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনাকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন আব্দুর রহমান আল গাফেকী। তিনি একটি বিস্ময়কর পরিকল্পনা করেছিলেন। খুব কম লোকই এ সম্পর্কে জানে। আমার লেখা ‘তারিখুল আন্দালুসিয়া’ (আন্দালুসিয়ার ইতিহাস) বইয়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।
যাই হোক, মুসলমানরা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে ইউরোপের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হতে চাইলে কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। দুই’শ বছরেও তারা ইস্তাম্বুল জয় করতে পারেনি। ফলে মুসলমানরা উত্তরে ইউরোপের দিকে এগিয়ে যেতে পারছিল না। এই অবস্থায় আব্দুর রহমান আল গাফেকী বললেন, আমি পশ্চিম দিক দিয়ে ইস্তাম্বুলে আক্রমণ চালাবো। পশ্চিম তথা স্পেন, ফ্রান্স– এসব অঞ্চল দিয়ে ঢুকে আমি ইউরোপ জয় করবো।
ইউরোপ অভিযান স্থগিত
আল গাফেকী অগ্রসর হতে থাকলেন। কিন্তু তৎকালীন উমাইয়া খলিফা তাকে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন। কারণ তিনি মাত্র দুই হাজার চার’শ সৈন্য নিয়ে ইউরোপ অভিযানে যাচ্ছিলেন। যেখানে সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা ৭০ লাখের কম নয়। তাই খলিফা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এটা করতে যাবেন না। এটা খুবই বিপজ্জনক কাজ।’ তবে আমার মনে হয়, তাকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিলে ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখতে হতো।
যাই হোক, এক’শ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কোন জাতির অধীনে সবচেয়ে বেশি অঞ্চলের কর্তৃত্ব ছিল? সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনী কার ছিল? বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় কারা অগ্রগামী ছিল? দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, কাব্যসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কারা এগিয়ে ছিল? শ্রেষ্ঠ সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল?
এসব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– মুসলমানগণ।
মুসলিম সভ্যতার উত্থান-পতন
রোমান, পারস্য ও স্প্যানিশ সভ্যতা নিয়ে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে এসব সভ্যতার শত শত বছর লেগে গিয়েছিল। অথচ মুসলমানদের লেগেছে একশ বছরেরও কম।
সময় থাকলে আরো বিস্তারিত বলা যেতো। কিন্তু সময় খুব কম থাকায় সংক্ষেপে বলে যাওয়ার চেষ্টা করবো
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ
যাই হোক, ইসলাম ক্রমান্বয়ে সাফল্যের দিকে যেতে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়ে। সভ্যতাও আরো বৃহৎ পরিসরে গড়ে ওঠতে থাকে। ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগ চলছিল, মুসলমানরা তখন ছিল যথেষ্ট সৃজনশীল। চিকিৎসাশাস্ত্রে তারা নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। মুসলমানরা ছাড়া সত্যিকার অর্থে চিকিৎসাশাস্ত্রের সূচনাও হয়নি। গণিতেও আমাদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। শূন্য (০) সংখ্যাটি উদ্ভাবনের ফলে গোটা বিশ্বই হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানরা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। যতদিন তারা জিহাদ অব্যাহত রাখে ততদিন পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।
সামাজিক অবক্ষয়
কিন্তু এক সময় তারা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুসলিম শাসকেরা দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দাসী, গানবাজনা, বিভিন্ন ধরনের খাবার-দাবার নিয়ে তারা মত্ত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ তো একটা মুকুটের পেছনেই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত ব্যয় করত।
তারা ছিল যথেষ্ট ধনী এবং ক্ষমতাবান। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ ছিল না। তাদের ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা। এক পর্যায়ে তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার পরিবর্তে আয়েশী জীবন বেছে নিলো। তারা কর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।
জিহাদ নিয়ে একটি গল্প
ইসলামের শত্রুরা মুসলিম অঞ্চলের এসব পরিস্থিতির খোঁজ-খবর রাখতো। তাদের নজরদারি নিয়ে স্পেনের একটি গল্প বলি। তৎকালীন স্পেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্স ছিল মুসলমানদের দখলে। ফ্রান্স তখনো শক্তিশালী ছিল। স্পেন ফিরে পাওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তাই মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনার লক্ষ্যে ফরাসি নেতৃবৃন্দ স্পেনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গুপ্তচর পাঠাতো। তারা পাহাড় পেরিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে আসা-যাওয়া করতো। এভাবে মুসলমানদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতো। গল্পটা ছিল এ রকম–
ফরাসি নেতৃবৃন্দ কয়েকজন গুপ্তচর পাঠালেন। তারা সীমান্ত পেরিয়ে দেখলো, ১৬ বছরের একটি ছেলে কাঁদছে। একেবারে মেয়েদের মতো কান্না। তারা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, তুমি কাঁদছো কেন? ছেলেটি বললো, কোরআনের হাফেজ না হওয়া পর্যন্ত আমার মা আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে দিচ্ছেন না। কিন্তু আমি এখনই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই। আমি এখনই জিহাদ করতে চাই।
খেয়াল করেছেন! ইন্টারনেট একসেস পাওয়া, বা একটি দামি গাড়ির জন্য কিন্তু তারা কাঁদতো না!
যা হোক, গুপ্তচররা ফিরে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দকে এ ঘটনা জানালো। সব শুনে তাদের সম্রাট বললেন, এ রকম একটি মরণপণ জাতিকে আক্রমণ করা যায় না।
ত্রিশ বছর পর আরেকজন গুপ্তচরকে পাঠানো হলো। সীমানা পেরিয়ে সে দেখতে পেলো ১৬ বছরের একটি ছেলে কাঁদছে। সে জিজ্ঞেস করলা, বাবা, তুমি কাঁদছো কেন? ছেলেটি জবাব দিলো, আমার মা আমাকে একটি দাসী কেনার অনুমতি দিচ্ছেন না। সব শুনে তাদের নেতৃবৃন্দ বললো, হ্যাঁ, এবার আমরা আক্রমণ করতে পারি। তারপর তারা ঠিকই আক্রমণ চালিয়ে স্পেনের উত্তরাঞ্চল দখল করে নিলো।
এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, কম বয়সী ছেলেমেয়েরা কীভাবে বেড়ে ওঠছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারা কিসে আকৃষ্ট হয়, তাদের মন কিসে আচ্ছন্ন– এসবের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের ইসলাম। বৃদ্ধরা নয়, বরং এখনকার তরুণ প্রজন্ম, অর্থাৎ, আমাদের সন্তানদের আগ্রহ কোনদিকে, তারা কী নিয়ে ভাবে, তাদের জীবনের লক্ষ্য কী, তাদের উচ্চাকাঙ্খা কি নারী ও মেয়ে নাকি জিহাদ ও কোরআন– এসবই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে।
ক্রুসেডের মহড়া
ক্রুসেডাররা যখন দেখলো মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে, দুনিয়াবি বিষয়-আশয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তারা জেরুসালেম পুনর্দখলের জন্য ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করল। সাতটি দেশ সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানি– এই তিন দেশের তিন রাজা স্বয়ং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন।
ফিলিস্তিন দখলের জন্য ইউরোপ থেকে কত সংখ্যক সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, তা জানেন? জেরুসালেম দখলের জন্য পাঁচ লক্ষ সেনা পাঠানো হয়েছিল। শহরের উত্তর দিক ও সমুদ্র পথে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। এবং তারা জয়লাভ করেছিল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। আমার লেখা ‘তারিখ আল-কুদ্স ওয়া ফিলিস্তিন’ (জেরুসালেম ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস) শিরোনামের গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি।
আনতাকিয়ার ট্রাজেডি
আমরা কেন পরাজিত হয়েছিলাম, সে বিষয়ে ছোট্ট একটি ঘটনা বলি। জার্মান সেনাবাহিনী তুরস্ক এবং সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল হয়ে আনতাকিয়া শহরে পৌঁছে যায়। আনতাকিয়া চারদিক থেকেই স্থলবেষ্টিত একটি শহর। মাত্র একদিকে (নদী পথে) সাগরের সাথে শহরটির সংযোগ রয়েছে।
তখনো শহরটির পতন হয়নি। আর আনতাকিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারলে জার্মান বাহিনীর পক্ষে জেরুসালেম দখল করা সম্ভব নয়। কারণ, আনতাকিয়ার উপর দিয়েই জেরুসালেম যেতে হয়। আনতাকিয়ার মুসলমানরা ছয় মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তাদের অর্থ, খাদ্য এবং অস্ত্রের খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেউ তাদের কাছে এসব সাহায্য নিয়ে যায়নি।
তখন আনতাকিয়ার কাছাকাছি মুসলমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী অঞ্চল ছিল মিশর। তাই আনতাকিয়া থেকে দ্রুতগামী নৌযানে করে একটি প্রতিনিধি দল মিশরে পাঠানো হলো। প্রতিনিধি দলটি মিশরের শাসকের সাথে দেখা করে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ করলো।
ফলে মিশরীয় শাসক তাদের সাথে করে নিজের একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন। তারা আনতাকিয়ার নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করলো। কিন্তু তাদের সাথে কথা বলে আনতাকিয়ার নেতৃবৃন্দ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারণ, অর্থ, অস্ত্র বা খাদ্য পাঠানোর ব্যাপারে মিশরীয় শাসকের কোনো ভাবনাই ছিল না। দেখা গেলো, মিশরীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর মূলত দুটি কারণ ছিল। প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে মিশরীয় শাসক জানিয়েছেন– আমি শুনেছি, আনতাকিয়ায় একজন অপূর্ব সুন্দরী দাসী রয়েছে। আমি তাকে কিনতে চাই। এছাড়া আমি একজন খুব ভালো মানের আর্টিস্টের কথা শুনেছিলাম। তাকে আমি নিয়োগ দিতে চাই। মিশরীয় শাসকের এই চিঠি যখন আনতাকিয়ার নেতৃবৃন্দের হাতে পৌঁছে, তখন তারা পরাজয় মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবেই শহরটির পতন ঘটে।
দখলদারিত্বের নিরানব্বই বছর
একই ঘটনা বর্তমানে ফিলিস্তিনের সাথে ঘটছে। সেখানকার মুসলমানরা যখন চিৎকার করে বলছে, আমাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমানরা তখন এই চিৎকারে ভ্রুক্ষেপ না করে মুভি দেখায় ব্যস্ত রয়েছে। তখনো যা হয়েছিল, এখনও তা হচ্ছে। তাই, পতনই অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিভিন্ন সময়ে প্রায় নিরানব্বই বছর ফিলিস্তিন তাদের দখলে ছিল। প্রথমবার ৮৮ বছর তাদের দখলে থাকার পর জেরুসালেম আমাদের দখলে ফিরে আসে। তারপর তাদের দখলে ১০ বছর থাকার পর আমরা পুনর্দখল করি। তৃতীয়বারের মতো তারা আবার তা দখল করে এবং এক বছর পর আমরা পুনরায় তা পুনর্দখল করি। এই নিরানব্বই বছর তখনকার মুসলমানরা তাদের লড়াই চালিয়ে যায়। এখনকার মতো সমঝোতা করার জন্য হোটেলে আলোচনায় না বসে তারা জিহাদ চালিয়ে গিয়েছিল।
ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ
জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন মুসলমানরা কীভাবে ফিরে পেয়েছিল? এক্ষেত্রে আমরা সবাই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর অবদানের কথা জানি। কিন্তু তিনি কোথাকার মানুষ, আমরা সাধারণত তা জানি না। হঠাৎ একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটলো, আর অমনি মুসলিম উম্মাহর চেতনা ফিরে আসলো! – ব্যাপারটি মোটেও তেমন ছিল না।
আলেমদের ভূমিকা
সালাহ উদ্দিনের আগমনের প্রায় শতাব্দীকাল আগে দুজন মনীষী ছিলেন। এদের একজন ছিলেন আবু হামিদ আল গাজালী, আর অপরজন আবু বকর আত-তুরতুসি। দুজনই ইসলামের অন্যতম মহান আলেম ছিলেন। এই মনীষীগণ নিছক বইপত্র নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেননি। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধনেও তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। ক্রুসেডাররা আসার বহু আগেই তাঁরা খেয়াল করলেন, উম্মাহ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তখনই তাঁদের আশংকা ছিল, শত্রুরা হয়তো শীঘ্রই আক্রমণ করবে।
তাই তাঁরা বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। চলমান পরিস্থিতির উত্তরণ এবং জিহাদ ঘোষণা করার জন্য তাঁরা খলিফাকে অনুরোধ জানালেন। খলিফা জবাব দিলেন, আমি আপনাদের সাথে আছি। আমরা এগুলো বাস্তবায়ন করবো। তারপর তিনি আবার দাসীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কোনো পদক্ষেপই আর নিলেন না।
দিনের পর দিন তাঁরা শুধু এ ধরনের প্রতিশ্রুতিই শুনে আসছিলেন। যা ছিল নিছক কথার কথা এবং মিথ্যা প্রচারণা মাত্র। যেমন একদিন মসজিদে দাঁড়িয়ে খলিফা বললেন, আমাদের অবশ্যই জিহাদের ডাক দেয়া দরকার।
কিন্তু কে দেবে জিহাদের ডাক? এই দায়িত্ব তো তার নিজেরই! কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না।
অবশেষে তুরতুসি এবং গাজালী বুঝতে পারলেন এসব নেতৃত্বের উপর কোনো ভরসা নেই। এসব কথার ফুলঝুরির চেয়েও কাজের কাজ করা জরুরি।
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলছি, এ জন্য দুঃখিত। আমি আপনাদেরকে ইতিহাস শোনাচ্ছি, বারংবার যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আপনারা যদি ইতিহাস বুঝতে না পারেন, তাহলে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের ঘটনাপ্রবাহ ধরতে পারবেন না।
যা হোক, এই মনীষীগণ ছিলেন সত্যিকারের আলেম। তারা নিছক তাদের পদমর্যাদা, বেতনভাতা কিংবা বইপুস্তক নিয়ে পড়ে না থেকে উম্মাহর ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। উম্মাহর জন্য জরুরি উদ্যোগগুলো তারা নিজেরাই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
হারাকাত ইয়াহইয়া আদ-দ্বীন
এই দুজন মনীষী মিলে অন্যান্য আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তরুণ নারী-পুরুষদেরকে তারা বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাদের এই আন্দোলন ‘হারাকাত ইয়াহইয়া আদ-দ্বীন’ নামে পরিচিত। এর অর্থ ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হৃদয়ে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটানো। বলাবাহুল্য, তারা এতে সফল হয়েছিলেন।
দ্রুত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কোনো কোনো শহরে অন্য শহরগুলোর তুলনায় এটি অধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইসলামের জন্য কর্মরত কোনো কোনো কর্মী অন্যদের তুলনায় বেশি আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন।
দেখুন, ইসলাম যদিও আল্লাহ তায়ালার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, তাই আল্লাহ চাইলে বলতে পারতেন– হয়ে যাও। এর ফলে ইসলাম বিজয়ী হয়ে যেতো এবং গোটা বিশ্ব জয় করে ফেলতে পারতো। কিন্তু ইসলাম কখনোই এই পদ্ধতিতে কাজ করেনি। আপনাকে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, অনুগত হতে হবে। খন্দকের মতো আপনাকে চতুর্দিক থেকে শত্রুরা ঘিরে ফেলবে, কিংবা উহুদের মতো আপনি পরাজিত হবেন। তারপরও আপনাকে ইসলামের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মহানবী (সা) স্বয়ং আহত ও রক্তাক্ত হয়েছিলেন। কেন? কারণ, এটাই ইসলামের পথ। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই কষ্ট করতে হবে। ইসলাম নিজে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে না। নিছক দোয়ার মাধ্যমেও ইসলামের সফলতা আসবে না। যদিও দোয়া গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং কাজ করতে হবে।
ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী
ইরাকের কুর্দিস্তানের মসুল শহরে ‘হারাকাত ইয়াহইয়া আদ-দ্বীনের’ ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি হয়। উত্তর ইরাকের ওই শহর এবং আশপাশের এলাকা একটি রাজকীয় পরিবার শাসন করতো। সেই রাজকীয় পরিবারের নেতৃত্ব দিতেন ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী। তাঁর সম্পর্কে আপনারা কারা কারা জানেন?
ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী সালাহ উদ্দিনের চেয়েও বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জিহাদ ঘোষণা করলেন। ওই পরিস্থিতিতে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক, যিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। তার একটি ছোট সেনাবাহিনী ছিল। তখন বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত এবং কায়রোর ফাতেমীয় খেলাফতে অধীনে ছিল সুবিশাল সেনাবাহিনী। তাছাড়া, ইমাদ উদ্দীন জঙ্গীর মসুল শহরটি ছিল খুবই ছোট। যা আমাদেরকে মদীনার কথা মনে করিয়ে দেয়।
তিনি তার আশপাশের মুসলিম শাসকদের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আহবান জানালেন, আসুন ঐক্যবদ্ধ হই এবং ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করি। সেইসব শাসকেরাও নিজেদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করলেন না।
তখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর দামেস্কে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে সেখানকার শাসকের নিকট তিনি বার্তা পাঠালেন, দামেস্ক মুসলের সাথে যোগ দিলে দুই বাহিনী মিলে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি হবে। ফলে ক্রুসেডারদেরকে পাল্টা আক্রমণ করা যাবে। কিন্তু দামেস্কের শাসক মনে করলেন, ইমাদ উদ্দীন তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠতে পারে। তাই তিনি খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দামেস্কের সাথে শান্তিচুক্তি এবং ইমাদ উদ্দীনের বিরুদ্ধে জোট গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন।
এ খবর জানতে পেরে দামেস্কের জনগণ ফুঁসে উঠতে শুরু করলো। তারা ছিল ভালো মুসলমান। তারা তাদের শাসকের কার্যক্রম মেনে নিতে পারল না। কিন্তু তাদের শাসক ছিলেন স্বৈরচারী। তিনি তাদের দমিয়ে রাখলেন। তাই জনগণ প্রকাশ্যে কিছু করতে পারছিল না। কিন্তু গোপনে তারা ইমাদ উদ্দীনকে জানিয়ে দিলো, আমরা আপনার সাথে আছি।
আসলে মুসলমানরা যদি খাঁটি মুসলমান হয়, তাহলে শাসকরাও তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারে না।
যাই হোক, ইমাদ উদ্দীন সিদ্ধান্ত নিলেন, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আগে এই বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তাই তিনি দামেস্ক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। জনগণ তাকে সহায়তা করলো এবং দামেস্ক তার দখলে চলে আসলো। তারপর তিনি আরো অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে তিনি আলেপ্পো, হোমস নগরীসহ একের পর এক অঞ্চল জয় করলেন। এভাবে ইরাক থেকে বৈরুত পর্যন্ত ফিলিস্তিনের উত্তর দিকের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। এই সমগ্র অঞ্চল তার শাসনাধীনে চলে আসলো।
নুরুদ্দীন জঙ্গী
ইমাদ উদ্দীনের অধীনস্ত একজন নেতা ছিলেন আসাদ উদ্দীন শারকুহ। তিনি তখন লেবাননের বায়ালবেক শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি জঙ্গী পরিবারের মতো কোনো রাজকীয় পরিবারের সন্তান না হলেও শীর্ষ নেতৃবৃন্দের একজন ছিলেন।
ইতোমধ্যে ইমাদ উদ্দীন জঙ্গী মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে নুরুদ্দীন জঙ্গী ক্ষমতায় আসেন। ইমাদ উদ্দীনের মতো নুরুদ্দীনও সালাহ উদ্দীনের চেয়ে বড় মাপের ব্যক্তি ছিলেন।
যাই হোক, তিনি ক্ষমতায় এসে আসাদ উদ্দীনের নেতৃত্বে মিশরের ফাতেমীয় খেলাফতের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। এই দলে আসাদ উদ্দীনের ভাতিজা ইউসুফও ছিলেন। ইউসুফকেই আমরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী হিসেবে জানি। সালাহ উদ্দীন ছিল তার উপাধি।
ফাতেমীয় শাসকের বিশ্বাসঘাতকতা
নুরুদ্দীনের পাঠানো প্রতিনিধি দল মিশরে গিয়ে বললো, আপনারা ক্রুসেডারদের উপর দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করুন। আর আমরা আক্রমণ করবো উত্তর দিক থেকে। এভাবে আমাদের সম্মিলিত বাহিনী তাদেরকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারি। ফাতেমীয় শাসক বললেন, হুম, চমৎকার প্রস্তাব!
কিন্তু আসাদ উদ্দীনের প্রতিনিধি দল দরবার ত্যাগ করার পর পরই তিনি ক্রুসেডারদের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন। তারা ক্রুসেডারদেরকে ফাতেমীয়দের সাথে শান্তিচুক্তি ও নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে জোট গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলো। বর্তমানেও এ রকম ঘটছে। এটা নতুন কিছু নয়।
যাই হোক, এই খবর পেয়ে একই প্রতিনিধি দলকে নুরুদ্দীন আবার পাঠালেন। কিন্তু ফাতেমীয় শাসক বললেন– না, আপনারা ভুল শুনেছেন। তাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি হয়নি। আমি আপনাদের সাথেই আছি। এ কথা শুনে প্রতিনিধি দল ফিরে গেলো। অথচ ফাতেমীয়দের সাথে খ্রিস্টানদের চুক্তির বিষয়টি আসলেই সত্য ছিল।
এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুরুদ্দীন জঙ্গী এক অভাবনীয় কাজ করলেন। তিনি একটা সেনাবাহিনী গঠন করলেন। বাহিনীটি ফিলিস্তিনের উপর দিয়ে গেলো, অথচ ক্রুসেডারদের আক্রমণ না করে ফাতেমীয়দের মিশরে আক্রমণ (অবরোধ?) করে বসলো। তারপর খলিফার কাছে বার্তা পাঠানো হলো– হয় আমাদের সাথে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের যোগ দিন, আর নয়তো আমরা আপনাদের সাথে লড়াই করবো। খলিফা জবাব পাঠালেন, আমরা আপনাদের সাথেই আছি। আপনাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমি বাহিনীকে প্রস্তুত করছি।
খলিফার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আসাদ উদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনী ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হলো। অব্যবহিত পরেই আসাদ উদ্দিন খবর পেলেন, তার সাথে চাতুরী করা হয়েছে। ফাতেমীয় খলিফা আবারো নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি আসাদ উদ্দীনের বাহিনীর গতিবিধি গোপনে খ্রিস্টানদের জানিয়ে দিচ্ছেন। এই খবর পেয়ে তিনি পুনরায় ফিরে এসে কায়রোর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন। তারপর খলিফার কাছে খবর পাঠালেন, আমি আপনার সাথে লড়াই করার জন্য আসিনি। আমি শুধু এটুকু নিশ্চিত করতে চাই, ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করার জন্য আপনি আমাদের সাথেই যাচ্ছেন। তখন খলিফা আবারো নানা রকম ছলচাতুরীপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করলেন।
সালাহ উদ্দীনের বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ
সালাহ উদ্দিন পুরো ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তার চাচা আসাদ উদ্দীনকে গিয়ে বললেন, চাচা! এই নেতাদের উপর কোনো ভরসা নেই। তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনুমতি নিন। চাচা জবাব দিলেন, মুসলমানদের মাঝে কোনো ঝামেলা হোক, তা আমরা চাই না। সালাহ উদ্দীন বললেন, খলিফার উপর কোনো ভরসা নেই। অথচ আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে ক্রুসেডারদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক নেতারা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না। কিন্তু সালাহ উদ্দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আসাদ উদ্দীন দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাই চাচার অনুমতি ছাড়াই সালাহ উদ্দীন কিছু সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং শাসককে হত্যা করলেন।
এর ফলে নুরুদ্দীনের কর্তৃত্ব উত্তর সিরিয়া ও এর আশপাশের অঞ্চল এবং মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ ঘটনার দুই মাস পর আসাদ উদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। তখন নুরুদ্দীন মিশরের গভর্নর হিসেবে সালাহ উদ্দীনকে নিযুক্ত করেন।
এবার তারা ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইতোমধ্যে নুরুদ্দীনও ইন্তেকাল করলেন। তারপর নুরুদ্দীনের পরিবারের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সালাহ উদ্দীন তাদের কাছে বার্তা পাঠালেন, নিজেরাই এভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অতীতের শাসকদের মতো তারাও এ কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা নিজেদের স্বার্থেই মত্ত হয়ে রইলো।
সালাহ উদ্দিন এবার বিষয়টি নিজেই সমাধা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন হয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গীর শাসিত অঞ্চলে পৌঁছলেন এবং এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। এর ফলে তিনি পুরো অঞ্চলের উপর নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন।
এবার ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর সমর্থন নিয়ে তিনি খ্রিস্টানদের পরাজিত করলেন। হাত্তিনের যুদ্ধে তিনি তাদেরকে করুণভাবে পরাজিত করলেন। অথচ তার সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ হাজার। এই পরাজয়ে খ্রিস্টানরা মহা ক্ষিপ্ত হলো। ক্রুসেডাররা যুদ্ধের ময়দানে আগের চেয়ে বেশি রসদ পাঠাতে লাগলো। তারা আক্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করলো। আর সালাহ উদ্দীন মাত্র ১২ হাজার সেনা নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।
এভাবে আমরা আবার আমাদের কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছিলাম। কিন্তু এর পেছনে ছিল এক দীর্ঘ ইতিহাস। একজন গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী হুট করেই আবির্ভূত হননি। শত্রুদেরকে পরাজিত করার আগে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলামী স্কলারগণ যে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন, তারই ফলাফল ছিলেন একজন আইয়ুবী।
ইজ্জ উদ্দীন ইবনে আব্দুস সালামের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন
কয়েক বছর পর ইতিহাসের গতিধারায় এবার আগমন ঘটলো মোঙ্গল ঝড়ের। সামনে যাকেই পেয়েছে, তাকেই তারা শেষ করে দিয়েছে। প্রথমে তারা আব্বাসীয় খেলাফত তছনছ করে দিলো। তারপর একে একে উত্তর ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান প্রভৃতি মুসলিম অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালালো। তারপর তারা প্রবেশ করে ফিলিস্তিনে। এবার তারা উত্তর আফ্রিকা দখল করার পরিকল্পনা করে, যাতে ইউরোপে প্রবেশ করা যায়। কেউই তাদেরকে থামাতে পারছিল না।
আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সামনে যেন অনুসরণীয় কিছু উদাহরণ থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি এই দীর্ঘ ইতিহাস বলে যাচ্ছি। প্রিয় তরুণ ভাই ও বোনেরা! মহান মানুষদের কারণেই ইসলাম মহান হয়েছে। ইসলাম আপনাতেই মহান হয়ে যায়নি। তাই আমাদেরকে এর জন্য কাজ করতে হবে।
যাইহোক, এমন এক পরিস্থিতিতে আবির্ভাব ঘটে একজন মহান মনীষীর। তাঁর নাম ইজ্জ উদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম। তিনি ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। মিশরীয় ছিলেন না। মোঙ্গলরা আক্রমণ করার আগেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার জন্য তিনি দামেস্কের শাসককে আহ্বান জানালেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসক এটি পছন্দ করলেন না। তিনি তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করলেন। তখন তিনি মিশরে চলে গেলেন। মিশরের শাসক তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি ছিলেন মিশরে অবস্থানরত সিরিয়ান। দেখুন, ইসলামে জাতীয়তা নেই। যাই হোক, মিশরে তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের নেতা হয়ে ওঠলেন। সকল আলেম তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। এ কারণে তাকে সুলতানুল উলামা (আলেমদের সুলতান) হিসেবে অভিহিত করা হয়।
দেখুন, আমরা যদি সত্যিকারের মুসলিম হয়ে থাকি, তাহলে আপনার জাতীয়তা কি, কোত্থেকে আপনি এসেছেন, আমি তা বিবেচনা করবো না। আপনিও আমার ব্যাপারে তা করবেন না। কারণ, তখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে বিবেচনা করবো না।
সাইফুদ্দীন কুতুজ
যাই হোক, ইজ্জ উদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম জিহাদের বাণী ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। এক পর্যায়ে মামলুক শাসকরা জিহাদ ঘোষণা করতে সম্মত হয় এবং তারা তা করেও। কার বিরুদ্ধে এই জিহাদ? অপ্রতিরোধ্য মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে। এই তাতার জাতির গতি তখন পর্যন্ত কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি।
মামলুক শাসক সাইফুদ্দীন কুতুজের নেতৃত্বে মিশরে খুব ছোট একটি সেনাদল গঠন করা হলো। এই মহান ব্যক্তিটির কথা আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার। সাইফুদ্দীন কুতুজ ঘোষণা করলেন, এই যুদ্ধ শুধু ইসলামের জন্য। কোনো জাতীয় স্বার্থ, সম্পদ বা তেলের জন্য এই যুদ্ধ নয়।
এই সেনাবাহিনীর সর্বাগ্রে ছিলেন সেই বৃদ্ধ আলেম ইজ্জ উদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম। শুধু খুতবা দেওয়া আর অকর্মন্য বসে থাকার মতো আলেম তিনি ছিলেন না। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য আলেমদের ভূমিকা আবারো আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।
যাই হোক, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মামলুকরা আইন জালুতের প্রান্তরে মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং সেখান থেকে তাতাররা পালিয়ে যায়। এই পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ডে মোঙ্গলদের আধিপত্যের অবসান ঘটে।
ইসলামী সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্য
যাই হোক, আমরা আবারো ইসলামী সভ্যতার একটি অগ্রগতি লক্ষ করলাম। ইসলাম অন্যান্য সভ্যতার মতো নয় যে, ২/৩ বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইসলামের ক্ষেত্রে কখনোই এমনটি ঘটেনি। ইসলামী সভ্যতার পতন ঘটতে শত শত বছরে লেগেছে। কী জন্য এই পতন হয়েছে? কারণ, নেতৃবৃন্দের অনেকেই ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। আলেমদের কেউ কেউও বিচ্যুত হয়েছিলেন। তবে ইসলামের মতাদর্শ অক্ষুন্ন রয়েছে। কারণ কোরআনও অবিকৃত রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত কোরআন অবিকৃত থাকবে এবং মুসলমানরা তা পড়ে অনুধাবন করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা বার বার ফিরে আসবে।
উসমানীয় খেলাফতের পতন
বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল। সময় সংক্ষেপ করার জন্য আমি বেশ কিছু ঘটনা বাদ দিয়ে দ্রুত ইতিহাস বলে যাওয়ার চেষ্টা করবো।
তখন পর্যন্ত উসমানীয় খেলাফত ছিল ইসলামের কেন্দ্রভূমি। শুরুর দিকে প্রচণ্ড প্রতাপশালী এই খেলাফত ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে এসে সাম্রাজ্যটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।
তখন খলিফা ছিলেন সুলতান আব্দুল হামিদ। ফিলিস্তিন ভূমি যেন ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যে একদিন থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে এক দল ইহুদী আসে। এ ব্যাপারে তারা খলিফার সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা চালায়। খলিফা তাদেরকে বললেন, এই সমঝোতা হতে পারে কেবল আমার লাশের বিনিময়ে! এ কথা শুনে তারা ফিরে গেলো। সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইহুদী সম্মেলনে হার্জেল বললেন, আব্দুল হামিদ যতদিন মুসলমানদের নেতৃত্বে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন নিয়ে আমাদের কোনো আশা নেই। তাকে অবশ্যই ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।
মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক
এই লক্ষ্যে তারা বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যেতে লাগলো। এক পর্যায়ে তারা তুরস্কের ভেতরেই তাদের অনুগত একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হলো। প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি তাদের সাথে হাত মেলালো। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সেনাবাহিনীর একটি ডিভিশনের কমান্ডার। তার নাম মোস্তফা কামাল। পরবর্তীতে তাকে আতাতুর্ক (জাতির পিতা) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি তার উপাধি, নামের অংশ নয়।
যাই হোক, ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ১৯০৯ সালে তারা খলিফা আবদুল হামিদকে নির্বাসনে পাঠাতে সক্ষম হয় এবং কর্তৃত্ব তাদের হাতে চলে আসে। যদিও তখন পর্যন্ত খেলাফত ছিল। তবে তা ছিল নামে মাত্র। সুলতান আব্দুল হামিদের পর একে একে সিংহাসেন আরোহণ করেন সুলতান মোহাম্মদ রাশাদ ও সুলতান মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ। কিন্তু ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল মূলত ইহুদীদের অনুগত ব্যক্তিদের হাতে।
লরেন্স অব অ্যারাবিয়া
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা তখন বেশ শক্তিশালী ছিল। তারা এই দুর্বল সম্রাজ্যটি দখল করে নিতে চাইলো। তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করলো। এক পর্যায়ে তারা মিশর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। তারপর তারা ফিলিস্তিন দখলের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু উসমানীয় সেনাবাহিনী তাদেরকে দক্ষিণ জর্ডানের আকাবা অঞ্চলে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। ফলে এডমন্ড অ্যালেনবি তার ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হতে পারছিল না। তাই ব্রিটিশরা এবার অটোমানদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে দিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। তারা নিজস্ব গুপ্তচর পাঠালো। সেই গুপ্তচরের নামটি খুবই বিখ্যাত– লরেন্স অব অ্যারাবিয়া। তিনি যে ব্রিটিশ গুপ্তচর ছিলেন, তার প্রামাণ্য দলীল রয়েছে।
তিনি হেজাজ শহরে গিয়ে তৎকালীন আরবদের নেতা শরীফ হোসাইনের ছেলে ফয়সালের সাথে দেখা করলেন। তিনি তাকে আরব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হলেন। তাকে বললেন– আপনারা তো তুর্কি নন, আরব। তাহলে আপনাদের পক্ষে কীভাবে তুর্কিদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া সম্ভব! আপনারা যদি তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়তে চান, তাহলে আমরা সহায়তা করবো। ব্রিটিশরা তাদের আরো কথা দিলো– আপনারা তুর্কিদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে যদি সহায়তা করেন, তাহলে আমরা পুরো আরব অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিবো। এভাবে আরবরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশদের পক্ষে যোগদান করলো।
শরিফ হোসাইনের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তার ছেলে ফয়সাল। লরেন্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা পূর্ব দিক থেকে আকাবায় আক্রমণ চালালো। অটোমানরা পশ্চিম দিক ও সাগর পথের আক্রমণ ঠেকাতে সেনাবাহিনী প্রস্তুত রেখেছিল। কিন্তু পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ তাদের জন্য ছিল অপ্রত্যাশিত। ফলে আকস্মিকভাবেই আরবদের হাতে আকাবা শহরটির পতন ঘটলো। তারপর ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ব্রিটিশ ও আরবরা যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে সেখান থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এরপর ফয়সালের নেতৃত্বে আরব বাহিনী ও অ্যালেনবির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো।
অ্যালেনবি এক পর্যায়ে জেরুসালেম দখল করলেন। তারপর সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সমাধিতে গিয়ে কবরে লাথি মারলেন। তখন তার স্বগোতোক্তি ছিল– ‘সালাহ উদ্দীন! আমরা ফিরে এসেছি, আরবদের সহযোগিতা নিয়েই আমরা ফিরে এসেছি!’ ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!
তারপর দামেস্ক দখল নিয়ে শুরু হলো দুই বাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা। উভয় বাহিনী একই দিনে শহরটিতে প্রবেশ করে।
আরব জাতীয়তাবাদ ও সাইকস-পিকট চুক্তি
সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে তখন নানা ধরনের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ চলছিল। অবশেষে ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নিলো, আল-হোসেইন পরিবারের হাতে তারা নামে মাত্র আরবের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করবে। ফলে শরিফ হোসাইনের ছেলে ফয়সাল পেলেন দামেস্কের ক্ষমতা, রাজী পেলেন ইরাকের ক্ষমতা। এভাবে অন্যরা বাদবাকি অঞ্চলের ক্ষমতা পেলো। তবে সবই ছিল নামে মাত্র। এটি ১৯১৭ সালের ঘটনা। এর আগে ১৯১৬ সালে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল।
আমি বলবো, এগুলো ছিল আরবদেরই হাতের কামাই। কিন্তু তখন তারা যড়যন্ত্রটা বুঝতে পারেনি, যা আমরা এখন বুঝতে পারছি। পরবর্তীতে ব্রিটিশ দলিলপত্র প্রকাশ হয়ে পড়লে দেখা গেলো, ১৯১৬ সালেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে চুক্তিটি হয়েছিল, যা ‘সাইকস-পিকট চুক্তি’ হিসেবে এখন পরিচিত। চুক্তির শর্তানুযায়ী আরব ভূমি দখল করার পর সিরিয়া ও লেবানন পাওয়ার কথা ফ্রান্সের। আর অবশিষ্ট আরব অঞ্চল পাবে ব্রিটেন। তবে ইতালি এই ভাগাভাগিতে ক্ষুব্ধ হয়। তাই ইতালিকে লিবিয়ার ভাগ দেয়া হয়।
মহানবী (সা) বলেছেন,
تُوْشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلىٰ قَصْعَتِهَا. قَالُوْا أَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلاَّ، بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ، وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. قَالُوْا مِمَّ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لَمَّا أَصَابَكُمُ الْوَهْنُ. قَالُوْا: وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ
ভাবানুবাদ: শীঘ্রই অন্যান্য দেশ তোমাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে (ঐক্যবদ্ধ হওয়ার) আহ্বান করবে, যেভাবে মানুষ নৈশভোজের জন্য একে অন্যকে আমন্ত্রণ করে। সাহাবীরা তখন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমরা কি সংখ্যায় তখন এতোই কম হবো (যাতে আমরা পরাজিত হয়ে পড়বো)? রাসূল (সা) বললেন, না, তোমরা বরং সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। কিন্তু তখন তোমরা হয়ে পড়বে জলে ভাসা খড়কুটোর মতো। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমাদের এই অবস্থা হবে? তিনি বললেন, কারণ, তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমরা দুর্বল হয়ে পড়বো, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, যখন তোমরা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুর কথা ভুলে যাবে, তখন দুর্বল হয়ে পড়বে।
অতএব, মুসলিম উম্মাহর একমাত্র আকাঙ্খা হওয়া উচিত আখেরাতকে ভালোবাসা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।
যাই হোক, আগের কথায় ফিরে আসি। এভাবেই শত্রুরা আমাদের বোকা বানিয়েছিল। তারা আমাদের ভূমি দখল করেছে। তারপর সব জায়গায় পুতুল সরকার বসিয়েছে। মুসলমান ও আরবদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। ফলে আরব ও তুর্কিদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে। এ ধরনের অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে।
১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন। তিনি ঘোষণা করেন, আমরা এই নামে পরিচিত হতে চাই না। তুরস্ক এখন থেকে আর মুসলিম বিশ্বের অংশ নয়। আমরা ইউরোপীয় হিসেবে পরিচিত হতে চাই। আমরা আরবি ভাষা ও বর্ণমালা আর ব্যবহার করতে চাই না।
এর ধারাবাহিকতায় আরবি ভাষায় আজান পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে আজান দিতে হতো তুর্কি ভাষায়। সম্ভবত ৫৪ বছর পর্যন্ত তুর্কি ভাষায় আজান দিতে হয়েছিল! এরচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার আর কী হতে পারে? আমরা অধঃপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম। কী দুর্ভাগ্য!
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
এবং তারা নানা রকম পরিকল্পনা আঁটতো, আর আল্লাহও পরিকল্পনা আঁটতেন। নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। (সূরা আনফাল: ৩০)
বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী পুনর্জাগরণ
১৯২৪ সালে খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটায় বিশ্ব রাজনীতিতে ইসলামের আর কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকলো না। মুসলমানরা চরম দুর্বল হয়ে পড়লো। বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ ছাড়া ইসলামের জন্য স্কলারদের কোনো অবদান ছিল না। জামালুদ্দীন আফগানী, মোহাম্মদ আব্দুহু, রশিদ রিদার মতো অল্প কয়েকজন মাত্র কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সবাই নিজের মতো করেই করছিলেন। সম্মিলিতভাবে কোনো কাজ হচ্ছিল না। কেউ এগিয়ে এসে বলছিল না– আসুন সবাই মিলে ইসলামের জন্য কাজ করি।
তারপর আকস্মিকভাবেই কয়েকজন মহান স্কলার আবির্ভূত হলেন। অথচ অনেকেই তখন যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব ওঠে আসেনি। আসলে অতীতেও কখনো এমনটি হয়নি। সবসময়ই কাজের শুরু হয় স্কলারদের মাধ্যমে। তারপর তা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে নেতৃত্ব ওঠে আসে। আমরা জানি– كَمَا تَكُوْنُوْا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ (মানুষ যেমন, নেতৃত্বও তেমন)।
অতএব, অবশ্যই শুরুতে একটি গণআন্দোলন থাকতে হবে। কিন্তু এর সূচনা কে করবেন? অবশ্যই স্কলারগণ। বিংশ শতাব্দীতে যেসব মহান ব্যক্তি মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে প্রথমেই আসে ইমাম হাসান আল বান্নার নাম। খেলাফতের পতনের মাত্র চার বছর পর ১৯২৮ সালে তিনি মিশরে তার এই আন্দোলন শুরু করেন। অনেক মানুষ তার আন্দোলনে শামিল হতে থাকলো। সুন্নী ধারার মুসলমানরা (আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত) এতে শরীক হতে থাকলো। আরব উপদ্বীপে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। মরক্কোতেও আন্দোলন শুরু হলো। ফিলিস্তিনেও আন্দোলন গড়ে ওঠতে থাকে। সিরিয়ায় আন্দোলনটি শুরু হয় মোস্তফা আস-সিবায়ীর নেতৃত্বে। আমিনুল হোসাইনীসহ অনেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ করে একই ধ্যান-ধারণার আলোকে পাকিস্তানে একজন আন্দোলন শুরু করলেন। হাসান আল-বান্নার সাথে যার ইতোপূর্বে দেখাও হয়নি। তিনি হলেন ইমাম আবুল আ’লা মওদূদী।
ইসলামী পুনর্জাগরণের তাৎপর্য ও ধারাবাহিকতা
উল্লেখিত সবার মূল বক্তব্য কী ছিল?
আমাদের ভরসার একমাত্র জায়গা হলো ইসলাম। ইসলাম নিছক ইবাদতের জন্য নয়। ইসলাম হচ্ছে একটি জীবনব্যবস্থা। রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন, বিচারব্যবস্থা, সমাজ জীবন ইত্যাদি সবই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য রয়েছে। আমাদেরকে আবার জেগে ওঠতে হবে। আমাদের তরুণদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের ইতিহাসে নারীরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার। ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাদেরকেও অতি অবশ্যই ভূমিকা রাখার সুযোগ হবে।
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! গত ছয়’শ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম সর্বত্র ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। অতীতে আপনারা এই আন্দোলন হয়তো দেখেছেন লিবিয়া, সুদান, বাংলাদেশ কিংবা অন্য কোথাও। কিন্তু সেগুলো সফল হয়নি। তবে বর্তমানে আপনি মুসলিম বিশ্ব কিংবা অমুসলিম বিশ্ব– যেখানেই যান না কেন, আপনি দেখবেন সর্বত্রই মুসলনরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসছে। ইসলামের প্রতি তরুণদের কমিটমেন্ট চোখে পড়ার মতো। এর প্রেক্ষিতে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, আমরা আবার স্রোতের গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে পারবো। আমি এই সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঠিক যেভাবে আপনাদেরকে এখন দেখছি।
ইতিহাসের গতিপথ
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! বেশিরভাগ মানুষ ৯/১১, বেনিন হামলা ইত্যাদি সব ঘটনা নিয়ে চিন্তিত। তারা আসলে সামগ্রিক চিত্রটা দেখতে পাচ্ছে না। খুব কম মানুষই এ বিষয়ে সচেতন। এই সামগ্রিক চিত্রটা পেতে হলে ইতিহাস ও সভ্যতার গতিধারা বুঝতে হবে।
ইসলাম খুব দ্রুত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তারপর প্রায় ৮’শ বছর ধরে এটি ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকে। অতঃপর গত ৬’শ বছর ধরে পতন হতে হতে ১৯৪৮ সালে একবার এবং ১৯৬৭ সালে আবারো একদম তলানীতে এসে ঠেকে। ওই সময় আমরা আল্লাহ তায়ালার শত্রু ইহুদীদের কাছে পরাজিত হই। তারা আমাদের কেন্দ্রভূমি ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আপনারা দেখতে পাবেন, ১৯৬৭ সালের পর আবারো শক্তিশালী পুনর্জাগরণ শুরু হয়। এর আগে আরব জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির ব্যাপক প্রভাব ছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পরাজয়ের পর আমরা আবার জেগে ওঠি এবং নতুন করে পুনর্জাগরণ শুরু হয়। প্রথমবারের মতো মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। মুসলমানদের উদ্যোগে ব্যাংক, মিডিয়া, সংবাদপত্র, স্যাটেলাইট টিভি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম নারী ও শিশুদের জন্য নানা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক কথায় দুনিয়া জুড়ে প্রতিটি সেক্টরে মুসলমানদের অংশগ্রহণ শুরু হয়।
আগামী দিনের ইসলাম
সব মিলিয়ে একটা জোয়ার তৈরি হয়েছে। কিন্তু এর পরবর্তী ধাপ কী? আগামী দিনের ইসলাম কেমন হবে?
মহানবীর (সা) একটি প্রসিদ্ধ হাদীস শুনিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করবো। এই হাদীসটির মাধ্যমে তিনি যেন আমাদের নিকট ইতিহাসের গতিপথ জানিয়ে দিচ্ছেন। হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। নাসিরুদ্দীন আলবানী সংকলিত হাদীস গ্রন্থসহ আরো অনেক গ্রন্থে হাদীসটি স্থান পেয়েছে। তাই এটি নিয়ে কোনো সংশয় নেই বলা যায়।
تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت
ভাবানুবাদ: আল্লাহ তায়ালা যতদিন চাইবেন, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে নবুয়ত বহাল থাকবে। অতঃপর আল্লাহ যখন চাইবেন, তখন তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুয়তী শাসনব্যবস্থার মতোই খেলাফত ব্যবস্থা আসবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততদিন তা থাকবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এক সময় এর সমাপ্তি ঘটবে। অতঃপর আসবে রাজতন্ত্রের যুগ। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন এসব রাজতন্ত্র টিকে থাকবে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এর সমাপ্তি ঘটবে। তারপর আসবে সামরিক শাসন।[1] আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততদিন এ শাসন থাকবে। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় এর অবসান ঘটবে। তারপর নবুয়তী শাসনব্যবস্থার মতো খেলাফত ব্যবস্থা আবারো প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথা বলে রাসূল (সা) চুপ হয়ে গেলেন। [মুসনাদে আহমদ, চতুর্থ খণ্ড, (কায়রো: মুয়াসসাহ আল-কুরতুবাহ), ২৭৩, (নং. ১৮৪৩০)]
আল্লাহর রাসূলের (সা) এই হাদীসের প্রতিটি ধাপকে আমরা সত্যে পরিণত হতে দেখছি। প্রথমে নবুওয়াত বহাল ছিল মাত্র ২৩ বছর। তারপর এসেছিল খেলাফত, যা ৩০ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। তারপর এসেছে রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র বুঝাতে হাদীসে ‘মুলকান আ-দ্দান’ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী রাজতন্ত্র বুঝাতে আরবীতে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। বাস্তবেও আমরা এর ঐতিহাসিক সত্যতা পেয়েছি। যেমন, উমাইয়া শাসন ছিল ১৩০ বছর, আব্বাসীয় শাসন ছিল ৪’শ বছর। এভাবে মামলুক, ফাতেমীসহ আরো অনেকে দীর্ঘদিন শাসন করেছে। উসমানীয় শাসন প্রায় ৬’শ বছর টিকে ছিল। তারপর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে এসব রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। তারপর এসেছে সামরিক শাসন। বর্তমানে কয়টা মুসলিম দেশ সামরিক শাসনের বাইরে? চারপাশে খেয়াল করে দেখুন! গুটি কতক বাদে প্রায় সব মুসলিম দেশই সামরিক শাসনের অধীন। রাসূল (সা) সত্য কথাই বলেছেন। চৌদ্দশ বছর আগের একটি হাদীসের সত্যতা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। সামরিক শাসনের যুগের সমাপ্তির পর কী আসবে– এ সম্পর্কে যদি আমরা কোনো মতামত দেই, তাহলে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বয়ং মহানবী (সা) জানিয়ে গেছেন, যিনি নিজ থেকে কিছু বলেন না। আল্লাহ বলেছেন,
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
তিনি নিজ থেকে কোনো কথা বলেন না। বরং এসব কথা অহী ছাড়া আর কিছু নয়, যা তার কাছে পাঠানো হয়। (সূরা নাজম: ৩-৪)
অতএব, রাসূলের (সা) ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী মুলকান জাবরিয়্যাহর পর আবু বকর, ওমর, উসমান, আলীর খেলাফত ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।
উপসংহার
তারপর কোন ব্যবস্থা আসবে, আমরা তা জানি না। কিন্তু ইসলাম যে আবারো বিজয়ী হতে যাচ্ছে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আগামী দিন হবে ইসলামের দিন। তাই এখন আপনাদের সামনে রয়েছে দুটি পথ: ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাজ করা এবং পরকালে পুরস্কৃত হওয়া, নতুবা বস্তুবাদী জীবন উপভোগ করা এবং পরকালে বঞ্চিত হওয়া।
মক্কা বিজয় সম্পর্কে নাজিল হওয়া একটি আয়াত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا
তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা এক নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি, যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে। (সূরা হাদীদ: ১০)
এখানে বিজয় বুঝাতে ‘ফাতাহ’ না বলে ‘আল-ফাতাহ’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সুনির্দিষ্ট বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। অবাক করা ব্যাপার হলো, এই আয়াত যখন নাজিল হয়, তখনো মক্কা বিজয় হয়নি! আল্লাহ নিজেই বলেছেন, বিজয় আসার আগে যারা জিহাদ ও অর্থ ব্যয় করবে তারা অধিক উত্তম।
প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সিদ্ধান্ত এখন আপনার হাতে। আমরা যদি ইসলামের জন্য কাজ করি, তাহলে কাঙ্খিত বিজয় দ্রুত আসবে। আর যদি অলসতা করি, তাহলে বিজয় আসতে সময় লাগবে।
তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো আত্মগঠন করা, পরিবার গঠন করা এবং প্রত্যেকেই যেন ইসলামের পথে চলে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। আপনার চারপাশে ইসলামের আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন। ইসলামী সংগঠন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মিডিয়া, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি গড়ে তুলুন। আল্লাহ তায়ালা যে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন, আগামী দিনে ইসলামের সেই নিশ্চিত বিজয়ের অংশীদার হতে অন্তত কিছু একটা করুন।
ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমার কথা শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।
هٰذَا، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. شَكَرَ اللهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ. وَنَسْئَلُ اللهُ تَعَالَى لَنَا وَلَكُمُ الْقَبُوْلُ. وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
নোট:
[1] হাদীসে ব্যবহৃত ‘মুলকান জাবরিয়্যাহ’ পরিভাষার অর্থ হলো জবরদস্তিমূলক শাসন। ড. সোয়াইদান যদিও এর অর্থ করেছেন সামরিক শাসন। আসলে সামরিক শাসন হলো জবরদস্তিমূলক শাসনের একটি প্রকার মাত্র। স্বৈরাচারী শাসনও জবরদস্তিমূলক শাসনের আওতায় পড়ে। – সম্পাদক