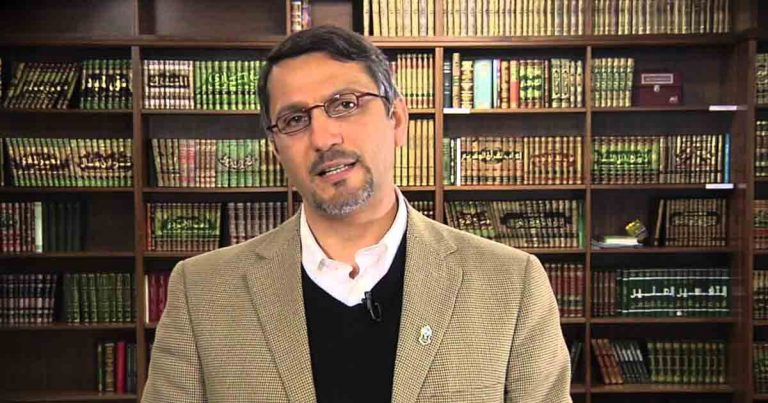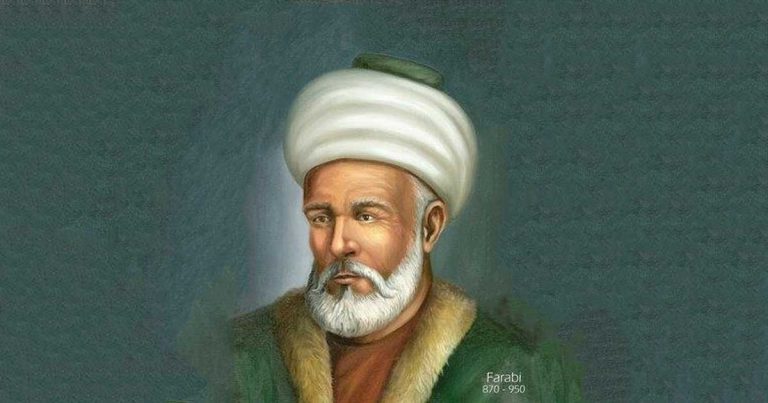কিয়ের্কেগার্দ ও অস্তিত্বের তিন স্তর
এডিটর’স নোট:
অস্তিত্ববাদী দর্শনের জনক হলেন সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫)। ব্যক্তি জীবনে গভীর আস্তিক এই দার্শনিক, মানুষ কীভাবে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে, সেই পথ খুঁজেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সর্বশক্তিমান এক সত্তার নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই কেবল মানুষ আত্মসত্তাকে খুঁজে পায়, অর্থাৎ মানুষ হয়ে ওঠে। কিয়ের্কেগার্দের এ সংক্রান্ত ভাবনাগুলোর সারসংক্ষেপ নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করেছে একাডেমি অব আইডিয়াস। ভিডিওটির ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে সিএসসিএস-এর পাঠকদের জন্য অনুবাদ করেছেন এন এইচ আব্দুল্লাহ।
*****
“মানুষের যদি একটি শাশ্বত চেতনা না থাকে, বন্য উন্মত্ততা দ্বারাই যদি মানুষের সবকিছু পরিচালিত হয় – হোক সেই কর্ম মূল্যবান কিংবা তুচ্ছ, একটি চির অতৃপ্ত মন ও বিশাল শূন্যতার মাঝেই যদি মানুষের সবকিছু ঢাকা পড়ে থাকে; তাহলে হতাশা ছাড়া জীবনের আর কীইবা মানে থাকে?” (Fear and Trembling)
কিয়ের্কেগার্দের মতে, মানুষ হলো অসীম ও সসীম, ক্ষণস্থায়ী ও চিরন্তন, স্বাধীন ও শর্তাধীন ইত্যাদি বিপরীতমুখী উপাদানের সমন্বয়। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো, নিজের মধ্যে এই বিপরীতধর্মী উপাদানগুলোকে এমনভাবে সমন্বয় করা, যাতে এগুলোর সহায়তায় একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটা করে ফেলতে পারার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ‘আত্মসত্তা’ (selfhood) অর্জন করে। জীবনের কোনো এক পর্যায়ে যে ব্যক্তি হতাশাপূর্ণ একটি অবস্থা পার করে না, তার আত্মা অসুস্থতায় আক্রান্ত হয় এবং তার আত্মসত্তা (self) বলতেও কিছু নেই।
কিয়ের্কেগার্দ তাঁর লেখায় বিভিন্ন প্রকার জীবনদর্শন (life-views) বা ‘অস্তিত্বের স্তরের’ (existence-spheres) চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এগুলোর কার্যকারিতা যাচাই করেছেন। এই জীবনদর্শনগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিত আমরা এখন তুলে ধরবো।
“জীবনদর্শন, জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলার সহজাত তাড়না প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যেই থাকে।”
কীসে কল্যাণ আছে, জীবনকে কীভাবে যাপন করতে হয়, তা বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব জীবনদর্শন থাকে। তবে এই জীবনবোধ সবার মধ্যে সচেতনভাবে গড়ে ওঠে না।
বরং বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে আসলে ‘আমজনতা’ (mass-men, or philistines)। কখন যে তারা সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধ ও সমাজের প্রত্যাশাকে নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেয় এবং প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, সেটি তারা টেরই পায় না। সমাজের এসব প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সে নিজে নিজে কখনো তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিয়ে ভাবে না। আমজনতার দৃষ্টি কেবল বাইরের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ– বলতে গেলে পুরো জীবনটাই স্রেফ অন্যদের অনুকরণ করে কাটিয়ে দেয়।
“‘শোন! সেখানে গিয়ে কিন্তু ভদ্র আচরণ করবে। অন্যান্য ভদ্র বাচ্চারা কীভাবে কী করে, সেগুলো খেয়াল করবে এবং তাদের মতো আচরণ করবে। ঠিক আছে?’ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে মায়েরা তার বাচ্চাদেরকে যেভাবে শাসন করে, ব্যাপারটা যেন ঠিক সেরকম। ফলে দেখা যায়, পরবর্তীতে বড় হয়ে সে অন্যদের অনুকরণেই জীবনযাপন করে। সে নিজে থেকে নতুন কিছু করতে পারে না। অন্যরা কী ভাবছে – এটা না জানা পর্যন্ত তার নিজস্ব কোনো মতামতও কখনো গড়ে ওঠে না। তার জীবনটা হয়ে পড়ে অনেকটা পুতুলনাচের পুতুলের মতো। অত্যন্ত সুনিপুণভাবে জীবনভর সে অন্যদের অনুকরণ করে যায়।” (Concluding Unscientific Postscript)
স্বীয় ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে আমজনতার এই অসচেতনতা অনেকটা পশুর পালের সাথে তুলনীয়। আমজনতার ব্যাপারে যে যা-ই বলুক না কেন, কিয়ের্কেগার্দ এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমজনতার কারো আত্মসত্তা (self) বলতে কিছু থাকে না। এ কারণে মানুষ হিসেবে তাদের জীবনের কোনো স্বার্থকতা নেই।
তবে সবাই আমজনতার মতো জীবন কাটায় না। কখনও কখনও মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন সে নিজেকে সামাজিক পরিচয় ও সামাজিক শৃঙ্খলের বেড়াজাল থেকে আলাদা করে নেয়।
এ ধরনের সচেতনতা তখনই তৈরি হয়, যখন কেউ গভীরভাবে বুঝতে পারে যে, সমাজের সাথে তার বন্ধনটি মূলত এক প্রকার শৃঙ্খল, যা অত্যন্ত নিস্পেষণমূলক এবং এই বন্ধন তাকে একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। সামাজিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার পর সে মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করে– তার সামনে বহু বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। তখন সে এসব বিকল্প পথের সম্ভাবনা নিয়ে খুব করে ভাবতে থাকে। জীবন তার সামনে হাজির হয় একটি উর্বর জমিন হিসেবে, যেখানে সে জীবন সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। ব্যক্তিসত্তার এ পর্যায়টি কিয়ের্কেগার্দের মতে ‘অস্তিত্বের স্তরের’ (existing-sphere) প্রথম ধাপ। তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘নান্দনিক জীবনদর্শন’ (the life-view of aestheticism)।
এই পর্যায়ে নান্দনিকতার প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিটির (aesthete) মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটে। এ সময় সে বিভিন্ন ধরনের পেশা ও সম্পর্কে জড়ায়। শখের বশে নানান কিছু করে। এভাবে সে জীবন নিয়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিন্তু কোনোটিতেই সে স্থির থাকতে পারে না। স্থায়ী কোনো অনুরাগ তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। কোনো কিছুর কাছে নিজেকে সে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারে না। তার স্বাধীনতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে – এই আশংকায় সে যে কোনো ধরনের সিরিয়াস রিলেশনশিপ এড়িয়ে চলে। কারণ, জীবন সম্পর্কে তার চলমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা কখন যে কোনদিকে মোড় নেবে তার ঠিক নেই।
কিয়ের্কেগার্দ বলেন,
“শিল্পসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিকে (aesthete) অবশ্যই সারা জীবনের জন্য কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে থাকতে হয়। নয়তো তার স্বাধীন সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একই কারণে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বের সম্পর্কও তার জন্য ক্ষতিকর। বিয়ে তো আরো বেশি ভয়ানক ব্যাপার। লোকেরা বলে, স্বামী-স্ত্রী নাকি ‘দুই দেহে এক প্রাণ’। এটা আসলে খুবই দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর কথা। সমাজের আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে আপনার স্বাধীনতা আর থাকবে না। মন চাইলেই কোনো একদিকে বেরিয়ে পড়তে পারবেন না। উদ্দেশ্যহীনভাবে দুনিয়ার যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবেন না।”
নিম্নস্তরের শিল্পসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি (vulgar aesthete) স্থূল সুখের পেছনে জীবন কাটিয়ে দেয়। অথচ বারবার একই ধরনের স্থূল আনন্দ খুব দ্রুতই মানুষকে তৃপ্ত করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে তার কাছে এসব বিরক্তিকর ও অর্থহীন মনে হয়। আসলে কেউ যখন নিজের আত্মসত্তার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন যে কোনো ধরনের স্থূল আনন্দকে জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা তার থাকে না।
কিয়ের্কেগার্দ অবশ্য নিম্নস্তরের শিল্পসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির চাইতে পরিশীলিত শিল্পসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির (refined aesthete) ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কারণ, এরাই হলো প্রকৃত আনন্দময়তার পূজারী। নন্দনতত্ত্বের দুনিয়ায় এরা হলো সর্বোচ্চ স্তরের আদর্শ ব্যক্তি।
‘আর্ট অব প্লেজারের’ একজন এক্সপার্ট হওয়ার কারণে পরিশীলিত শিল্পসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা আনন্দের নতুন নতুন উৎসগুলো পরখ করে দেখে। এ ধরনের ব্যক্তি নিছক আনন্দলাভের জন্য অন্যদেরকে পটিয়ে আড্ডা দেয়া, সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করা, ভ্রমণ করা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, ভালো ভালো খাবার খাওয়া – এসবের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এই আনন্দময়তার মধ্যে ডুবে থাকার সময়টা তার কখনোই ফুরাবে না মর্মে তার মাঝে এক অতি আশাবাদ তৈরি হয়।
আনন্দময়তার একজন প্রকৃত পূজারী হওয়ার কারণে একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সে তার খালাতো ভাই সম্পর্কীয় নিম্নস্তরের শিল্পসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির চেয়ে বেশি দক্ষ। তবুও তার মনের গহীনে এক ধরনের শূন্যতা চুপটি মেরে লুকিয়ে থাকে। যেসব আনন্দ বা সুখ জীবনকে অর্থপূর্ণ করেছে বলে সে মনে করে এসেছে, সেগুলোর তাৎপর্য আসলে কেবল আনন্দের ওই সময়গুলোতেই সীমাবদ্ধ। আনন্দলাভের একটি মুহুর্ত থেকে পরবর্তী মুহুর্তটির মাঝখানের সময়টুকুতে অন্য কোনো ধরনের কাজকর্মের প্রতি তার আগ্রহ থাকে না। সবকিছু তার কাছে তখন অর্থহীন মনে হয়।
“আমার কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। ঘোড়ায় চড়তে আমার ভালো লাগে না, কারণ এটা খুব জোরে ছোটে। হাঁটতে ইচ্ছা করে না, কারণ এটি খুব ক্লান্তিকার কাজ। শুয়ে থাকতেও আমার ভালো লাগে না। কারণ, হয় আমাকে শুয়েই থাকা লাগবে, নয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। এর কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। মোট কথা, আমার কোনো কিছুই ভালো লাগে না।” (Either Or, v.1, p.20)
অন্য সকল নন্দনতত্ত্বের মতো পরিশীলিত নন্দনত্ত্বও (refined aestheticism) শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে ব্যক্তিকে হতাশায় নিমজ্জিত করে। কিয়ের্কেগার্দের পরামর্শ হলো, শিল্পসত্তাসম্পন্ন কেউ যদি তার জীবনদর্শনের মাঝে শূন্যতা অনুভব করে, তাহলে সে যেন তার পথ পরিবর্তন করে নেয়।
কিয়ের্কেগার্দ বলেন,
“তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবন সম্পর্কে প্রতিটি নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণই আসলে দিনশেষে হতাশার জন্ম দেয়। এবং এক পর্যায়ে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যারা লালন করে তারা সবাই হতাশায় নিমজ্জিত হয়। হয়তো সে এটি জানে কিংবা জানে না। তবে যখন সে এটি টের পায় (একটা পর্যায়ে এসে এটি অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়ায়), তখন জীবনের স্বার্থকতা লাভের জন্য আরো উন্নত একটি পর্যায়ে পৌঁছা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।”
কিয়ের্কেগার্দের মতে, এই উচ্চতর পর্যায়ে এসে ব্যক্তি ‘নৈতিক স্তরে’ (ethical sphere) নিজেকে উন্নীত করে। মানুষের ভেতরকার সবচাইতে পবিত্র জিনিসটার (নৈতিকতা) সাথে তার পরিচয় ঘটে। এবং নৈতিকতাকে সে ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ক শক্তি বলে মনে করে। একজন নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি (ethicist) মনে করে, এর মাধ্যমে সে একটা সমন্বিত ও স্থায়ী পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সময়ের সাথে সাথে কতগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে গ্রহণ করে নেয়ার মধ্য দিয়ে সে এই কাজটি সম্পন্ন করে।
কিয়ের্কেগার্দ বলেছেন,
“সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় গ্রহণ করাটা ব্যক্তিত্বের জন্য খুব ক্রুশিয়াল একটি বিষয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব নিজেই এগুলোর মধ্যে একাকার হয়ে যায়। আবার এগুলো গ্রহণ না করলে ব্যক্তিত্ব ক্ষয় হতে হতে শুকিয়ে মরে যায়।”
একটা সমন্বিত আত্মপরিচয়ের (unified identity) খোঁজে আমজনতার মতো নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিও সমাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। সে অন্ধভাবে কোনো কিছু মেনে নেয় না। এভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ আত্মসচেতন থেকেই একজন নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করে।
প্রতিভা, স্বভাব ও আকাঙ্খার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও আত্মসচেতন ব্যক্তি হিসেবে সে নিজেকে সমাজের সাথে এমনভাবে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে, যাতে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে। সমাজবিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিবর্তে সে এমন এক সামাজিক সত্তা হয়ে ওঠতে চায়, যে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অন্যান্য সত্তার উপর নির্ভরশীল।
এ প্রসঙ্গে কিয়ের্কেগার্দের মত হলো,
“নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া নয়, বরং সামাজিক ও নাগরিক সত্তা হয়ে ওঠা হলো ব্যক্তিসত্তার (self) লক্ষ্য। ফলে সে তার ব্যক্তিত্বের কারণেই কতগুলো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে। এর মধ্য দিয়ে সে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।”
নন্দনতাত্ত্বিকের মতো তার জীবন প্রবৃত্তিতাড়িত নয়। নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে। সমাজের চোখে যা ভালো বা মন্দ, সেটাকে সে তার নিজের কর্মের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে। সামাজিক প্রথা ও দায়িত্ব পালনকে নিষ্পেষণমূলক ও সংকীর্ণতা বলে মনে হয় না। বরং এগুলোকে সে তার ভাবমূর্তি বিনির্মাণে কাজে লাগায়। নিজের স্বার্থ ও সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার মাঝে সে এক ধরনের সমন্বয় করে।
এ ধরনের নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হলো–
“আমি আমার পেশার জন্য, স্ত্রী-সন্তানের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আসলে আমি তাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি না, বরং এর মধ্যেই আমি মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দ খুঁজে পাই।” (Either Or)
সামাজিক মর্যাদা, অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ নৈতিকবোধসম্পন্ন ব্যক্তি বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করে বটে। অন্যদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তিও আদায় করে নেয় হয়তো। কিন্তু এতে তার ‘আত্মসত্তা (selfhood) অর্জিত হয় কিনা, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।
এ ধরনের নৈতিক জীবনদর্শনের অন্যতম সমস্যা হলো, প্রত্যেকটি সমাজেরই রীতিনীতি ও প্রথার মধ্যে কোনো না কোনো খুঁত থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা অত্যন্ত মারাত্মক হয়। নৈতিক ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক নৈতিকতাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে জীবনযাপন করে, তাই তার সমাজের ত্রুটিগুলো বুঝতে পারার মতো সুবিধাজনক অবস্থান তার থাকে না।
ফলে বিদ্যমান অসুস্থ সমাজে সে বেশ বেকায়দায় থাকে। একদিকে, এই সমাজে সে নিজেকে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, একজন স্বার্থক মানুষ হয়ে ওঠার জন্য এই সমাজ তার জন্য উপযোগী নয়। তাছাড়া জীবন সম্পর্কে নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি (ethicists’ sense of self) অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সাময়িক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার বিয়ে এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ।
“আমি আর আমার স্ত্রী মিলে একটি একক সত্তা। আমাদের দুজনের কোনো একজন আলাদাভাবে কিছুই নই। দুজনের সমন্বিত রূপটাই হচ্ছে আমাদের আসল রূপ।” (SLW 93)
অথচ মানুষ এক সময় মারা যায় এবং পার্থিব জিনিসও একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যক্তিসত্তাকে এ ধরনের একটা অস্থায়ী সম্পর্কে সমর্পণ করে দেয়ার মাধ্যমে সময়ের পরিক্রমায় ব্যক্তি তার আত্মসত্তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়ার স্থায়ী ঝুঁকিতে পড়ে যায়। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা (anxiety) হলো এমন এক শিক্ষক, যা মানুষকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষাটি দেয়:
“উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা করার মানে হলো, তার জন্য সম্ভাবনাও রয়েছে। সম্ভাবনার সকল পথের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়া একজন ব্যক্তির কথা ভাবুন। বর্ণমালা যেমন একটা বাচ্চার নখদর্পনে থাকে, তারচেয়েও ভালো করে সে বুঝতে পারে, জীবন থেকে তার পাওয়ার আসলে কিছুই নেই। এই আতঙ্ক, দুর্দশা ও ধ্বংস প্রতিটি মানুষের আশপাশেই ঘুরাফেরা করে। এ থেকে সবচেয়ে দরকারী যে শিক্ষাটি লোকেরা অর্জন করে, তা হলো– প্রতিটি সম্ভাব্য বিপদই পরমুহুর্তের বাস্তবতায় পরিণত হতে পারে। ফলে সে বাস্তবতাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখে।”
বৈষয়িক সফলতা অজর্নের পরেও একজন নৈতিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে– আত্মসত্তা (self) অর্জনের জন্য নৈতিক স্তরও অনুপযুক্ত, এরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; তখন তার মনে গভীর হতাশা জেগে ওঠে। এই প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতা অবশ্য ভালো লক্ষণ। কারণ, এই পরিস্থিতিতে সে চারদিকে অন্ধকার দেখে এবং মনেপ্রাণে মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। অবশেষে ব্যক্তিটি বিশ্বাসের আলোর সন্ধান লাভ করে। তার ভাষায়, “অনিবার্যভাবেই হতাশার বিপরীত জিনিসটি হলো বিশ্বাস।”
কিয়ের্কেগার্দের মতে, বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে ব্যক্তিটি ‘ধর্মীয় স্তরে’ (religious sphere) পৌঁছে যায় এবং জগতের অতিবর্তী এক সত্তার (transcendent source) কাছে নিজেকে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করে। এ পর্যায়ে ব্যক্তি নিজের মধ্যকার অসীম ও সসীম উপাদানের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় খুঁজে পায়। অবশেষে এর মাধ্যমে সে প্রকৃত আত্মসত্তা অর্জন করে।
“সম্পূর্ণভাবে হতাশা কেটে যাওয়ার পর ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা যায়: নিজের ভেতর আত্মস্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে সেই শক্তির কাছে পুরোপুরিভাবে সঁপে দেয়, যে শক্তি তার সত্তার উৎস। (Sickness Unto Death)
ধর্মীয় স্তরের ভেতর আবার একটা প্রাথমিক ধাপ রয়েছে। বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার আগে ব্যক্তিকে যা অবশ্যই পার হয়ে আসতে হয়।
এই পর্যায়ে ব্যক্তি জাগতিক সবকিছু পরিত্যাগ করে, সসীম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও নিস্পৃহ হয়ে অসীমের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণ জ্ঞাপনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে।
এভাবে জগতের সবকিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণেও ব্যক্তিকে প্রায় সময় গভীর বেদনা ও হতাশায় ভুগতে হয়। কিয়ের্কেগার্দ এই অবস্থাকে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এটি সেই ব্যক্তির ঘটনার মতো, যে কারো প্রেমে পাগলপারা হয়ে গেলো এবং পরবর্তীতে বুঝতে পারলো– এ ধরনের প্রেমের সম্পর্ক বাস্তবসম্মত নয়। এই কাল্পনিক প্রেমকে বাস্তবে রূপদান করা অসম্ভব ব্যাপার।
এই ধরনের উপলব্ধি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অসীম সত্তাকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে অগ্রগামী ব্যক্তিটি ‘অসীমের পথে যাত্রা’ শুরু করে। মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সে এক শাশ্বত সত্ত্বাকে ভালবাসতে শুরু করে।
পূর্বের সকল জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ব্যক্তি এই সসীম জগতে বাস করলেও তার জীবন থাকে অসীম জগতের সাথে সম্পর্কিত। সসীম জগতে যেন যে একজন আগন্তুক মাত্র। এর ভালোমন্দ তাকে স্পর্শ করে না।
অসীমতার প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণে অগ্রগামিতার এই পর্যায়ে এসেও ব্যক্তির বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে না।
সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে ওঠতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি ‘দ্বিমুখী তৎপরতার’ মধ্য দিয়ে যেতে হবে: (১) ক্ষণস্থায়ী ও জাগতিক সবকিছু পরিত্যাগ করে তাকে অবশ্যই ‘অসমীতার দিকে যাত্রা’ করতে হবে। (২) একইসাথে সসীমতার দিকেও তার যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। অর্থাৎ, সে যা কিছু পরিত্যাগ করেছে, তা এক সময় ফিরে পাবে– এই বিশ্বাসও থাকতে হবে। সর্বোচ্চ পার্থিব আকাঙ্খাগুলোও একসময় ফিরে পাবে, এ ব্যাপারে তার দৃঢ়বিশ্বাস থাকতে হবে।
যুক্তির বিচারে বিবেচনা করলে বিশ্বাস হলো ‘উদ্ভট’ বিষয়। কিন্তু ‘আধ্যাত্মিকতা যুক্তির শেকল থেকে মুক্ত’। এ পর্যায়ে বিশ্বাস যুক্তিকে অতিক্রম করে যায়। তখন ‘উদ্ভট’ তো আর উদ্ভট থাকে না। বিশ্বাসের ছোঁয়ায় তা বাস্তব হয়ে ওঠে।
ব্যাপারটা ঠিক ‘বিশ্বাসীদের পিতা’ ইবরাহীমের মতো। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে নিজ পুত্র ইসহাককে কুরবানী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে আল্লাহ তাঁর সন্তানকে এই দুনিয়াতেই আবার ফেরত দেবেন। একইভাবে একজন বিশ্বাসী অভিযাত্রিকও ক্ষণস্থায়ী সবকিছুকে পরিত্যাগ করে এবং একইসাথে এই সবকিছুই পুনরায় ফিরে পাওয়ার উপর বিশ্বাস রাখে। বরং আগের চেয়ে আরো বেশি করে ফিরে পাবে।
এ ব্যাপারে তিনি বলেন,
“নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবি থেকে সেই ধনী তরুণের উচিত ছিলো সবকিছু পরিত্যাগ করা। যদি সত্যিই সে তা করতো, তাহলে ‘নাইট অব ফেইথ’ এসে তাকে বলতো– অদৃশ্য শক্তির বলে তুমি সবকিছুই আবার ফিরে পাবে। বিশ্বাস করো!”
‘ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং’ বইয়ে কিয়ের্কেগার্দ একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর (knight of faith) সুনির্দিষ্ট কোনো উদাহরণ না দিলেও একটি ভাসা ভাসা চিত্র এঁকেছেন:
“এই তো তিনি! তার পরিচয় তো এখন উন্মোচিত! আমি তার দেখা পেয়েছি। প্রথমবার দেখামাত্রই তাকে চিনতে পেরেছি। এবং সাথে সাথে থমকে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রায় অনুচ্চারিত স্বরে বলে উঠেছি– ‘হায় ঈশ্বর! ইনি কি সত্যিই সেই ব্যক্তি! দেখতে তো একদম ট্যাক্স কালেক্টরের মতো লাগছে!’ তবে বাস্তবতা হলো, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি।”
কারণ ক্ষণস্থায়ী সবকিছু ত্যাগ করার পর মুহুর্ত থেকে সে আবার সেই ক্ষণস্থায়ী জগতেরই বাসিন্দা। এখন থেকে জগতের সাথে তার সম্পর্ক পরমসত্তা বা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত হয়েছে। বাহ্যিকদৃষ্টিতে ‘নাইট অব ফেইথকে’ আর দশটা সাধারণ গড়পরতা মানুষের মতোই মনে হবে। কিয়ের্কেগার্দ যাদেরকে ‘আমজনতা’ বলেছেন, তাদের মতো মনে হবে।
আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের বিশ্বাসী মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা করা অসম্ভব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তো সে অসীমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে এবং প্রতিনিয়ত সেই সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে। জগতের অতিবর্তী সত্তার (transcendent) সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অসীম ও অসীমের সাথে সে একটা আদর্শ সম্পর্ক তৈরি করেছে। একইসাথে সে পরমসত্তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক এবং আপেক্ষিকের সাথে সাময়িক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। এই জগতে সে বাস করে বটে, তবে সে নিছক এই জগতের কেউ নয়। তাই পার্থিব জগতের উপর সে নির্ভরশীলও নয়। এ কারণে পার্থিব বিষয়সম্পদ ও সম্পর্কগুলোকে সে অনায়াসেই উপভোগ করলেও এগুলো তার উপর চেপে বসতে পারে না। ফলে কোনো হতাশাও তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না।
“তার কাছে সসীম জিনিসের স্বাদ ঐ ব্যক্তির মতো যে কোনোদিন এর চাইতে উচ্চতর কোনোকিছুর সন্ধান পায়নি। কারণ তার সসীমের ভেতর থাকার যন্ত্রণা থেকে সে মুক্ত থাকবে। এছাড়া তার রয়েছে নিরাপত্তা। সেই নিরাপত্তা তাকে এমন প্রশান্তি এনে দেয় যেন সসীম বিষয়বস্তুই হচ্ছে সবচাইতে পরম বস্তু। সবকিছু চিরতরে ত্যাগ করার পর সে এসব আবার ফিরে পায় সেই অলীক শক্তির বলে (by virtue of the absurd)। অসীমের সাথে সে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। তবে তা এতোটা সুনিপুণ ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে করে, মনে হয় যেন সে সসীমের সাথেই সম্পর্ক রক্ষা করছে। এর ব্যতিক্রম অন্য কিছু যে তার ভেতরে ক্রিয়াশীল আছে, বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারে না।” (Fear and Trembling)
যেহেতু ঈশ্বর বা পরমসত্তার অস্তিত্বের কোনো ‘প্রমাণ’ নেই, তাই ‘নাইট অব ফেইথের’ ধারণাটি সম্পর্কে এক ধরনের অস্পষ্টতা থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিয়ের্কেগার্দও তা স্বীকার করে নিয়েছেন–
“ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার আশায় আমি প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছি। ফলে আমি সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় এক সত্তাকে উপলব্ধি করেছি। অবশ্য কিছুটা খুঁতখুঁতে ভাবও আমার মধ্যে কাজ করে। মোট কথা, এটি এক ধরনের নৈর্বক্তিক অনিশ্চয়তা (objective uncertainty)।”
ধারণাগতভাবেই একটি ‘নৈর্বক্তিক অনিশ্চয়তা’ থাকায় ঈশ্বর বা পরমসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনোই নিশ্চিত বস্তুগত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। মানবীয় বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাকে পাওয়া অসম্ভব। তাই বিশ্বাসী হয়ে বেঁচে থাকাটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ সবসময়ই প্রতারিত হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায়।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,
“ঝুঁকি ছাড়া কোনো বিশ্বাস হয় না। ব্যক্তির ভেতরকার অসীম আবেগ ও নৈর্বক্তিক অনিশ্চয়তা – এই দুটির মধ্যকার অসঙ্গতি বা বৈপরীত্যই হলো মূলত বিশ্বাস। ঈশ্বরকে নৈর্বক্তিকভাবে বুঝার ক্ষমতা থাকলে তো মানুষের বিশ্বাস করারই আর প্রয়োজন থাকে না। আমি যদি আমার বিশ্বাসকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে আমাকে অবশ্যই ‘নৈর্বক্তিক অনিশ্চয়তাকে’ মেনে নেয়ার ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে। এর মানে হলো, অতল সাগরের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান অবস্থায়ও আমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে– সৃষ্টিকর্তা চাইলে আমাকে বাঁচাতে পারেন।”
বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের (Divine) সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এ ধরনের সম্পর্ক ‘একক ব্যক্তিসত্তার’ মধ্যে কেবল ধর্মীয়ভাবেই ধারণ করা সম্ভব। “সবসময় কেবল একজন ব্যক্তি বা একক ব্যক্তিসত্তার উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের আহ্বানগুলো করা হয়। এই আহ্বান শুনে অন্য কেউ আসলো কি আসলো না, তা পরোয়া না করেই ঈশ্বরের পথে কে এগিয়ে যায় – এর মাধ্যমে যে সেই পরীক্ষা করা হচ্ছে, তা নিশ্চিত।” (JP, I, p. 100)
কাউকে সাথে পাওয়া যাক বা না যাক, ঈশ্বরের পথে যে একাই এগিয়ে যায়, সে-ই ‘ব্যক্তিসত্তা’ (self) অর্জন করে। এটি তার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। “এটিই তার কাছে সময়ের শাশ্বত দাবি।” এর মাধ্যমে ব্যক্তি স্বীয় ব্যক্তিসত্তার গহীন থেকে অস্থিরতা দূর সক্ষম। এবং এভাবে সে একজন পরিপূর্ণ বোধসম্পন্ন স্বাধীন সত্তায় পরিণত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে মানুষ হিসেবে সফলতা অর্জন করে।
যখন সব কথা বলা হয়ে যায়, সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, জীবনমঞ্চের পর্দা টানা হতে থাকে, তখনো “তার নিকট মহাকালের দাবি হলো– সে যেন একজন স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিসত্তা হিসেবে বেঁচে থাকে।” নিজেকে নিবিড়ভাবে পরমসত্তার নিকট পুরোপুরি সঁপে দেয়ার মাধ্যমেই কেবল এটি অর্জন করা যেতে পারে।
“আপনি নারী বা পুরুষ, ধনী বা গরীব, স্বাধীন বা পরাধীন, সুখী বা অসুখী – যাই হোন না কেন; সোনার চামচে খেতে খেতে বিরক্ত, কিংবা নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা – আপনার অবস্থা যাই হোক না কেন; চিরদিন আপনার নাম স্মরণ করা হোক, কিংবা হাজারো মানুষের ভীড়ে আপনি অচেনা, অজ্ঞাত হিসেবে জীবন পার করে দেয়া কেউ একজন; আপনি এবং কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেকে মহাকালের পরিক্রমায় একটিমাত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন– জীবনের শেষ পর্যন্ত কি তোমার মাঝে হতাশা ছিলো, নাকি ছিলো না? যদি থেকে থাকে, তাহলে তুমি যা কিছু অর্জন করেছো বা হারিয়েছো, তার সবই বৃথা।” (Sickness Unto Death)