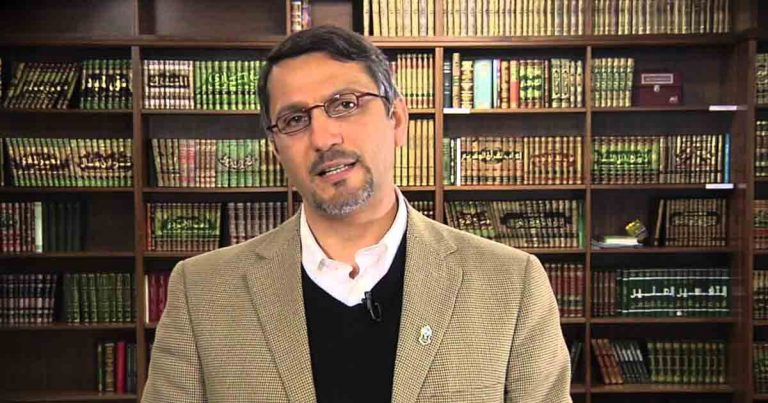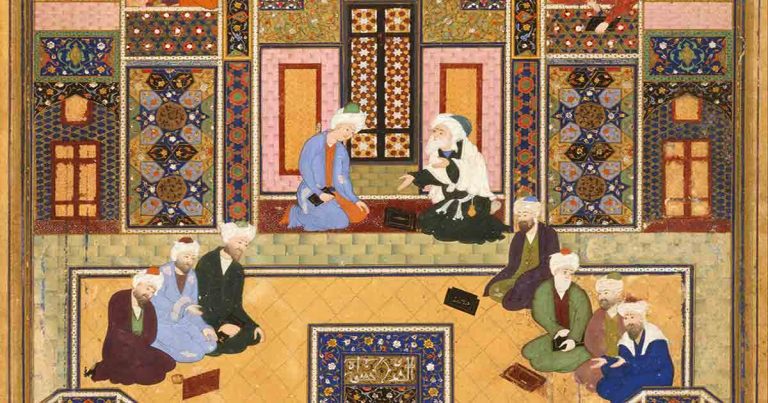দর্শন যেভাবে আমার জীবন বাঁচালো
এডিটর’স নোট: জুলস ইভান্সের জীবনের গল্পটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। উঠতি বয়সে তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকের জীবনই এভাবে শেষ হয়ে গেছে। তিনিও সে পথেই আগাচ্ছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হন। তাঁর নতুন জীবনের পথ চলায় দর্শন কীভাবে ভূমিকা রেখেছে, ২০১৩ সালে টেড টকের এক প্রোগ্রামে সেই গল্পটিই তিনি দর্শকদের সামনে বলেছেন। সিএসসিএস পাঠকদের জন্য এটি ভাষান্তর করেছেন আইয়ুব আলী।
***
আধুনিক কগনিটিভ বিহেভিয়োরাল থেরাপির (CBT) পেছনে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের অবদান নিয়ে এখন আমি কিছু বলতে চাই। সিবিটির মাধ্যমে বর্তমানে অসংখ্য মানুষ প্রাচীন গ্রিকদের প্রজ্ঞার সাথে পরিচিত হতে পারছে। আমাদের আত্মিক উন্নয়নে দর্শন সাহায্য করে– সক্রেটিসের এই বক্তব্যের তাৎপর্য আমরা এখন বুঝতে পারছি। যা হোক, আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে দর্শন আমাকে কীভাবে সাহায্য করেছে, সেই গল্পটা এবার বলা যাক।
তখন নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়। আমাদের কৈশোর কাল। বলতে পারেন, আমি ও আমার বন্ধুরা ছিলাম অতি উৎসাহী ‘নিউরো সায়েন্টিস্ট’। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে আমরা আমাদের ব্রেইনের উপর বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতাম। শুরুটা হয়েছিলো গাঁজা সেবনের মাধ্যমে। এর ফলাফল ছিলো বেশ ইন্টারেস্টিং। তারপর এলএসডি গ্রহণ শুরু করলাম। তারপর ধীরে ধীরে এমডিএমএ, এমফেটামিনস, কেটামিন, ম্যাজিক মাশরুম ইত্যাদিতে আমরা অনেক বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। এগুলো আমাদের নিউরাল কেমিস্ট্রিকে উলটপালট করে দিয়েছিলো। আমাদের মনে হতো, আমরা অসাধারণ একটি সময় পার করছি। আমরা তখন হাস্যকর সব কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। এমনকি আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছে গেছি বলেও আমাদের মনে হতো।
এরপরেই ধাক্কাটা আসলো। চোখের সামনে আমার ফুর্তিবাজ বন্ধুরা একে একে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো। নেশা করতে করতে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলো। ফলে তাকে আটকে রাখতে হতো। অথচ তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১৬ বছর। ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পরে তার প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে। আমার অন্যান্য বন্ধুরা ততদিনে বাইপোলার ডিজঅর্ডার, বিষণ্নতা, দুঃশ্চিন্তা, মস্তিস্কবিকৃতি ইত্যাদিতে ভুগতে শুরু করে। এক পর্যায়ে আমার নিজেরও প্যানিক অ্যাটাক শুরু হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মাত্র ফার্স্ট টার্ম চলছিলো। প্যানিক আ্যাটাক সম্বন্ধে তখন আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। আমি শুধু বুঝতে পারতাম যে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ছি। এক ধরনের প্রচণ্ড ভীতি আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আমার আত্মবিশ্বাস তখন একদম তলানীতে। কারণ, তখন আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার আগামীকালটা কেমন যাবে। ফলে আমি আরো বেশি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। কারণ, কখন, কোথায়, কার সামনে আমার প্যানিক অ্যাটাক শুরু হবে এবং আমাকে লজ্জায় ফেলে দেবে, তা আগে থেকে বুঝার উপায় ছিলো না।
তবে সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটি ছিলো, ততদিনে আমার মস্তিষ্কের কিছু স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে। আমার তখন যে অবস্থা, তাতে এ ব্যাপারে হয়তো আমার কিছুই করার ছিলো না। মনে হতো, ২১ বছর বয়সের আগেই আমি আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দিনকে দিন আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আমার এই চরম শোচনীয় পরিস্থিতে আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করি। তারপর আমি অর্থনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করি। আমার কাজ ছিল জার্মানির মর্টগেজ বন্ড মার্কেট নিয়ে রিপোর্ট করা। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা কারো এরচেয়ে ভালো আর কোন চাকরিটা জুটতে পারে…!
আমার বাবা-মা আমাকে একজন নামিদামি থেরাপিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, আমি সোশ্যাল এংজাইটি, বিষণ্নতা এবং পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছি। আমার ধারণা, প্রতিটি রোগ নির্ণয়ের জন্য তাকে আলাদা করে ফি দিতে হয়েছে। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারেননি। তাই আমি নিজেই সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে বুঝতে পারলাম, কগনিটিভ বিহেভিয়োরাল থেরাপি তথা সিবিটির মাধ্যমেই এসব সমস্যার কিছুটা নিরাময় হয়তো সম্ভব।
সোশ্যাল এংজাইটিতে আক্রান্তদের জন্য লন্ডনের একটি সিবিটি সাপোর্ট গ্রুপ সম্পর্কেও জানতে পেরেছি, যারা প্রতি বৃহস্পতিবার আমার বাসার খুব কাছেই বসতো। এক বৃহস্পতিবারে আমি সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, ১০ জন লোক গোল হয়ে বসে আছে। সেখানে কোনো পেশাদার থেরাপিস্ট ছিলো না। তবে সেই গ্রুপের কেউ একজন ইন্টারনেট থেকে সোশ্যাল এংজাইটির উপর একটি সিবিটি কোর্স অবৈধভাবে ডাউনলোড করে এনেছে। আমরা কোর্সটি শোনতাম, এক্সারসাইজগুলো প্র্যাকটিস করতাম, হোমওয়ার্কগুলো ঠিকঠাক মতো করতাম এবং পরস্পরকে উৎসাহ দিতাম। অন্যদের কথা জানি না, তবে আমার ক্ষেত্রে এটা বেশ ভালোই কাজে দিয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি প্যানিক অ্যাটাক থেকে আরোগ্য লাভ করি। আবেগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটিও আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করি।
এসব কার্যকারিতা দেখে সিবিটি নিয়ে আমার মধ্যে ঔৎসুক্য বাড়তে থাকলো। এর উৎপত্তি নিয়ে আমি ভাবতে থাকলাম। এক পর্যায়ে জানতে পারলাম, সিবিটির উদ্ভাবক হলেন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী আলবার্ট এলিস। তিনি তখন নিউ ইয়র্কে থাকতেন। ২০০৭ সালে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমি নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলাম এবং তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি ততদিনে ৯২ বছর বয়সের অশীতিপর বৃদ্ধ, রোগেশোকে অত্যন্ত দুর্বল। দুঃখজনকভাবে, সেটাই ছিলো তাঁর দেয়া জীবনের শেষ সাক্ষাৎকার। এর কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান। এই থেরাপি উদ্ভাবনের জন্য আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। কারণ, এর ফলেই আমার জীবন বেঁচে গেছে।
যা হোক, আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সিবিটির ধারণা তিনি কীভাবে পেলেন। জবাবে তিনি বললেন, পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডীয় ধারার একজন সাইকো-এনালিস্ট। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তাঁর রোগীদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি না হওয়ায় তিনি বেশ হতাশ ছিলেন। মানুষের আবেগ-অনুভূতিগুলোকে বুঝার জন্য তিনি তখন ভিন্ন উপায় খুঁজতে লাগলেন। এরই এক পর্যায়ে তিনি প্রাচীন গ্রিক দর্শনে ফিরে গেলেন। এটি ছিলো একসময় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। বিশেষ করে নির্বিকারবাদী (stoic) দার্শনিক এপিকটেটাসের একটি লাইন তাঁকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল। এপিকটেটাস বলেছেন: “নিছক কোনো ঘটনা নয়; বরং ঘটনা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিই তার মনে বিশেষ অনুভূতির জন্ম দেয়।” এলিস প্রদত্ত মানবীয় আবেগ সংক্রান্ত ABC থিওরির পেছনে এই উক্তিটিই প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো। এবিসি থিওরির A দিয়ে বুঝায় Activating events, অর্থাৎ আমাদের জীবনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়া। B দিয়ে বুঝায় Beliefs তথা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস। অর্থাৎ, ঘটনাকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি। আর C দিয়ে বুঝায় Consequent emotion, অর্থাৎ ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের অনুভূতির যে ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা যে ধরনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাই, সেগুলো হয়তো স্বয়ংক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে যায়। ব্যাপারটি হয়তো নিছক একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।
মনে করুন, আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম, একজন লোক আমাদের দিকে ভ্রু কোঁচকে তাকিয়ে আছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বভাবতই আমরা অপমানিত বোধ করি এবং রেগে যাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, আমরা বুঝি A থেকে সরাসরি C-তে চলে গেছি।
কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখবেন, ঘটনাটিকে আপনি আসলে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি ভেবেছেন, “লোকটি বুঝি আমার দিকেই ভ্রু কোঁচকে তাকিয়ে আছে। কিছু মানুষ আমাকে সবসময় অবজ্ঞা করে। এটি অত্যন্ত অমার্জিত ও অশোভন কাজ। যা করা একদম উচিত নয়।”
সত্যি বলতে কী, এভাবে চিন্তা করার ফলেই আপনি অপমানবোধ করেন, রেগে যান। দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটি বুঝতে পারলেই আমরা নিজেদের চিন্তার যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারবো। যেমন আমরা নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারি, লোকটি কি আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলো? লোকটি হয়তো এমনিতেই ভ্রু কোঁচকে ছিলো। আর লোকটি যদি আমার দিকেই তাকায়, তাতেই বা কি আসে-যায়? এ নিয়ে ভেবে ভেবে আমিও কি তার মতো মন খারাপ করে সারাটা দিন পার করবো?
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরো উদার হওয়া উচিত, তাহলে আমাদের আবেগ-অনুভূতির উপরও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ব্যাপারটি শুনতে খুব সোজা মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা অতটা সহজ নয়। কারণ, আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো সবসময়ই অবচেতনে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে। আমাদের মনের ভেতর সবসময়ই একটি অদৃশ্য কণ্ঠ সক্রিয় থাকে। আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ব্যাপারে এটি নানা ধরনের জাজমেন্ট দিতে থাকে। মনের সাথে এটি সর্বদাই কথা চালিয়ে যেতে থাকে। আমরা সাধারণত মনের গহীনের সেই কথাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করি না। এমনকি প্রায় সময় আমরা এটা বুঝতেও পারি না। শৈশব থেকে এ পর্যন্ত আমরা যত ধরনের মতামত ও ধ্যানধারণা শুনে এসেছি, সেইসব মিলেই আসলে আমাদের ভেতরের এই সত্তাটা তৈরি হয়। আমরাও সেই বিশ্বাস বা চিন্তাচেতনাকে কোনো প্রকার প্রশ্ন না করেই গ্রহণ করে নেই। আমরা ধরেই নেই, আমাদের ভেতরকার এই সত্তাটির বলতে থাকা সিদ্ধান্তমূলক মতামতগুলো সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও সত্য। তবে বাস্তবতা হলো, এটি তা নয়। বরং এটি প্রায় সময়ই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে।
এই অদৃশ্য কণ্ঠটিকে আপনি টুয়েন্টি-ফোর আওয়ার নিউজ চ্যানেলের সাথে তুলনা করতে পারেন, যেটি আপনার জীবনযাপন সম্পর্কে বিরামহীনভাবে মন্তব্য করে যাচ্ছে। অথচ সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট ও বিকৃত। এটি কখনোই সত্যকে পুরোপুরি যাচাই করে দেখে না। এখন আপনার যদি বিষণ্নতার মতো কোনো ইমোশনাল সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, আপনার সেই অদৃশ্য কণ্ঠ বা সত্তাটি সবসময় শুধু নেতিবাচক দিকটিই তুলে ধরে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি হয়তো ভাবেন– সবাই আপনাকে অপছন্দ করে, কিংবা, আপনি যাই করতে যান সেখানেই ব্যর্থ হন।
গ্রিকদের মতে, আমাদের বিশ্বাস বা চিন্তাচেতনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ। আমরা আমাদের স্বীয় কারাগারে বন্দি। আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করি। আমাদের নেতিবাচক ও ক্ষতিকর ধ্যানধারণাগুলো যদি আমাদেরকে নানাভাবে কষ্টেও ফেলে দেয়, এমনকি মৃত্যু মুখে পর্যন্ত ঠেলে দেয়; তবু আমরা সেগুলো আঁকড়ে ধরে থাকি।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেদের তৈরি এই কারাগার থেকে আমরা কীভাবে মুক্তিলাভ করতে পারি? গ্রিক দর্শনের জনক সক্রেটিস এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। তার মতে, নিজেকে প্রশ্ন করা শিখতে হবে। আমাদের ভেতরের সত্তাটি যা বলে সেটাকে ধ্রুব সত্য মনে না করে, বরং সত্তাটিকে কীভাবে একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় নিয়ে আসা যায়, তা আয়ত্ব করতে হবে। এথেন্সে সক্রেটিস তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে এ বিষয়টি শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাদের বাছবিচারহীন বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন নিয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। একইভাবে, আপনি যদি একজন কগনিটিভ থেরাপিস্টের কাছে যান, তিনিও আপনাকে একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় এনগেজ করে ফেলবেন। তিনি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবেন, যাতে আপনি আপনার ধ্যানধারণাগুলো যাচাই করতে পারেন।
চাইলে আপনি নিজেও এটি করে দেখতে পারেন। এ জন্য আপনাকে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে। তারপর নিজের তৈরি কারাগার তথা নিজস্ব ধ্যানধারণার শেকলে যে আপনি বাধা পড়ে আছেন, তা বুঝতে হবে।
আমাদের কি নিজেদের উপর সত্যিই কোনো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবো, তা কি আমরা আসলে নিজেই ঠিক করি? আমরা কি আদৌ আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, ডিএনএ, শৈশব এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি?
এই জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর পেতে হলে দার্শনিক এপিকটেটাস সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদেরকে বলা দরকার। তিনি ছিলেন প্রথম খ্রিষ্টাব্দের মানুষ। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন দাস। তাঁর নামের অর্থ হলো ‘অর্জিত’। নিজেদের অবস্থা ও জীবনযাপনের উপর তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের দাসদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না বললেই চলে। তা সত্ত্বেও আত্মার মুক্তি ও প্রশান্তি নিয়ে এপিকটেটাস যে দর্শনভাবনার জন্ম দিয়েছিলেন, তা আজ পর্যন্ত অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ধারণা।
তিনি আমাদেরকে আত্মার মুক্তি সংক্রান্ত যে দর্শন দিয়ে গেছেন, তার মূলকথা হলো, জীবনের সবকিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– (১) যে বিষয়গুলোকে আমরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এবং (২) যে বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এ দুটির পার্থক্য বুঝতে পারার মধ্যেই মানসিক প্রশান্তির মূলমন্ত্র নিহিত।
এখন তাহলে ভাবুন তো, জীবনের কোন বিষয়গুলোর উপর আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই? এপিকটেটাসের মতে, আবহাওয়া, সরকার ও অর্থব্যবস্থার উপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্য কাউকেও আমরা আসলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। অন্যদের উপর আমাদের কিছুটা প্রভাব হয়তো থাকে, কিন্তু তারপরও অন্যরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই থেকে যায়। এমনকি নিজ দেহের নিয়ন্ত্রণও আমাদের হাতে পুরোপুরি নেই। যেমন, আমরা সুস্থ্ থাকতে চাই। সুস্থ্ থাকার চেষ্টা করা উচিতও বটে। কিন্তু তারপরও আমরা কখনো কখনো অসুস্থ হই, আহত হই, বৃদ্ধ হই এবং একসময় মারাও যাই। আবার ধরুন, আমরা অনলাইনে সবসময় আমাদের সুনাম ধরে রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা সবসময় তাতে সফল হই না। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও আমাদের হাতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নেই।
তাহলে কোন বিষয়ের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? এপিকটেটাসের মতে, একটিমাত্র বিষয়ই আমরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সেটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা ধ্যানধারণা। তিনি মনে করতেন, যাবতীয় ইমোশনাল সমস্যার পেছনে মানুষের দুটি ভুল সচরাচর দায়ী– (১) যে বিষয়গুলো আদতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে মানুষ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক জীবনকে নিজের মনমতো করে পরিচালনা করার এক প্রকার বেপরোয়া আকাঙ্খা তাদের মধ্যে কাজ করে। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন তারা হতাশ, অসহায় ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। (২) নিজেদের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সামাজিক জীবনের কোনো ব্যাপারকে তারা অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়। এক্ষেত্রে তারা সাধারণত বলে: ‘এই এই কারণে আমি ওই কাজটা করতে পারিনি, আমার আর কোনো উপায় ছিলো না।’ ইত্যাদি ইত্যাদি।
আমার নিজের কথাই বলি। আমার যখন সোশ্যাল এংজাইটির সমস্যা ছিলো, তখন অন্যরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে সেটা নিয়েই আমি সবসময় চিন্তিত থাকতাম। আমি তখন মনে করতাম, অন্যদের অবশ্যই উচিত আমার কাজকর্মকে মেনে নেয়া। কিন্তু লোকেরা তা না করলে আমি একদম ভেঙ্গে পড়তাম। এ ধরনের লাগামহীন চিন্তাভাবনাই আসলে তখন আমার নিঃসঙ্গবোধ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি নিজেকে বাহ্যিক কোনোকিছু কিংবা অন্যদের মতামতের দাস বানিয়ে ফেলেছিলাম। অথচ এর প্রতিকার সর্বদা আমার হাতেই ছিলো। আমি চাইলে যেকোনো সময়ই নিজেকে বলতে পারতাম– ‘আমি চাই অন্যরা আমাকে পছন্দ করুক। কিন্তু পছন্দ করা বা না করার ব্যাপারটা বলতে গেলে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তা সত্ত্বেও আমাকে আমার মতো করেই আমি গ্রহণ করবো এবং লোকনিন্দার পরোয়া না করে সঠিক কাজটিই করে যাবো।’ এভাবে ভাবতে পারলে আমার দুশ্চিন্তা বেশ কমে যেতো, নিজের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতাম। সর্বোপরি, আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রশান্তি লাভ করতাম।
এখন আমার এই টেড টক শুনে হঠাৎ আপনার উপলব্ধি হলো, ‘এখন আমি বুঝতে পারলাম কীভাবে বাঁচতে হয়।’ এ ধরনের সাময়িক উপলব্ধির সমস্যা হলো, এর ফলে আপনি হয়তো কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য নিজেকে পাল্টাতে পারবেন। তারপর আপনি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন। কারণ, আমরা আসলে অনেক বেশি ভুলোমনা। সক্রেটিসের মতে, আমাদের মধ্যে অবাস্তব কল্পনার জগতে বাস করার প্রবণতা রয়েছে।
আমরা কি সত্যিই আমাদেরকে বদলাতে পারি? এটি আসলে একটি দার্শনিক প্রশ্ন। মানুষ যে কতটা অভ্যাসনির্ভর প্রাণী, গ্রীকরা তা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো। তারা আরো বুঝতে পেরেছিলো, নিজেদের পরিবর্তনের জন্য আমরা যদি দর্শনের সাহায্য নেই, তাহলে সেটি শুধু চমৎকার সব আইডিয়াই দিবে না, আমাদের জীবনের একটি কার্যকর অভ্যাসেও পরিণত হবে। আর তাই গ্রিক ‘ethics’ শব্দটি ‘ethos’ তথা অভ্যাসের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
কোনো অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে গ্রিকদের অনুসৃত কৌশলগুলো সম্পর্কে এবার কিছুটা বলা যাক। যেমন, তাদের কথাবার্তায় প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ছিলো। সহজে আয়ত্ব করার জন্য তারা তাদের দার্শনিক ভাবনাগুলোকে নানা ধরনের প্রবাদ, প্রবচন ও মন্ত্র হিসেবে চর্চা করতো। যেমন, ‘নিজেকে জানো’, ‘সর্বক্ষেত্রে সংযমী হও’ প্রভৃতি বাক্যগুলো ছাত্ররা উচ্চস্বরে বারবার পড়তো; যতক্ষণ না সেগুলো তাদের সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়। এছাড়াও তারা সেগুলো একটা খাতায় লিখে রাখতো যা ‘enchiridion’ নামে পরিচিত। সবসময় সেটি তাদের সাথেই থাকতো।
সিবিটির পদ্ধতিও অনেকটা একই রকম। এখানেও আপনি নিজেকে অটো সাজেশন দিতে থাকবেন, যতক্ষণ না সেটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়।
গ্রিকদের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিলো ডায়েরি রাখা। দর্শনের শিক্ষার্থীরা দিনশেষে তাদের কৃত ভালো-মন্দগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখতো। অবাস্তব কল্পনার জগতে বাস করা বলতে সক্রেটিস বুঝিয়েছিলেন– আমরা কী করি, আমরা আসলে কারা, তা আমরা সাধারণত উপলব্ধি করি না। এক্ষেত্রে ডায়েরি আমাদেরকে সাহায্য করে। আমাদের সারাদিনের কর্মকাণ্ডের একটি বিবরণ ডায়েরিতে পাই। একইসাথে আমাদের অগ্রগতির একটা চিত্রও আমরা সেখান থেকে পাই। এ ব্যাপারে এপিকটেটাস বলেছেন, আপনি যদি বদমেজাজ ত্যাগ করতে চান, তাহলে দেখুন কতদিন পর্যন্ত আপনি নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। আপনি যদি টানা ৩০ দিন এটি করতে পারেন, তাহলে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে ধরে নিতে পারেন।
সিবিটির কৌশলও অনেকটা ডায়েরি রাখার এই পদ্ধতির কাছাকাছি।
তৃতীয় যে পদ্ধতিটি গ্রিকরা অনুসরণ করতো সেটি হলো ফিল্ডওয়ার্ক। নিছক তাত্ত্বিকভাবে কোনো দর্শনকে গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়, বরং এর বাইরে গিয়ে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ করাটাও জরুরি। এপিকটেটাস তার ছাত্রদের বলতেন: শ্রেণীকক্ষে তোমরা হয়তো ভালো শ্রোতা, কিন্তু বাস্তবজীবনে কোনো ইস্যু মোকাবেলা করতে গিয়ে তোমাদের শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই জীবনের নানান ধরনের পরিস্থিতি সামলানোর জন্য অনুশীলনের বিকল্প নেই।
একইভাবে সিবিটিতেও আপনার চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের উপরই শুধু গুরুত্ব দেওয়া হয় না। একইসাথে আপনার বিহেভিয়্যার তথা আচার-আচরণের পরিবর্তনের উপরও অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। এজন্যই একে বলা হয় ‘কগনিটিভ বিহেভিয়োরাল থেরাপি’।
সোশ্যাল এংজাইটি কাটিয়ে উঠার জন্য আমার ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাভাবনাগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করা জরুরি ছিলো। তবে সে জন্য নিছক থেরাপি কক্ষের অনুশীলনই যথেষ্ট ছিলো না। আমাকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে হয়েছে। যেমন, আমাকে পার্টিতে যেতে হয়েছে, মানুষের সামনে কথা বলার অভ্যাস করতে হয়েছে; যেন একদিন আজকের মতো সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি।
প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমানে গ্রিক পদ্ধতিগুলোর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভার্শন থাকার পরেও আমাদের কি আর প্রাচীন দর্শনের দরকার আছে? এখন আমাদের যেহেতু সিবিটি রয়েছে, তাই গ্রিকদের কাছে ফিরে যাবার আর প্রয়োজন নেই বলে আমাদের মনে হতে পারে। তবে আমি মনে করি, দুটি কারণে প্রাচীন দর্শনের কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।
প্রথমত, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্যকর্মগুলো ছিলো অসাধারণ। প্লাটো, সেনেকা, মার্কাস অরেলিয়াস এবং এপিকটেটাসের মতো দার্শনিক ও লেখকের অনন্যসাধারণ কর্ম দ্বারা পশ্চিমা সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাঁদের লেখালেখির সৌন্দর্যের কারণে এখনো সেগুলো বেশ সমাদৃত।
দ্বিতীয়ত, আবেগজনিত সমস্যাগুলোর সমাধানে সিবিটি একটি চমৎকার স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটি কিছু কিছু বিষয় উপেক্ষা করে গেছে। সদগুণাবলির ব্যাপারটিকে এখানে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। উত্তম চরিত্র, সুন্দর জীবন, সফল ক্যারিয়ার, ভালো বন্ধু, কিংবা একটি সুন্দর সমাজ বলতে আসলে কী বুঝায়? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা সিবিটিতে খুঁজে পাই না। এছাড়া জীবনের মৌলিক কিছু প্রশ্নও সিবিটি এড়িয়ে গেছে। জীবনের মানে কী? জীবনে সফল হওয়া বলতে আসলে কী বুঝায়? উন্নত জীবন, সুন্দর সমাজ বলতে আসলে কী বুঝায়, এ জাতীয় মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিকরা দিয়ে গেছেন। যদিও তারা সবাই একই রকম উত্তর দেননি।
প্লাটোর মতে, স্রষ্টার অনুগামী জীবনই উত্তম। এপিকিউরাস মনে করতেন, পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও সুখে-শান্তিতে বসবাস করার নামই সুন্দর জীবন। এরিস্টটলের মতে, সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত জীবনই হলো সুন্দর জীবন।
‘সুন্দর জীবন বলতে কী বুঝায়?’ এই প্রশ্নটির উত্তরে মনোবিদ্যা একটিমাত্র উত্তরকেই সঠিক বিবেচনা করবে বলে আমি মনে করি না। বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর কখনোই দিতে পারবে না। ঠিক এ কারণেই দর্শনের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। একই কারণে আমাদের স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোম্পানিগুলোতেও আরো বেশি ব্যবহারিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা যেন শুধু নিজেদেরকে পরিবর্তন করার কিছু কলাকৌশল জেনেই ক্ষান্ত না হই। বরং একটি সুন্দর জীবনযাপন করা বলতে আসলে কী বুঝায়, সেই প্রশ্নটি করাও যেন আমরা শিখতে পারি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিনির্মাণে দর্শন আমাদের পথ দেখাতে পারে। ধন্যবাদ।