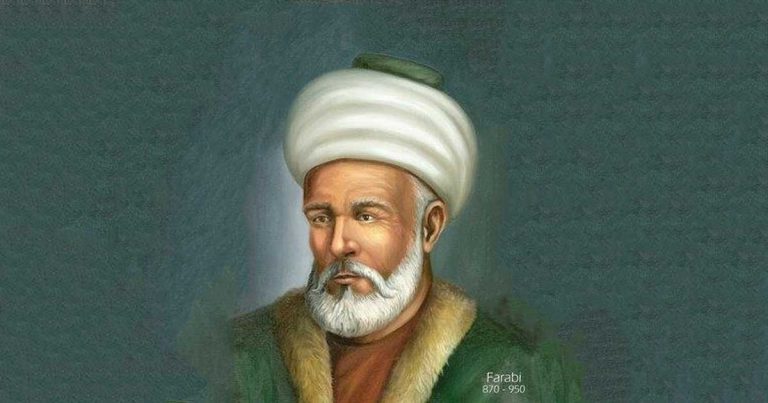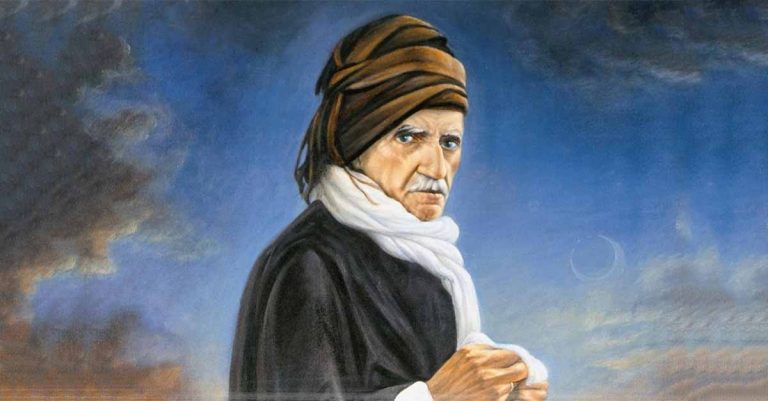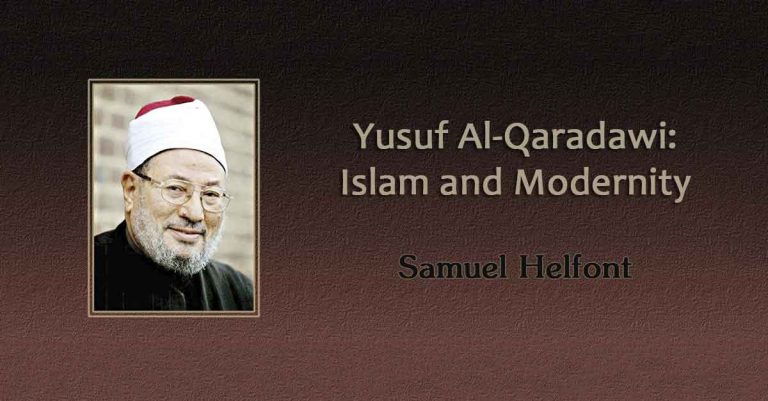দ্য লাইফ অব মোহাম্মদ
এডিটর’স নোট:
২০১১ সালে বিবিসিতে প্রচারিত হয় মহানবীর (সা) জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি ‘দ্য লাইফ অব মোহাম্মদ’। তিন পর্বের এই ডকু-ফিল্মটি সম্প্রচারের পর পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত হয়। এই প্রথম কোনো পাশ্চাত্য মিডিয়া মহানবীর (সা) জীবনীর উপর পূর্ণাঙ্গ কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলো। ডকুমেন্টারিটির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন ব্রিটিশ স্কলার জিয়াউদ্দীন সরদার। উপস্থাপনা করেছেন ব্রিটিশ সাংবাদিক রাগেহ ওমর। ক্রিসেন্ট ফিল্মস নির্মিত ডকুফিল্মটির পরিচালনা করেছেন ফারিস কেরমানী। মহানবীর (সা) জন্মস্থান মক্কা, হেরা গুহাসহ ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে উপস্থাপক দর্শকদের নিয়ে গেছেন। পক্ষ-বিপক্ষের স্কলারদের প্রচুর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। মহানবীর (সা) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাশ্চাত্য একাডেমিয়াতে সাধারণত যেসব প্রশ্ন তোলা হয়, এখানে ধরে ধরে সেসব ‘আপত্তি’ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সিএসসিএস-এর পাঠকদের জন্য এটি অনুবাদ করছেন মাসউদুল আলম।
*****
ভূমিকা
চৌদ্দশ বছর আগে বর্তমান সৌদি আরবের মক্কায় একজন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দেয়া এই ব্যক্তিটি প্রায় দেড়শ কোটি মুসলমানের নিকট সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, যিনি মানবজাতির কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তিনি একটি ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, যার নাম ইসলাম। তাঁর মৃত্যুর পর এটি একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিসেবে গড়ে ওঠে, যা কালক্রমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের অনেকগুলো আশ্চর্য সুন্দর স্থাপত্যশিল্প এই সভ্যতার হাত ধরে গড়ে ওঠেছে।
সে যাই হোক, বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে একাধিক নজিরবিহীন সন্ত্রাসী হামলার সাথে মোহাম্মদের (সা) নামকে জড়ানো হয়েছে।
মুসলমানদের কাছে তিনি হলেন অনুসরণীয় চূড়ান্ত আদর্শ। তাঁর বিস্তারিত জীবনীও মুসলমানরা জানে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বাইরে বলতে গেলে কেউই তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। তাই তিনি আসলে কে, তিনি কী বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ কেন তাঁর শিক্ষার বিরোধী– এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
মোহাম্মদের (সা) উপর নাজিলকৃত ঐশীবাণী, বহুবিবাহ নিয়ে বিতর্ক, ইহুদীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে অনুসৃত নীতি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে প্রণীত আইনসহ তাঁর জীবনের বহু জটিল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আমি এই সিরিজে তুলে ধরবো। তৎকালীন সময় ও তাঁর জীবনীর উপর আমি একটি নির্মোহ পর্যালোচনা করতে চাই। বর্তমান বিশ্বকে কীভাবে তা প্রভাবিত করছে, সে ব্যাপারটি বুঝতে চাই। তাঁর শিক্ষা আমাদের জন্য ভালো নাকি মন্দ– সেটিও বুঝে নিতে চাই। আমি ইসলামের নবী মোহাম্মদের (সা) সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন।
প্রথম পর্ব: সত্যসন্ধানী
মুসলমানরা অতি সাধারণ দুই টুকরো সাদা কাপড় পরিধান করে মক্কায় হজ ও ওমরা করতে আসে। দৈনন্দিন পরিধেয় কাপড়ের পরিবর্তে পবিত্রতা ও সমতার প্রতীক হিসেবে তারা এই সাধারণ কাপড় তারা পরিধান করে। গত চৌদ্দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, অর্থাৎ মোহাম্মদের (সা) সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ঐতিহ্যটি পালিত হয়ে আসছে।
জন্মের পর পরই আমার কানে প্রথম যে শব্দগুচ্ছ প্রবেশ করে, তাহলো কালেমায়ে শাহাদাত, ঈমানের সাদামাটা ঘোষণা– ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল’। এই ঘোষণা একইসাথে আমাকে মক্কা এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছিলো। অধিকাংশ মুসলমানের মতো আমিও বাবা-মায়ের পরিবর্তে মোহাম্মদের (সা) নামই সর্বপ্রথম শুনেছি।
ত্রিশ বছর আগে যখন আমার বয়স ছিলো পাঁচ, তখন পরিবারের সাথে হজ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিলাম। মক্কার কাবাঘর হলো ইসলামের সর্বাধিক পরিচিত প্রতীক। মুসলমানরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, কাবার দিকে ফিরে প্রতিদিন পাঁচবার তারা নামাজ আদায় করে। আল্লাহর দরবারে নিজেকে সঁপে দিয়ে কাবার চারদিক প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে মুসলমানরা মোহাম্মদের (সা) পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কোন একতার টানে সারা দুনিয়া থেকে লোকজন এখানে আসে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সবাই নবী মোহাম্মদের (সা) জীবনের মতো করে নিজের জীবনকে সাজাতে চায়। খ্রিস্টানদের কাছে যিশু যতটা গুরুত্বপূর্ণ, মুসলমানদের কাছে মোহাম্মদ (সা) ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই মানুষটি তাদের শুদ্ধ পরিচয় নির্ধারণ করেছেন।
তবে তারা যিশুর মতো মোহাম্মদকে (সা) আল্লাহর পুত্র মনে করে না। আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই তাঁর জন্ম হয়েছিলো, যিশুর মতো অলৌকিকভাবে নয়। তিনি সাধারণত কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন না। যিশুর মতো তিনি পুনরুত্থিতও হননি। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন।

মক্কা নগরী
চৌদ্দশ বছর আগে মোহাম্মদ (সা) যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানকার পরিবেশ ছিলো বসবাসের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল। সেই তপ্ত মরুভূমি ও রুক্ষ পার্বত্যঞ্চলটি আকারে ছিলো ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ। এর অবস্থান ছিলো তৎকালীন দুনিয়ার দুই বৃহৎ পরাশক্তির মাঝখানে। উত্তরে ছিলো রোমানদের সর্বশেষ সাম্রাজ্য খ্রিস্টান বাইজেন্টাইন। এর রাজধানী ছিলো কনস্টান্টিনোপল। আর পূর্বে ছিলো আরেক প্রাচীন শক্তি, বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ– সাসানীয় সভ্যতা। এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য আরব উপজাতি ও গোত্র আধিপত্য বিস্তার ও টিকে থাকার লড়াইয়ে সর্বদা লিপ্ত থাকতো। পুরো অঞ্চল জুড়ে শহর ছিলো মাত্র গুটিকয়েক। এরমধ্যে অন্যতম হলো তাঁর জন্মস্থান মক্কা।
মোহাম্মদ (সা) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের আগেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। আর মা আমেনা ছিলেন খুবই দরিদ্র। সবচেয়ে বড় কথা হলো, একজন ‘মেসিয়াহ’র যে আগমন ঘটছে, এর কোনো ইঙ্গিত ছিলো না। তাঁর আগমনে আকাশে বিশেষ কোনো তারকার আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর উপাসনা করতে দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞানী লোকদের আগমনও ঘটেনি। মাত্র গুটিকতেক জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যাপারটি খেয়াল করেছিলেন। বাদবাকিরা ঘটনাটিকে আদৌ তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। মোহাম্মদ (সা) ঠিক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এর কোনো চিহ্ন এখন আর নেই। কোনো স্মৃতিসৌধ নেই, যাদুঘর নেই, এমনকি একটি ফলক পর্যন্তও নেই।
কেন মহানবীর প্রতিকৃতি আঁকা হয় না?
বেশিরভাগ মুসলমানই ব্যক্তি মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর প্রচারিত শিক্ষার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য মেনে চলেন। মোহাম্মদ (সা) নিশ্চয় উচ্চ মর্যাদায় আসীন, কিন্তু তাই বলে তিনি উপাসনাযোগ্য নন। তাঁর ইবাদত করা শিরক হিসেবে বিবেচিত। ইসলামে এটি জঘন্য ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আর তাই মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করে, সে জন্য মোহাম্মদের (সা) স্মৃতি বিজড়িত বহু স্থানের চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। মোহাম্মদের (সা) প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই খ্রিস্টান চার্চগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ যিশু ও কুমারী মাতা মেরির অসংখ্য ছবি দেখা গেলেও মসজিদগুলোতে মোহাম্মদ (সা) কিংবা অন্য কারোরই কোনো ছবি নেই। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কনটেম্পোরারি ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক তারিক রমাদান এ সম্পর্কে বলেন,
ঠিক এ কারণেই মুসলমানদের জন্য ইসলামী একেশ্বরবাদ (যাকে আমরা আরবীতে বলি ‘তাওহীদ’ তথা আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাই আমরা আল্লাহর কোনো প্রতিকৃতি বানাই না। এটি খোদার সাথে আমাদের এই বিশেষ সম্পর্কেরই দাবি। আমরা নবীদেরও কোনো ধরনের প্রতিকৃতি বানাই না। কেবল সর্বশেষ নবী মোহাম্মদই (সা) নন, ইব্রাহীম (আ), মুসা (আ), ঈসা (আ) সহ সকল নবীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি কমিটমেন্টের কারণেই আমরা কখনো মহানবীর (সা) ইবাদত করি না।
অতীতে কিছু উসমানীয় ও ইরানী মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ে মোহাম্মদের (সা) ছবি আঁকা হয়েছিলো। তবে সেগুলোর সবগুলোতেই তাঁর মুখাবয়বকে আড়াল রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ড্রয়িং ও পেইন্টিংয়ে মোহাম্মদের (সা) প্রতিকৃতি আঁকার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।
অতি সম্প্রতি একটি ডেনিশ কার্টুনে পাগড়ির ভেতর বোমা সম্বলিত একজন সন্ত্রাসী হিসেবে মুহাম্মদকে (সা) চিত্রিত করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম বিশ্ব জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই প্রতিবাদের পেছনে নিছক মুখাবয়ব আঁকাই মুখ্য কারণ ছিলো না। এই ধরনের কার্টুন প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে অপমান করাটাই ছিল মূল ইস্যু।
মহানবীর জীবনীর বিশুদ্ধতা কতটুকু?
মোহাম্মদের (সা) ছবি খুব একটা না থাকলেও তাঁর জীবনী সংক্রান্ত অসংখ্য লিখিত বিবরণ রয়েছে। এরমধ্যে প্রথমটি হলো স্বয়ং ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন। এছাড়াও মোহাম্মদের (সা) জীবনের অসংখ্য ঘটনা ও নিজের কথা তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলো হাদীস নামে পরিচিত। মুসলিম পণ্ডিতগণ মোহাম্মদের (সা) অসংখ্য বাণী ও তাঁর সম্পর্কে বলা ঘটনাগুলো নানাভাবে যাচাই করে বিশুদ্ধ রেফারেন্সগুলো আলাদাভাবে সংরক্ষণ করেছেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের সিনিয়র লেকচারার ড. আমিরা বেনিসন এ প্রসঙ্গে বলেন,
মুসলিম পণ্ডিতরা সংগৃহীত হাদীসগুলো যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীসগুলো থেকে ভুয়া ও জাল হাদীসগুলো আলাদা করার চেষ্টা করেছেন। এসব বিষয়ে তারা সর্বোচ্চ পরিমাণ সচেতন থাকতেন।
জেরুসালেমে অবস্থিত হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক রবার্ট হয়ল্যান্ড অবশ্য হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে বলেন,
এ ব্যাপারটি নিয়ে গবেষকরা নানা ধরনের সমস্যায় পড়েন। যেমন একটা সমস্যা হলো, এগুলোর লিখিত ভাষ্য তৈরি হয়েছে অনেক পরে। ৮২০ খ্রিষ্টাব্দের আগে প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো লিখিত বর্ণনা পাই না। অথচ মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। তারমানে একটা লম্বা সময় পরে এসে এসব লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, মাঝখানের এই সময়টাতে প্রত্যেক যুগের লোকেরা নিশ্চয় হাদীসগুলো পরবর্তী যুগের লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু তা ছিল মুখে মুখে। হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার প্রশ্নে এটা একটা সম্ভাব্য দুর্বলতা।
তবে সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদেল হালিম মনে করেন, এই সংশয়ের কোনো ভিত্তি নেই। তাঁর যুক্তি হলো,
ঐতিহাসিকভাবেই আরবরা তাদের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতো। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই তাদের ইতিহাস, বংশলতিকা ইত্যাদি সবকিছু সময়ের পরম্পরায় চলে এসেছে। আর সেখানে মোহাম্মদ (সা) তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর অনুসারী ছিলো হাজার হাজার, বিরোধী লোক ছিলো কম। তাঁর অনুসারীরা সবকিছু বলে গেছেন, সংরক্ষণ করে গেছেন। এখন কিছু লোকের ‘এগুলো তো বানোয়াট কথা মাত্র’ কিংবা ‘এগুলোর লিখিত রূপ তো অনেক পরে এসেছে’ নিছক এ জাতীয় বক্তব্যের কারণেই হাদীসের এই সমস্ত সূত্রগুলোকে উপেক্ষা করা যায় না।
হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক চলমান থাকলেও কিছু অমুসলিম সূত্র থেকেও কিন্তু মোহাম্মদের (সা) ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়। এটি অবাক হওয়ার মতো একটি ব্যাপারই বটে। সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের নিয়ার অ্যান্ড মিডল-ইস্ট হিস্ট্রির ইমেরিটাস অধ্যাপক জেরাল্ড হটিং আমাদের জানাচ্ছেন,
মোহাম্মদকে নিয়ে অমুসলিম সূত্রে বর্ণিত তথ্যপ্রমাণ খুব বেশি নেই। অল্পকিছু ঐতিহাসিক দলীল রয়েছে মাত্র। মোহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে গ্রিক, সিরিয়াক ও আর্মেনীয় ভাষায় তাঁর নামের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। আমি মনে করি, তাঁর মৃত্যুর ৩০ বছরের মধ্যে এমনটি ঘটা একেবারে কম কিছু নয়।
প্রচলিত তথ্য হলো, ঐতিহাসিক সেবেউস মোহাম্মদের (সা) মৃত্যুর মাত্র ২৪ বছর পর আর্মেনীয় ভাষায় তাঁর সম্পর্কে লিখে গেছেন। তবে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক রবার্ট থমসন জানাচ্ছেন,
এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রথমবারের মতো একজন আর্মেনীয় তথা একজন অমুসলিম মোহাম্মদ সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কর্ম সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ দিয়েছেন। সেবেউস নিজে এসব বিষয়ে কথা বলেছেন ৬৩০ সালের দিকে। তারমানে এটি প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদের মৃত্যুর আগের ঘটনা।
অবাক করা বিষয় হলো, মোহাম্মদের (সা) পরিচয় ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে একদম সঠিক তথ্যই সেবেউস তুলে ধরতে পেরেছেন। অধ্যাপক রবার্ট থমসন আর্মেনীয় ভাষায় সেবেউসের লেখা থেকে অনুবাদ করে আমাকে শুনিয়েছেন–
সেই সময় মেহমেত (আর্মেনীয় ভাষায় মোহাম্মদকে মেহমেত উচ্চারণ করা হয়) নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মানুষের কাছে ধর্মপ্রচারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, বর্তমানে তিনি তাদেরকে অনেকগুলো বিধিনিষেধ দিয়েছেন। যেমন– মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করো না, মদপান করো না, মিথ্যা কথা বলো না, ব্যভিচার করো না ইত্যাদি।
মোহাম্মদের (সা) সময়কাল সম্পর্কে মুসলিমদের বর্ণনার সাথে সেবেউস ও অন্যান্য অমুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মোটাদাগে মিলে যায়। কোরআন ও হাদীসের সমন্বয় করলে আমরা মোহাম্মদের (সা) জীবনের বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো খুঁজে পাই।
তৎকালীন আরবের সমাজ কাঠামো
আমরা জানি, তিনি কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই গোত্রটি মক্কা নগরী শাসন করতো। আমরা এটিও জানি, তাঁর পরিবার ছিলো গরিব। জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি মোহাম্মদের (সা) মা আমেনার কাছে খুব সামান্য অর্থই রেখে যেতে পেরেছিলেন। তৎকালীন আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী জন্মের মাত্র কয়েক মাস পরেই তাঁকে শহরের প্রান্তে এক বেদুইন পরিবারের কাছে লালন-পালনের জন্যে দেয়া হয়। তিনি জীবনের প্রথম চার বছর একজন বেদুইন ধাত্রীর কাছে যাযাবর হিসেবে পালিত হন।
বসবাসের জন্য তৎকালীন আরব ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল একটি জায়গা। সেখানে কোনো আইন ছিলো না, কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিলো না। শান্তি ছিল সুদূর পরাহত। গোত্রীয় আনুগত্য এবং সামাজিক রীতিনীতিই ছিল নিরাপত্তার একমাত্র উপায়। ন্যায়বিচার ছিল দুর্লভ ব্যাপার। কদাচিৎ হয়তো এ ধরনের সুবিধা পাওয়া যেতো। অপরাধের শাস্তি ছিল নৃশংস। যেমন, রুটি চুরি করে কেউ ধরা পরলে প্রায় সময় তাকে মেরে ফেলা হতো। বেঁচে থাকার জন্য নিত্যদিনের কঠোর সংগ্রাম মানুষকে কতটা নিষ্ঠুর করে তুললে এমনটি করা সম্ভব! অধিকাংশ মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ বলতে গেলে ছিলোই না। এই সময়ের বাস্তবতাকে বুঝানোর জন্য মুসলমানরা একটা বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে থাকে– ‘জাহেলিয়াত’ তথা অজ্ঞতার যুগ।
সেই সমাজেরও একটি কাঠামো তথা বিশ্বাসব্যবস্থা ছিল। তবে ধর্ম বলতে আমরা এখন যা বুঝি, সে ধরনের সুসংগঠিত কোনো ধর্ম তখন সেখানে ছিলো না। ড. আমিরা বেনিসনের মতে,
আরবের লোকেরা ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী। তারা অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করতো। সাধারণত প্রত্যেক গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব দেবদেবী ছিলো। পুরো আরব জুড়ে ছিলো একই চিত্র।
মোহাম্মদের (সা) জন্মস্থান মক্কা এই বহু-ঈশ্বরবাদী পূজা-অর্চনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিলো। ‘মোহাম্মদ: অ্যা বায়োগ্রাফি অব দ্যা প্রফেট’ বইয়ের লেখিকা ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
বর্তমানে পৌত্তলিকতা বলতে আমরা যেমনটা বুঝি, তৎকালীন আরবের অধিকাংশ শহর ও অঞ্চলে কার্যত তেমন ধরনের পৌত্তলিকতাই দীর্ঘদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। ঘরের মাঝখানে এক ধরনের বর্গাকার বেদি থাকতো। বেদির চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। বিশেষ করে শহর ও কৃষিনির্ভর অঞ্চলগুলোতে এই প্রবণতা কিছুটা বেশি ছিলো। আল্লাহকে তারা সর্বোচ্চ খোদা মনে করতো। বেশিরভাগ আরবই অবশ্য খুব একটা ধার্মিক ছিলো না।
মুসলমানদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, আদমের (আ) সময় স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক কাবাঘর নির্মিত হয়েছিলো। তবে ঘরটির প্রকৃত নির্মাণকাল সম্পর্কে কোনো প্রত্মতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ (সা) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দীর্ঘকাল ধরেই মক্কা ছিলো আরবের লোকদের পৌত্তলিকতা চর্চার কেন্দ্র। তীর্থস্থান বিবেচনা করে লোকেরা সেখানে ভ্রমণ করতো। ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটরের আরব অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক সাজ্জাদ রিজভী বলেন,
মুসলিম বর্ণনা মতে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রধান প্রার্থনাগৃহ কাবার অস্তিত্ব স্মরণাতীত কাল থেকে বিদ্যমান। তাই ধারণা করা হয়, আল্লাহর ঘর কাবার প্রথম নির্মাতা ছিলেন আদম (আ)। সেই থেকে পরবর্তীতে অনেক নবী-রাসূল ঘরটির দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তারপর ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) কাবাঘর পুনর্নিমাণ করেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে কাবা নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি লোকেরা ভুলে যায়।
মক্কার সাথে ইবরাহীমের (আ) সম্পর্ক নিয়ে কোনো অমুসলিম সূত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটুকু জানা যায়, মোহাম্মদের (সা) জন্মের সময় কাবা ঘরে ৩৬০টিরও বেশি দেবদেবীর মূর্তি ছিলো। তবে এগুলোর মর্যাদার তারতম্য ছিলো। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হতো, যাতে বিরোধী গোত্রগুলো নির্ভয়ে মক্কায় এসে কাবা প্রদক্ষিণ করতে পারে এবং নিজ নিজ দেবতাদের উপাসনা করতে পারে। এখানে বার্ষিক তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো। মোহাম্মদ (সা) কোরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাদের হাতে ছিলো কাবার নিয়ন্ত্রণ। ফলে তারা ছিলো ধনী ও ক্ষমতাবান। অবশ্য মোহাম্মদ (সা) স্বয়ং এই সম্পদ ও ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে ছিলেন।
শৈশবে নিঃসঙ্গ মোহাম্মদ
পাঁচ বছর বয়সে মুহাম্মদকে (সা) মক্কায় তাঁর মা আমেনার কাছে ফিরিয়ে আনা হয়। কিছুদিন পর আমেনা মনস্থির করলেন, ইয়াসরিবে নিজের পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবেন। শহরটি মক্কা থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। ফিরতি পথে তিনি ছিলেন বেশ অসুস্থ। তার উপর মরুভূমিতে উটের কাফেলার সাথে চলার কারণে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। এরমধ্যে আবুয়া নামক এক ছোট্ট মরুদ্যানে কাফেলা থামলো। তারা সেখানে মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর মাকে রেখে যায়। তারা ভেবেছিলো, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিলে তিনি হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু আসলে তা হওয়ার ছিলো না। এর কয়েকদিন পরই আমেনা মারা যান। মা-বাবা দুজনকেই হারিয়ে মোহাম্মদ (সা) পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি একজন এতিম বালকে পরিণত হন।
এই হৃদয়বিদারক ঘটনা পরবর্তীতে মোহাম্মদের (সা) দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশাল ভূমিকা রেখেছিলো। ‘দ্যা প্রফেট মোহাম্মদ: এ বায়োগ্রাফি’ বইয়ের লেখক বারনাবি রজারসন বলেছেন,
সেই নির্জন স্থানটিতে মোহাম্মদ কার্যত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের মৃত্যু দেখা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিলো না। একসময় এই পরিচিত যাত্রাপথটিতে আরেকটি কাফেলা আসলেই কেবল তিনি পুনরায় সমাজে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ভয়ংকর, মর্মন্তুদ ও দুঃসহ একটি অভিজ্ঞতা।
শিশু মোহাম্মদের (সা) সামনে আরো স্বজন হারানোর বেদনা অপেক্ষা করছিলো। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর দাদা তাঁকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দুই বছর পর তিনিও মারা যান। তারপর তাঁকে লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালেব। তিনি ছিলেন মক্কার অভিজাতদের মধ্যে অন্যতম ক্ষমতাধর একজন ব্যক্তি। পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কাজে তিনি সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলা পাঠাতেন।
ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে মক্কার গুরুত্ব
ব্যবসায়িক রুট হওয়ার কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আশপাশের জনবহুল অঞ্চল ও সভ্যতাগুলোর সাথে আরব অঞ্চলের যোগাযোগ ছিলো। মক্কা ছিলো এই চেইনের একটি লিংক। বারনাবি রজারসনের মন্তব্য,
আমার ধারণা, ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো ইয়েমেন থেকে মশলা, সিলভার ও চামড়া বোঝাই করে মক্কায় নিয়ে আসতো। মক্কার কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের নিকট থেকে এসব কিনে নিতো। তারপর তারা সিরিয়া, গাজা, মিশর, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এসব নিয়ে বিক্রি করতো। আপনি তখন সেখানে গেলে হয়তো দেখতে পেতেন, পবিত্র ঘরটির পাশেই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের হই-হট্টগোল চলছে, উটগুলো জড়ো করে মালামাল বোঝাই করা হচ্ছে।
মুসলমানরা মক্কাকে তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এবং তাদের নবীর জন্মের জন্য উপযুক্ত একটি স্থান হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তবে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মক্কার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন। এমন একজন হলেন লেখক ও ইতিহাসবিদ টম হল্যান্ড। তিনি বলেন,
মুসলমানরা আমাদের সামনে মক্কাকে একটি বিশাল বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে তুলে ধরে। তাদের মতে, মক্কা ছিলো পৌত্তলিকদের কেন্দ্রভূমি। কিন্তু সমস্যা হলো, এই দাবির পেছনে ওই যুগের দলিলপ্রমাণ ও প্রত্মতাত্তিক সমর্থন নেই। মক্কা তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে থাকলেও (যদি তা আদতেই হয়ে থাকে) সে বিষয়ে ইসলামী যুগের পূর্বেকার কোনো তথ্য আমরা একদমই জানি না।
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদেল হালিম এ জাতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন,
তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়, মক্কা ছিলো মরু-আরবের কেন্দ্র। আমরা জানি, এইসব বিদেশী ঐতিহাসিকদের পক্ষে আরব মরুভূমির মতো প্রতিকূল ভূখণ্ড পেরিয়ে মক্কায় যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তারা শুধু সমুদ্র ও উপকূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তাই মক্কা নিয়ে তাদের ধারণা না থাকার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। যেমন ধরুন, এখানকার লোকজন সাধারণত টিম্বাকটুর কথা বলে না, আঠারো শতক বা তার আগের সময়ের প্রসঙ্গে সাধারণত কিছু বলে না। তারমানে এই নয়, এর আগে এসবের অস্তিত্ব ছিলো না।
কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অভিযোগ, মোহাম্মদের (সা) মৃত্যুর পর মুসলিম ঐতিহাসিকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মক্কার গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছে। তাদের মতে, এর মাধ্যমে মুসলমানরা দেখাতে চায় মুহাম্মদ (স) এমন একটি উন্নত এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে শহরটির নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রভাবমুক্ত ছিলো। এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে ইমেরিটাস অধ্যাপক জেরাল্ড হটিং বলেন,
মক্কা নামে তখন কোনো স্থানই ছিলো না, এমনটি আমি বলবো না। তবে ইসলাম আসার আগে মক্কার অস্তিত্ব খুব ভালোভাবে প্রমাণিত নয়। আমার ধারণা, ইসলামে যে মক্কার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা তা বুঝতে পেরেছিলো। ফলে ধীরে ধীরে এই ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছে। প্রাথমিক যুগ বলতে আমি নবী কিংবা তাঁর তৎকালীন অনুসারীদের কথা বলছি না। ইসলামের উত্থানের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের বিজয়ের হাত ধরে যে সমাজ গড়ে ওঠেছিলো, তার কথা বলছি।
মহানবীর বাণিজ্য সফর
যাই হোক, তরুণ বয়সে বাণিজ্য সফরে অংশগ্রহণ ছিল মোহাম্মদের (সা) জন্য একটা বিশাল অভিজ্ঞতা। এ সফরের মাধ্যমে তিনি শুধু দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভই করেননি, এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে তাঁর যোগাযোগও ঘটেছিলো। বিস্তীর্ণ মরুভূমি, ছোট ছোট মরুদ্যান, আরব শহর এবং প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন নগরীর মধ্য দিয়ে বাণিজ্য কাফেলাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতো। এসব নগরীর মধ্যে আরবের নাবাতীয় সভ্যতার রাজধানী পেত্রার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভয়াবহ ভূমিকম্পে শহরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এই সফর থেকে মোহাম্মদ (সা) হয়তো অন্যান্য জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জেনে থাকবেন। বারনাবি রজারসন এ ব্যাপারে বলেন,
অতি ধার্মিক মুসলমানদের সাথে কথা বলে দেখেছি, তারা এ ধরনের কোনো প্রভাব থাকার কথা একদমই মানতে চায় না। তারা মনে করে, মহানবী হলেন এমন এক সাদা কাগজ, যেখানে প্রতিটি শব্দ স্বয়ং আল্লাহ লিখে দিয়েছেন। কেউ চাইলে এ রকম ভাবতেই পারে। তবে আমি মনে করি, বাণিজ্য কাফেলার সাথে তাঁর সফরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে জানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা লাভ, বিশ্বের কাছে মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও বিশ্বের নানা ধরনের জটিলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পেত্রাসহ বড় বড় আরব সভ্যতাগুলোর ধ্বংসাবশেষ ও দামেস্কের ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করাসহ দুনিয়ার বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে তিনি আরব বিশ্বের তৎকালীন বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।
মোহাম্মদের (সা) দৈহিক বর্ণনা
মুসলিম সূত্র মতে, তরুণ বয়সেই মোহাম্মদ (সা) তাঁর চারিত্রিক সরলতা ও শুদ্ধতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আল-আমীন (সত্যবাদী) ও আস-সাদীক (সত্যনিষ্ঠ) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগতে পারে, যে ব্যক্তিটি এমন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পেরেছিলেন, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন? তাঁর ছবি বা প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ হলেও প্রচলিত মুসলিম বিবরণ থেকে তাঁর দৈহিক বর্ণনার বিস্তারিত লিখিত রূপ আমরা পাই। তাঁকে নিয়ে লেখা সর্বপ্রথম জীবনীগ্রন্থ অনুযায়ী, তাঁর উচ্চতা ছিলো গড়পড়তার চেয়ে একটু বেশি। তিনি দীর্ঘ পেশীবহুল সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। আঙ্গুলগুলো ছিলো সরু ও লম্বা। দীর্ঘ ও ঘন চুলগুলো ছিলো হালকা কোঁকড়ানো। চোখ দুটি ছিলো বেশ বড় ও কালো, তবে হালকা বাদামী। দাড়ি ছিলো ঘন। গায়ের রঙ ফর্সা। এক কথায়, বিয়ে করার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন।
খাদীজার সাথে বিয়ে
মোহাম্মদের (সা) বিয়ে করার প্রথম প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়েছিলো। কিছুটা অবমাননাকরও ছিলো বটে। তিনি তাঁর চাচাতো বোনকে বিয়ে করার জন্য চাচার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু একজন এতিম যুবকের তুলনামূলক নিচু সামাজিক অবস্থানের কারণে তাঁর চাচা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তবে কিছুদিন পরই তাঁর ভাগ্যের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। একজন বয়স্ক ধনী নারী খাদীজা নিজের ব্যবসায়িক কাজে তাঁকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। মোহাম্মদ (সা) তার ব্যবসায়িক টার্গেট পূরণ করতে পেরেছিলেন। সিরিয়া থেকে খাদীজা প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। খাদীজা মোহাম্মদকে (সা) বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। জর্দান রাজপরিবারের প্রিন্সেস বাদিয়া বিনতে আল হাসান এই ঘটনা ব্যাখ্যা করে বলেন,
সায়্যেদিনা খাদীজার (রা) সাথে তাঁর বিয়ে ছিলো খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা। খাদীজা (রা) ছিলেন বয়সে কিছুটা বড়। এছাড়া তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্তমান যুগেও এ ধরনের ঘটনা কিছুটা ব্যতিক্রম। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এই যুগেও পাশ্চাত্যেরই অনেক পুরুষ একজন সফল নারীকে বিয়ে করতে ভয় পায়। তাই আমি মনে করি, এই বিয়েতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে মহানবীর (সা) অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং নারীদের প্রতি তাঁর সম্মান প্রকাশ পেয়েছে। এখনো যদি কেউ এ ধরনের বিয়ে করতে চায়, তাহলে তার মধ্যেও এইসব গুণ থাকতে হবে।
বর্তমান যুগেও মুসলিম বিশ্বে একজন বয়স্ক নারীর পক্ষে কমবয়সী কোনো যুবককে বিয়ে করতে পারা একটি বিরল ব্যাপার। আর তখন তো এমনটি কেউ ভাবতেও পারতো না। ক্যারেন আর্মস্ট্রং ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে বলেন,
ইসলাম আসার আগে আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে নারীদের সাথে প্রায় পশুর মতো আচরণ করা হতো। নারীদের মানবাধিকার বলতে কিছুই ছিলো না। তবে শহুরে কিংবা ব্যবসায়ী নারীরা কিছুটা সুবিধা পেতো। কুটির শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীরা ভূমিকার রাখার মোটামুটি সুযোগ পেতো। খাদীজা ছিলেন এমনই একজন নারী। তিনি বিধবা ছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁর স্বামীর ভালো ব্যবসা ছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এই ব্যবসার মালিকানা লাভ করেন এবং তা চালিয়ে নিতে সক্ষম হন।
খাদীজার (রা) সাথে মোহাম্মদের (সা) ২৪ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিলো। তখন বহুবিবাহ ছিলো অতি সাধারণ সামাজিক প্রথা। তা সত্ত্বেও খাদীজা (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেননি। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল দলীল থেকে প্রমাণিত, খাদীজার (রা) ব্যবসা পরিচালনায় তিনি কখনোই কোনো বাধা দেননি। অথচ বর্তমান যুগেও বেশিরভাগ মুসলিম সমাজে নারীদেরকে স্বাধীন মর্যাদা লাভের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। লন্ডনস্থ মুসলিম ইনস্টিটিউটের পরিচালক ম্যারল ওয়েন ডেভিস এ প্রসঙ্গে বলেন,
কমবয়সী কোনো যুবককে বিয়ে করা এখনো একজন বয়স্ক নারীর জন্য কলঙ্কের ব্যাপার। মুসলিম সমাজে ব্যবসা ও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ করা এখন পর্যন্ত বেশ কঠিন। মুসলিম সমাজ গঠনে নারীরাও যে পুরুষদের সমান অংশীদার, খাদীজা (রা) তা দেখিয়ে গেছেন।
বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার উপর মহানবীর অসন্তোষ
খাদীজাকে (রা) বিয়ে করে মোহাম্মদ (সা) সুখী থাকলেও এই নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনে তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না। তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। বারনাবি রজারসন ব্যাপারটি বর্ণনা করেছেন এভাবে,
জীবনের ২৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সময়কালটি হওয়ার কথা ছিলো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। কারণ, এ সময় তিনি খাদিজার মতো সম্পদশালী, সুন্দরী ও বিশ্বস্ত নারীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। চার চারটি ফুটফুটে কন্যার বাবা ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলে সন্তান জন্মলাভ করেছিলো। যদিও তারা শিশুকালেই মারা যায়। তিনি ছিলেন একটি সম্মানিত গোত্রের সদস্য। সাপোর্ট দেয়ার মতো তাঁর একটি পরিবারও ছিলো। এতো কিছু থাকার পরেও, এমনকি সমাজের শীর্ষস্থানে থেকেও আশপাশের সবকিছু নিয়ে তাঁর মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তিবোধ কাজ করতো। তিনি গোত্রতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সহিংস রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছেন, এখানে অর্থকড়ি দিয়ে যে কাউকে কিনে ফেলা যায়।
এসব কারণে সামগ্রিকভাবে মোহাম্মদ (সা) মোটেও সুখী ছিলেন না। আরবের গোত্রতান্ত্রিক সমাজের কদর্য রূপ তিনি দেখেছিলেন। গোত্রীয় জীবনধারার বৈষম্যগুলো তাঁকে বিষিয়ে তুলেছিলো। এসব নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত থাকতেন। প্রাপ্ত সকল বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি এ সময়ে এক ধরনের মানসিক সংকটে ভুগছিলেন। লন্ডনভিত্তিক ইসলামিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমির চেয়ারম্যান আব্দুর রহীম গ্রীন এ ব্যাপারে বলেন,
সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের দুরাবস্থা দেখে তিনি সত্যিই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এসব দেখে নিশ্চিতভাবেই সেই গোড়ার প্রশ্নটি তাঁকে ভাবিয়ে তোলে– আমরা কেন পৃথিবীতে এসেছি, জীবনের উদ্দেশ্য কী, আমাদের চারপাশের জগতকে আমরা কীভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি, ইত্যাদি।
লন্ডনের স্থানীয় একজন ইমাম আজমল মাসরুর বলেন,
তরুণ বয়সে ইবরাহীম (আ) যেমন পথের দিশা খুঁজে বেড়াতেন, মুসা (আ) যেমন উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতেন, ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত অন্যান্য সকল নবী-রাসূল যেমন সঠিক পথের অনুসন্ধান করতেন, ঠিক তেমনি তিনিও এমন একটা পথের অনুসন্ধান করতে বলে আমার মনে হয়।
জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক জন এসপোজিটো বলেন,
সমাজ, নৈতিকতা, স্রষ্টার প্রকৃতিবিরোধী ধর্মীয় রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাই কারো জন্য খুব সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

হেরা গুহায় আধ্যাত্মিকতা চর্চা
এই পর্যায়ে মোহাম্মদ (সা) নির্জনে নিয়মিত আধ্যাত্মিকতা চর্চা করতেন। শান্তি ও নির্জনতার খোঁজে ও প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় সারা বছরই মক্কার পাহাড়-পর্বতে কাটাতেন। তিনি আসলে কীসের অন্বেষণ করতেন? সেখানে গিয়ে কী করতেন? তিনি যে সমাজের দুরাবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, তা নিশ্চিত। ফলে তিনি আসলে এক ধরনের ঐশী সত্য খুঁজে ফিরছিলেন।
মোহাম্মদ (সা) ক্রমান্বয়ে নিয়মিতভাবে ও গভীর মনোযোগের সাথে নির্জনে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করতে থাকেন। এতে তাঁর অভিব্যক্তি ও চিন্তা আরো শাণিত হতে থাকে। এই কাজের জন্য তিনি শহরের অদূরে ‘জাবালে নূরকে’ বেছে নেন। পাদদেশ থেকে পাহাড়টির চূড়ায় আরোহণ করা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি একদম চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহায় (যেটি এখন গারে হেরা নামে পরিচিত) অবস্থান করতেন। আরো গভীর ও ঐকান্তিকভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়ার লক্ষ্যে তিনি সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন।
হঠাৎ একদিন এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেলো, যা শুধু তাঁর জীবনকেই বদলে দেয়নি, বরং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসই পাল্টে দিয়েছে। এটি ছিলো ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।
ওহীর সূচনা
মোহাম্মদ (সা) তখন অন্যদিনের মতোই ধ্যানমগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তাঁর শরীর প্রচণ্ডভাবে কাঁপছিলো। পরবর্তীতে তিনি এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন– একজন ফেরেশতা এসে তাঁকে এমন শক্তভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন, যাতে শ্বাসরোধ হয়ে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। একদম বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি সেখানে শুয়েছিলেন। এই পর্যায়ে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান– “ইকরা!” – “পড়ো!” তিনি জবাব দিলেন, “আমি পারছি না। আমি পাঠক নই।” কণ্ঠস্বরটি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো, “পড়ো!” তিনি জবাব দিলেন, “আমি পাঠক নই।” তৃতীয়বারের মতো তাঁকে বলা হলো, “পড়ো!” এবার তিনি জবাব দিলেন, “আমি কী পড়বো?” তখনই এই কথাগুলো ভেসে এলো–
ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ- خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ- ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ- ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ- عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
অর্থ: ১. (হে মোহাম্মদ) তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, ২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে, ৩. তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার রব বড় মেহেরবান, ৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান) শিখিয়েছেন, ৫. তিনি মানুষকে (এমন কিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতো না। (সূরা আলাক: ১-৫)
নবীদের ওহী লাভের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
তিনি ঐশীবাণী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওহী নাজিলের সময় যে প্রচণ্ড কষ্ট হয়, বনী ইসরাইলের কয়েকজন নবীর অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা তা জানি। এটি কোনো শান্ত-স্নিগ্ধ বা কোমল অভিজ্ঞতা নয়। ওহী নাজিলের সময় শরীরের প্রতিটি তন্ত্রীতে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে। নবী জেরেমায়াহ তো চিৎকার করে ওঠেছিলেন, “আহ! ও খোদা! আমি তো কথা বলতে পারছি না! আমি তো শিশুর মতো হয়ে গেছি! তোমার ওহী আমার প্রতিটি কোষে আঘাত করছে।” নবী ঈসা গির্জায় ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে বলে ওঠেছিলেন, “আমি একদম শেষ, আমি সর্বশক্তিমান প্রভুকে দেখেছি!” ঐশীবাণী লাভের ঘটনা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার। এর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এটি আপনার পরিচিত দুনিয়াকে আমূল পাল্টে দেয়।
এ ব্যাপারে বারনাবি রজারসন বলেন,
নবীগণ ঐশ্বরিক ক্ষমতার যে স্পিরিট লাভ করে থাকেন, তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষা ও উপমার মাধ্যমে তাদের কাছে তুলে ধরা হলো নবীদের কাজ। আমার মতে, প্রচণ্ড কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মহানবী ওহী লাভ করেছিলেন। তাঁর গোটা সত্ত্বা জুড়ে প্রবাহিত এই বিশেষ অভিজ্ঞতাকে তিনি ভাষায় প্রকাশ করেছেন।
এটি ছিলো মোহাম্মদের (সা) জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে ১৫০ কোটিরও বেশি মানুষ তাঁর অনুসারী। তাঁর আনীত ঐশীবাণীর উপর তারা পুরোপুরি বিশ্বাস রাখে। এ কারণেই তাদেরকে মুসলমান বলা হয়।
অবশ্য হেরা গুহায় যখন সর্বপ্রথম ঐশীবাণী নাজিল হয়েছিলো, তখন মোহাম্মদের (সা) প্রতিক্রিয়া ছিলো একেবারেই ভিন্ন। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে ডাকছিলেন, “খাদীজা! খাদীজা! আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। আমার সাথে একি ঘটনা ঘটে গেলো? আমি তো এখন জীবন নাশের আশঙ্কা করছি।” খাদীজা (রা) নিজের চাদর দিয়ে তাঁর প্রায় অবশ শরীরটাকে ঢেকে দিলেন। তারপর মোহাম্মদের (সা) সকল সংশয় সত্ত্বেও খাদীজাই (রা) তাঁর ওহী লাভের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। খাদীজার (রা) কথাগুলো তাঁর জন্য নিছক সান্তনাবাণী মাত্র ছিলো না। তার কথা শুনেই সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাটির ব্যাপারে তিনি স্থিরচিত্ত হতে পেরেছিলেন। এভাবে সত্যসন্ধানী ব্যক্তিটি অবশেষে সেই আলোর সন্ধান পেয়ে গেলেন, যা তিনি খুঁজে ফিরছিলেন।
ওহী নাজিলে বিরতি
কিন্তু তারপর দীর্ঘদিন আর কিছুই ঘটলো না। ফলে তিনি মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়লেন। তাহলে কি এসব কিছু নিছকই বিভ্রান্তি ছিলো? ওহীর ব্যাপারটি কি নিছক আবেগের চরম বহিঃপ্রকাশ ছিলো? নাকি সত্যসন্ধানী মোহাম্মদকে (সা) আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন? মহানবীর (সা) তখনকার এ ধরনের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
তিনি চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। একটি বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এতো বেশি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিলেন।
এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসও পেরিয়ে গেলো। মোহাম্মদের (সা) জীবন টালমাটাল হয়ে ওঠলো। ওহী লাভের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর মাঝে সন্দেহ ঘনিভূত হতে লাগলো। এমনকি নিজের ব্যাপারেও তিনি সন্দিহান হয়ে পড়লেন। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেলো। তারপর হঠাৎ একদিন সকাল বেলা সকল নীরবতার অবসান ঘটিয়ে পুনরায় ওহী নাজিল হতে থাকলো–
وَٱلضُّحَىٰ- وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ- وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌۭ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ- وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ- أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ- وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ- وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ- فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ- وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
অর্থ: (১) শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের, (২) শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে) ছেয়ে যায়, (৩) তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি (তোমার ওপর) অসন্তুষ্টও হননি; (৪) অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম; (৫) অল্পদিনের মধ্যেই তোমার রব তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (এতে) খুশি হয়ে যাবে; (৬) তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি– অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, (৭) তিনি কি তোমাকে (সঠিক পথের সন্ধানে) বিব্রত অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, (৮) তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি, অতঃপর তিনি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন; (৯) অতএব তুমি কখনো এতিমের ওপর জুলুম করো না; (১০) কোনো প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না; (১১) তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও। (সূরা দোহা: ১-১১)
মোহাম্মদ (সা) এবার বুঝতে পারলেন, তাঁর উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাঁকে ঐশীবাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁর আগের অন্যান্য নবীদের মতো তিনিও বিশ্বাস করলেন, আল্লাহ তাঁকে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। এখন তাঁর দায়িত্ব হলো অন্যদের মাঝে এই বাণীর প্রচার করা; যেন তারা নিজেদের জীবনকে আরো উন্নত করতে পারে।
কোরআনের গুরুত্ব
মোহাম্মদের (সা) উপর নাজিলকৃত ওহীর সমষ্টিই পরবর্তীতে ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়। এটি এখন আমাদের নিকট কোরআন হিসেবে পরিচিত। এর শাব্দিক অর্থ হলো পঠিত। প্রচলিত মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী, স্বয়ং আল্লাহই কোরআনের লেখক, মোহাম্মদ (সা) মানুষের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন মাত্র।
বেশিরভাগ মুসলমান মনে করেন, কোরআন হলো আল্লাহর মোজেজা। মোহাম্মদ (সা) সবসময়ই জোর দিয়ে বলে গেছেন, তাঁর কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কোরআনের আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বা নিদর্শনের সাথে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। তবে এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র। আল্লাহর বাণী তথা কোরআনই কেবল মোজেজা হিসেবে বিবেচিত। কোরআনের আয়াতের মাঝেই নিহিত রয়েছে এর আধ্যাত্মিক শক্তি –
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
অর্থ: আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও, তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছো; তাদের (পথ) নয় যারা (তোমার) ক্রোধের পাত্র; তাদের (পথ) নয় যারা বিপথগামী। (সূরা ফাতেহা: ৬-৭)
‘উম্মী’ ধারণাটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, মোহাম্মদ (সা) লেখতে-পড়তে জানতেন না। তাঁর নিরক্ষরতার ব্যাপারটি মুসলমানদের ঈমানের অপরিহার্য বিষয়। একটি কারণে ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো, ইসলামের কোনো কোনো সমালোচক বলে থাকেন, বাণিজ্য সফরের সময় মোহাম্মদ নিশ্চয় ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছিলেন এবং সেই ধর্মীয় কনসেপ্টগুলোই নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে তিনি নিজস্ব ধর্মীয় বাণী হিসেবে প্রচার করেছেন। তাই মুসলমানদের যুক্তি হলো, তিনি যেহেতু লেখাপড়াই জানতেন না, তাই এ ধরনের যে কোনো প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। এবং নতুন ধর্ম ইসলামের ভিত্তি তথা ওহী সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের সমালোচক টম হল্যান্ডের বক্তব্য হলো,
কোরআনের কোনো কথা যে ইহুদী, খ্রিস্টান কিংবা সামারীয়দের থেকে মোহাম্মদ গ্রহণ করেননি, এটি যে সরাসরি আল্লাহরই কথা–তা বিশ্বাস করা মুসলমানদের জন্য জরুরি। ঠিক এ কারণেই মুসলিম বিশ্বাস মতে তিনি ছিলেন নিরক্ষর। অথচ কোরআনে প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতটাই বলা হয়েছে। তাদের এই বিশ্বাসের আরেকটা কারণ হলো, তিনি জন্মেছিলেন মরুভূমির মধ্যখানে। ফলে নিকটপ্রাচ্যের শক্তিশালী এই ধর্মগুলোর সংস্পর্শ থেকে তিনি শত শত মাইল দূরে ছিলেন বলে মনে করা হয়।
এ ব্যাপারে লেখক ও টিভি উপস্থাপক জিয়াউদ্দীন সরদার বলেন,
কোরআন ইহুদি-খ্রিস্ট ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত– এই বিতর্কটাই তো অযৌক্তিক। ইসলাম নিজেই তো নিজেকে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর ধারাবাহিকতা বলে দাবি করে। আমরা ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের ধারাবাহিকতা মাত্র। সেই অর্থে আমরা নিশ্চয় এই ধর্মগুলো দ্বারা প্রভাবিত।
আব্দুর রহীম গ্রীন এ ব্যাপারে বলেন,
কোরআন স্পষ্ট করেই বলেছে, মোহাম্মদ (সা) লেখতে পারতেন না। আর ‘উম্মী’ শব্দটির অর্থ মূর্খ বা অজ্ঞ নয়। এর অর্থ হলো যে লেখতে-পড়তে জানে না, যে ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থ পড়া শেখেনি বা অধ্যয়ন করেনি। অবশ্য অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তিকেও উম্মী বলার প্রচলন রয়েছে। তবে মূল কথা হলো, জিবরাইল (আ) হেরা গুহায় এসে যখন মহানবীকে (সা) বলেছিলেন, ‘পড়ো’, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ‘আমি পড়তে পারি না’।
খ্রিস্টানদের কাছে ব্যক্তি যিশু যেমন সবকিছুর ঊর্ধ্বে, মুসলমানদের কাছে কোরআনও তেমন ব্যাপার। খ্রিস্টানদের কাছে যিশু হলেন ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ ও প্রতীক। তাঁর জন্মগ্রহণের বিষয়টি মানুষের অহেতুক সন্দেহের ঊর্ধ্বে পবিত্র ও বিশুদ্ধ একটি ব্যাপার। মুসলমানদের ক্ষেত্রে কোরআনও তেমনি। এটি হলো আল্লাহর কথা। তাই এটি যে কোনো প্রকার অযাচিত মানবীয় হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্র। এ কারণেই কোরআনের অমর্যাদা হলে মুসলমানরা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পায়। তাদের দৃষ্টিতে, এতে শুধু মোহাম্মদই (সা) নন, স্বয়ং আল্লাহকেও অপমান করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোরআন পোড়ানো বা কোরআনের অমর্যাদা সংক্রান্ত বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে। কখনো গুয়ান্তানামো বে’র মুসলিম বন্দীদেরকে অপমান করার উদ্দেশ্যে, কখনো বা কোনো সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় এসব ঘটেছে।
দাওয়াতী কাজের সূচনা
শুরুতে মোহাম্মদ (সা) ঘনিষ্ঠজনদের মাঝে তাঁর এই বাণী গ্রহণের দাওয়াত দেন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা)। তারপর তাঁর কিশোর চাচাতো ভাই আলী (রা), পরবর্তীতে যিনি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু বকর (রা) এই বাণী গ্রহণ করেন। তিনি মোহাম্মদের (সা) ওফাতের পর ইসলামের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে অধ্যাপক সাজ্জাদ রিজভী বলেন,
সাধারণত বলা হয়ে থাকে, প্রথমদিকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর তরুণরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। অভিজাত পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের একদম প্রান্তিক লোকেরাও ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলো। এদিক থেকে দেখলে বুঝা যায়, ইসলাম ছিলো তখন একটি বিপ্লবী বার্তা। বিপ্লবী এই অর্থে যে, তৎকালীন সমাজের অচলায়তনকে ইসলাম ওলট-পালট করে দিতে চেয়েছিলো।
এখনকার মতো তখনো ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সহজ ও সোজাসাপ্টা ছিলো। দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে ঈমান গ্রহণের সাদামাটা ঘোষণা দেয়াই ছিলো যথেষ্ট।[1] ইসলাম গ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো, এটি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ও স্বাধীন ইচ্ছা থেকে হতে হবে। এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মোহাম্মদের (সা) চাচা আবু তালিবের ঘটনা থেকে। তিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুভাকাঙ্খী, আবার অন্যদিকে ছিলেন গোত্র সর্দার। মক্কায় যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে তিনি এ যাবৎ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আবু তালিবও এই বাণী গ্রহণ করেননি। মোহাম্মদ (সা) তাঁকে বুঝাতে বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কখনোই জোরাজোরি করেননি। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে ম্যারল ওয়েন ডেভিস বলেন,
কোরআনের সবচেয়ে স্পষ্ট, দ্ব্যার্থকতামুক্ত আয়াত হলো– ‘ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই’। এক্ষেত্রে কোনো যদি-কিন্তু-তবে নেই। এটিই হলো আসল কথা। কেউ যদি স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তার কাজকর্মের জন্য পরকালে সে কোনোভাবেই দায়ী হবে না। এটিই হচ্ছে ইসলামের মূলকথা।
‘ইসলাম: অ্যা ক্রিশ্চিয়ান পারস্পেকটিভ’ গ্রন্থের লেখক বিশপ মাইকেল নাজির আলী এ প্রসঙ্গে বলেন,
কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যাপারে একদম সুস্পষ্ট। কোরআনের একটি বহুল পরিচিত আয়াত হলো– ‘ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই’। মহানবী নিজেও পৌত্তলিক আরবদের উদ্দেশ্যে একই ধরনের কথা বলেছেন– ‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমার জন্য আমার দ্বীন’। পারস্পরিক সহিষ্ণুতার জন্য এটি খুব ভালো একটি উপায়। কিন্তু ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখে এসেছি, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করা হয়নি।
মোহাম্মদ (সা) যে ঐশীবাণী প্রচার করেছিলেন, পরবর্তীতে তা ইসলাম নামে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো ‘আত্মসমর্পণ’। এই অর্থে একজন বিশ্বাসী তথা মুসলমান হলেন তিনি, যিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন। ইসলাম শব্দটি এসেছে ‘সালাম’ শব্দ থেকে, যার অর্থ শান্তি।[2]
এক আল্লাহর ধারণা সংক্রান্ত যে বাণী ইবরাহীম (আ) প্রচার করতেন, পরবর্তীতে ইহুদী-খ্রিস্টানদের নবীগণও যা প্রচার করেছিলেন, মক্কায় দাওয়াতী মিশনের শুরুতে মোহাম্মদ (সা) মানুষের নিকট সেই বাণীই প্রচার করতেন। এর পাশাপাশি সমাজে বিদ্যমান অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিনিয়ত লোকদের সাবধান করতেন। অধ্যাপক জন এসপোজিটো বলেন,
একজন নবীর যত ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকার কথা, এর সবগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি মহানবী হয়ে ওঠেছিলেন। হ্যাঁ, নবীদের মূল কাজ হলো মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী তুলে ধরা। কিন্তু সত্যিকারের নবীগণ একইসাথে একজন সতর্ককারীও বটে। আর মহানবী তো ছিলেন একজন সংস্কারক। তাই তিনি সমাজকে সতর্ক করতেন। সমাজ যে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, তা নির্দ্বিধায় বলতেন।
কোরাইশদের নির্যাতন
তবে মোহাম্মদের (সা) এসব তৎপরতাকে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভালো চোখে দেখা হতো না। তিনি সার্বজনীন সমতার কথা বলতেন, মক্কার শাসক কোরাইশ নেতারা যা পছন্দ করতো না। তাঁরা ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মহানবীকে (সা) থামানোর জন্য তারা টাকা-পয়সা ও ক্ষমতার প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলো। এমনকি তিনি যা চাইবেন তাই দেয়া হবে, এমন প্রলোভনও দেখানো হয়েছিলো। তাদের এই সকল প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি একটাই জবাব দিয়েছিলেন–
সম্পদের লোভ কিংবা তোমাদের নেতা বা রাজা হওয়ার আকাঙ্খায় আমি আসিনি। আল্লাহর রাসূল হিসেবে তাঁর বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই কেবল আমি এসেছি। তোমরা যদি তা গ্রহণ করো, তাহলে উপকৃত হবে। আর যদি গ্রহণ না করো, তাহলে আমি ধৈর্য ধরবো এবং আল্লাহর চূড়ান্ত বিচারের অপেক্ষায় থাকবো।
ফলে মক্কার নেতারা বুঝতে পারলো, সোজা কথায় কাজ হবে না। তাই এবার তারা ভিন্ন পথ বেছে নিলো। তাঁর উপর নানাভাবে চড়াও হতে শুরু করলো।
মৃদু চাপপ্রয়োগ এ পর্যায়ে সহিংস নির্যাতনে রূপ নিলো। মোহাম্মদের (সা) সাহাবীরা, বিশেষ করে যাদের কোনো গোত্র পরিচয় কিংবা গোত্রীয় নিরাপত্তা ছিলো না (যেমন– দাস-দাসী), বর্বর নির্যাতনের সহজ শিকারে পরিণত হলো। তাদের কাউকে ছুড়ে ফেলা হতো জ্বলন্ত কয়লায়, কাউকে নির্দয়ভাবে পেটানো হতো, অসহায় নারীদের কাউকে কাউকে ছুরিকাঘাতে মেরে ফেলা হতো। এই নির্যাতনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
কোরাইশদের বিশ্বাসব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে মোহাম্মদ মূলত তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অনিশ্চিত করে তুলেছিলেন। কারণ, মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে তাদের এতদিনের ধর্মীয় রীতিনীতির গভীর সম্পর্ক ছিলো। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা যখন উপাসনার জন্য কাবায় আসবে, তখন মুসলমানদের দাওয়াতী তৎপরতা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সত্যিই খারাপ পরিণতি বয়ে আনবে– এমন আশংকা তারা করতো। তারা বুঝতে পেরেছিলো, এটি একটা বিশাল হুমকি। ফলে তারা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।
এমতাবস্থায় মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের ক্ষুদ্র দলটি চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁরা প্রকাশ্যে অকথ্য গালাগাল ও শারিরীক নির্যাতনের শিকার হতে থাকলেন। এমনকি গোপনেও তাঁরা একত্রিত হতে পারতেন না। নামাজ আদায় করতে পারতেন না। বর্তমানে মুসলমানরা ইবাদত পালনের যে স্বাধীনতা ভোগ করছে, তখন তা ছিলো সুদূর পরাহত।
ইসলামিক সেন্টারের অধীনে লন্ডনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হ্যারো উপশহরে বর্তমানে একটি পাঁচতলা মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের সর্বত্রই মুসলমানরা এখন মসজিদ নির্মাণের সুবিধা পাচ্ছে। অথচ মোহাম্মদ (সা) নিজ শহরে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে যখন একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁদেরকে হতে হয়েছিলো। হ্যারো মসজিদ কমিটির একজন দায়িত্বশীল আজমত আলীর সাথে মসজিদের নির্মাণাধীন ফ্লোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম–
– আমরা কত ভাগ্যবান! এই যে আমি আপনার সাথে কমিউনিটির একটি বিল্ডিংয়ের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছি, মহানবীর (সা) অভিজ্ঞতা তো এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলো। তিনি যখন তাঁর মতো করে একটি কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন, তখন এ জাতীয় কোনো সুযোগ বা স্বাধীনতা মোটেও পাননি।
– আপনি ঠিকই বলেছেন। তখন সময়টা আসলেই খুব প্রতিকূল ছিলো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাঁরা প্রচণ্ড কষ্ট করেছেন। তাঁদের সবকিছুতেই বাধা দেয়া হতো। নামাজ পড়তে গেলেও তাঁদেরকে নানান রকম লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতা সহ্য করতে হতো। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, মাশাআল্লাহ।
আবিসিনিয়ায় হিজরত
কোরাইশদের অত্যাচারের মোকাবেলায় শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে মোহাম্মদ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিরাপত্তার জন্য বিকল্প একটি উপায় খুঁজে বের করলেন। নানান দিক থেকেই এটি ছিলো একটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত। তিনি সাহাবীদেরকে বাড়িঘর ছেড়ে লোহিত সাগরের অপর পাড়ে অবস্থিত খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশী শাসিত আফ্রিকান রাজ্য আবিসিনিয়ায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেন।
৬১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একদল মুসলমান সপরিবারে গোপনে মক্কা ত্যাগ করেন। বর্তমানে ইথিওপিয়া হিসেবে যে দেশটি পরিচিত, সেখানে তাঁরা একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। মুসলমানদের চলে যাওয়ার খবরে কোরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নির্বাসিতদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্য আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীকে রাজি করাতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। ফলে প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য নাজ্জাশী মুসলমানদের নেতাকে ডেকে পাঠালেন। রাজদরবারে তিনি বললেন, মোহাম্মদ (সা) হলেন একমাত্র সত্য খোদার প্রেরিত নবী। তারপর তিনি কোরআন থেকে সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করতে থাকেন। তিনি যে আয়াত পড়ছিলেন, সেখানে কুমারী মরিয়মের (আ) গর্ভে ঈসার (আ) জন্মের বর্ণনা রয়েছে। আয়াতটিতে যিশুখ্রিষ্টকে আল্লাহর একজন নবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি শুনে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। নাজ্জাশীর চোখ দিয়ে তখন অশ্রু গড়াচ্ছিলো। যার ফলে তিনি মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় বসবাসের অনুমতি দেন।
শয়তানের আয়াত
ব্যর্থ মনোরথে মক্কায় ফিরে কোরাইশরা মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের উপর চড়াও হলো। তারা শহর জুড়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো, মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর পুরো গোত্রের সাথে কেউ কোনো কিছু করতে পারবে না। বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজারে ক্রয়বিক্রয় থেকে শুরু করে কোনো কিছুই তাদেরকে করতে দেয়া হতো না। মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীরা মক্কায় গণশত্রুতে পরিণত হলেন। এভাবে তারা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত প্রচারে আপস করা এবং কোরাইশদের দেবতাদেরকে মেনে নেয়ার জন্য মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখলো।
এখন পর্যন্ত বাদবাকি বিশ্বের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নির্ধারণে যে মৌলিক বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, সেই পরিস্থিতিতে হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যার ফলে সেটি হুমকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো। অবশ্য অধিকাংশ মুসলমান পুরো বিষয়টিকেই বানোয়াট মনে করে। সে যাই হোক, মোহাম্মদ (সা) এবং কোরআনকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ইসলামের বিরোধীরা এই ঘটনাটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। ঘটনাটির নানা ধরনের বর্ণনা আছে, তবে মূল ভাষ্যটি মোটামুটি এ রকম:
একদিন মহানবী (সা) কাবাঘরে বসে থাকা অবস্থায় একটি নতুন ওহী নাজিল হলো। যাতে বলা হলো– তিনি চাইলে কোরাইশদের সাথে সমঝোতায় আসতে পারেন যে, কোরাইশদের দেবদেবীদের উপাসনা করায় তাঁর আপত্তি নেই। কোরাইশরা এই ‘ওহী’ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো। তারা মনে করলো– যাক, মোহাম্মদ অবশেষে তাদের চিন্তাধারায় ফিরে আসছে। কিন্তু তারপরই ঘটলো আসল ঘটনা। তাৎক্ষণিকভাবে মোহাম্মদের (সা) কাছে আরেকটি ওহী নাজিল হলো। এতে বলা হয়, দেবদেবীদেরকে বাহ্যত মেনে নেয়া সংক্রান্ত যে ‘ওহী’টি নাজিল হয়েছিলো, তা ছিলো আসলে শয়তানের প্ররোচনা। এই কারণে এই আয়াতকে পরবর্তীতে ‘শয়তানের আয়াত’ বলে অভিহিত করা হয়। ঘটনাটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মোহাম্মদ (সা) নিজের ইচ্ছামতো আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে পারতেন, এমন অভিযোগ করার সুযোগ থেকে যায়। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ (সা) ও কোরআন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। ‘দ্যা ট্রুথ অ্যাবাউট মোহাম্মদ’ গ্রন্থের লেখক রবার্ট স্পেনসার এ ব্যাপারে বলেন,
মুসলমানরা এখন দাবি করে থাকে, এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি, এটি ইসলাম বিদ্বেষীদের বানানো গল্প। কিন্তু তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক যুগের মুসলিম সূত্রগুলোতে (যেমন আল্লামা জামাখশারী) কিংবা আরো আগের ইসলামী সূত্রে (যেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না) এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায়, এটি অস্বীকার করা মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট কঠিন। ঘটনাটি যদি ইসলামের শত্রুদের বানানোই হয়ে থাকে, তাহলে একজন খাঁটি মুসলমান কীভাবে এই ঘটনার উল্লেখ করলেন? অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার বটে!
মোহাম্মদের (সা) মৃত্যুর পর মুসলমানদের লেখা তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে এই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর সাংঘর্ষিক তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে কোরআনে কিংবা ইবনে ইসহাক কর্তৃক লিখিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মহানবীর (সা) প্রথম জীবনীগ্রন্থে এর কোনো উল্লেখ নেই। এমনকি নবম শতকের বিখ্যাত হাদীস সংকলনগুলোতেও এর উল্লেখ নেই। অথচ মুসলমানরা সাধারণত নিছক মোহাম্মদের (সা) সমালোচনা থাকলেই কোনো বর্ণনাকে অস্বীকার করে না। বরং কোনো বর্ণনা যথাযথভাবে যাচাইযোগ্য না হলেই কেবল তা বাতিল গণ্য করা হয়।
দ্য স্যাটানিক ভার্সেস
১৯৮৯ সালে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সালমান রুশদীর লেখা ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’ উপন্যাসের বিরুদ্ধে গোটা মুসলিম বিশ্বে সহিংস প্রতিবাদের ঝড় উঠে। উপন্যাসটি ছিলো ওই ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা একটি কল্পকাহিনী। মুসলমানদের মতে, কোরআনকে শয়তানের কাজ হিসেবে উপস্থাপন করা এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মোহাম্মদকে (সা) এভাবে চিত্রিত করা ছিলো ভণ্ডামিপূর্ণ অপপ্রয়াস। এ ঘটনায় পুরো দুনিয়ার মুসলিম জনমত ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ব্র্যাডফোর্ড কাউন্সিল অব মস্কেসের সভাপতি শের আজম স্মৃতিচারণ করে বলেন,
১৯৮৯ সালের ১৪ জানুয়ারির ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন আমরা হাজার হাজার মানুষ ওই বইটি নিষিদ্ধের দাবিতে সমবেত হয়েছিলাম। আমরা প্রকাশ্যে বইটি পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।
বই পোড়ানোর মাধ্যমে ঘটনার মাত্র শুরু হয়। কয়েক দিনের মাথায় মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সহিংস বিক্ষোভ এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অনেকেই বইটি নিষিদ্ধকরণের দাবির বিরোধিতা করেন। ঘটনার এক পর্যায়ে ইরানের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইস্যুটিকে কাজে লাগান। তিনি সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে রুশদীকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করেন। ফতোয়াটি এখন পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়নি। এই বইয়ের সাথে যুক্ত অনেকেই আক্রমণের শিকার হয়েছে, এমনকি নিহতও হয়েছে। তবে রুশদী এখনো অক্ষতভাবে বেঁচে আছেন।
মোহাম্মদ (সা) আসলে কে ছিলেন, তাঁর কী অবদান ছিলো এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, বর্তমান যুগে মুসলমান বলতে কী বুঝায়– এই সমস্ত প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে তাঁর জীবনের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার (যা আবার আদতেই ঘটেনি বলে অধিকাংশ মুসলিম স্কলার মনে করেন) আলোকে মোহাম্মদের (সা) জীবন ও কর্মকে বিবেচনা করা নিতান্ত মতলবী কাজ।
এই ইস্যুটির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্য মনে করে, ইসলামের ব্যাপারে যা খুশি বলার অধিকার তাদের রয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানরা মনে করে, অপমানিত না হওয়ার অধিকারও তাদের রয়েছে। জিয়াউদ্দীন সরদার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,
এ ঘটনাটির প্রতিবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ মুসলিমরা একটি স্বতন্ত্র কমিউনিটি হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। সেদিক থেকে বৃটিশ মুসলিমদের জন্য এটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। তবে আন্তর্জাতিকভাবেও মুসলমানদের জন্য সময়টি তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো। কারণ, একদিকে তারা রুশদীর লেখাকে প্রত্যাখ্যান করছিলো, এর প্রতিবাদে সভা-সমাবেশ করছিলো। অন্যদিকে রুশদীর বিরুদ্ধে দেয়া ফতোয়ার নিন্দা জানাতেও তারা সমবেত হয়েছিলো। পাশ্চাত্যে যা ঘটছে, সেটি যেমন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; তেমনি ট্র্যাডিশনাল ইসলামের কিছু ব্যাপারও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। উভয় দিকের বাস্তবতাই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো।
মোহাম্মদের (সা) প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে বৃটিশ মুসলিমরাও যে বৃহত্তর বিশ্ব মুসলিম সমাজের অংশ, এ ঘটনার পর তারা সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। পাশ্চাত্যের প্রধান পরিচয় তথা ‘উদার মূল্যবোধের’ সাথে ব্রিটিশ মুসলিম সমাজের তুলনামূলক রক্ষণশীল ও ট্র্যাডিশনাল মূল্যবোধের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হিসেবেও ঘটনাটিকে চিহ্নিত করা যায়। মোহাম্মদ (সা) কি বিশ্বের জন্য কল্যাণকর, নাকি ক্ষতিকর– পরস্পরবিরোধী এই বিতর্ক হলো এই দ্বন্দ্বের মূল বিষয়। এর পাশাপাশি মোহাম্মদের (সা) ব্যক্তিচরিত্রকেও অনেক সময় বিতর্কে টেনে আনা হয়।
কোরাইশদের বয়কট ও মহানবীর অহিংস প্রতিরোধ
যা হোক, মোহাম্মদ (সা) তৎকালীন মক্কার কোরাইশদের প্রাচীন গোত্রীয় মূল্যবোধের বিপরীতে এক আল্লাহর ধারণা সংক্রান্ত নতুন বাণী নিয়ে সাংঘাতিক এক মতাদর্শিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফলে কোরাইশরা মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের উপর আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তারা ঘোষণা করলো, এখন থেকে কেউই তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, এমনকি খাদ্যদ্রব্য কেনাবেচাও করতে পারবে না। কিন্তু এই চরম উসকানিমূলক পরিস্থিতিতেও তিনি ও তাঁর সাথীরা কোনো রকম সংঘাতে না জড়িয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিলেন। বর্তমানে কোনো কোনো মুসলমানের কর্মকাণ্ডের এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অধ্যাপক সাজ্জাদ রিজভী বলেন,
ইসলামের একদম প্রাথমিক যুগে সহিংসভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা আসলে সম্ভবই ছিলো না। তখন মুসলমানদের সংখ্যা কোনোভাবেই শ’দুয়েকের বেশি ছিলো না। মুসলমানরা তখন যদি মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হতো, তাহলে তারা গণহারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হতো। সেক্ষেত্রে এত বছর পর এসেও আমরা যে ইসলামকে জানি, তার নাম-নিশানা তখনই মুছে যেতো।
এভাবে চলার এক পর্যায়ে মোহাম্মদ (সা) ধারাবাহিক অহিংস প্রতিরোধের সুফল পেতে শুরু করলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গৃহীত এ ধরনের চরম পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মক্কার লোকেরাই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করলো। মুসলমানরা তো আসলে তাদেরই স্বজন ও গোত্রের সদস্য ছিলো। ফলে কোরাইশ নেতৃবৃন্দের উপর ব্যাপক সামাজিক চাপ তৈরি হলো। অব্যাহত চাপের মুখে দুই বছর পর তারা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে এর ফলে মোহাম্মদের (সা) দুঃখ-কষ্ট লাঘব হলো না। বরং শুরু হলো বলা যায়। তাই ওই বছরটিকে মুসলমানরা দুঃখ-দুর্দশার বছর হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

স্ত্রী ও চাচার মৃত্যু
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কয়েক মাসের মধ্যে মোহাম্মদের (সা) জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি স্ত্রী খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় তিনি একদম ভেঙে পড়েছিলেন। বিগত ২৫ বছর ধরে এই নারী ছিলেন একাধারে তাঁর একান্ত ভালোবাসার স্ত্রী, সবচেয়ে ঘনিষ্ট সঙ্গী এবং প্রধান পরামর্শদাতা। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নবুয়ত লাভের পর তাঁর যে ভয়াবহ দিনগুলো কেটেছে, তখন তিনিই প্রথম তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। খাদীজার (সা) অবদান সম্পর্কে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
খাদীজা ছিলেন অসাধারণ বিস্ময়কর একজন মানুষ। তিনিই সর্বপ্রথম ওহীর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এদিক থেকে বলা যায়, তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম। কারণ, স্বয়ং মহানবীরও আগে তিনি ঐশীবাণীর উপর ঈমান এনেছিলেন। সত্যকে চিনে নেয়ার সহজাত ক্ষমতা তাঁর ছিলো। তাঁর ব্যাপারে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলো দেখলে মনে হয়, তিনি ছিলেন মায়ের মতোই মমতাময়ী। তাঁর মৃত্যুতে মহানবী যেন মাতৃতুল্য একজন অভিভাবককেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। আসলে তিনি খাদীজাকে অনেক ভালোবাসতেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, একজন ধনী বিধবাকে বিয়ে করা মহানবীর সুবিধাবাদিতা ছিলো বলে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা প্রায় সময়ই অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু কোনো বর্ণনা থেকেই এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনি সারাজীবন খাদীজাকে ভালোবেসে গিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী স্ত্রীগণ কোনো প্রসঙ্গে খাদীজার কথা উল্লেখ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কারণ তাঁরা জানতেন, তাঁদের কেউই মহানবীর হৃদয়ে খাদীজার সমান জায়গা করে নিতে পারেননি।
খাদীজার মৃত্যুর কয়েক মাস পর মোহাম্মদের (সা) জীবনে আরো একটি বিপর্যয় নেমে আসে। এবার তাঁর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। এই মানুষটি তাঁকে কোরাইশদের সর্বপ্রকার কোপানল থেকে রক্ষা করতেন। চাচার মৃত্যুর পর মোহাম্মদের (সা) গোত্রের নেতৃত্ব চলে যায় তাঁর বিরোধী পক্ষের সবচেয়ে উগ্র ব্যক্তিদের হাতে। ফলে তাঁর উপর আবারো আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়। তাঁর শত্রুরা এবার তাঁকে স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে দিলো– হয় দাওয়াতী কাজ বন্ধ করো, নয়তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো।
মোহাম্মদ (সা) ও সাথীদের ক্ষুদ্র দলটি এবার সবচেয়ে অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁদের অর্ধেক গিয়ে আশ্রয় নিলেন ইথিওপিয়ায়। আর বাকিদের মক্কায় নির্যাতন সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। শত্রুরা এবার তাঁর ইসলামী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিতে প্রকাশ্যে পরিকল্পনা করতে লাগলো। এমনকি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনাও করতে লাগলো।
এই পরিস্থিতিতে তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিলো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সেটি নিছক তাঁর নিজের ভবিষ্যতই নয়, বরং পুরো দুনিয়ার ইতিহাসকেই পাল্টে দিয়েছিলো।
দ্বিতীয় পর্ব: হলি ওয়ার
মেরাজের ঘটনা
৬২০ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদের (সা) সবচেয়ে বড় দুজন শুভাকাঙ্খী মৃত্যুবরণ করেন। একজন হলেন তাঁর ২৫ বছরের বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী খাদীজা (রা)। অপরজন হলেন তাঁকে গোত্রীয় নিরাপত্তা প্রদানকারী চাচা আবু তালিব। ওই সময়টি ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এমন এক অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যা তাঁর এই দুঃসহ যাতনাকে মুছে দিয়েছিলো।
মুসলিম বর্ণনা মতে, এক রাতে মোহাম্মদ (সা) কাবার আঙিনায় ঘুমিয়েছিলেন। সেই রাতেই তিনি মক্কা থেকে কয়েক শত মাইল উত্তরে অবস্থিত জেরুজালেম নগরী ভ্রমণের এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইহুদী-খ্রিস্টানরা নগরীটিকে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করে। মহানবীর (সা) এই নৈশভ্রমণের ঘটনার ফলে মুসলমানদের কাছেও মক্কা-মদীনার পরেই তীর্থযাত্রা ও গভীর ধর্মীয় অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য জেরুজালেম নগরী পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত।
বর্তমানে জেরুজালেম নগরী মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। ইসরাইলী ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে চলমান সংঘাত কার্যত এই ভূমির জন্য দুই পক্ষের লড়াই। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব জুড়ে এই ইস্যুটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো? কেনইবা মহানবীর (সা) জন্মস্থান থেকে প্রায় আটশত মাইল দূরের একটি নগরী জেরুসালেমকে মুক্ত করার আহ্বান অসংখ্য মুসলমানকে এখনো উজ্জীবিত করে? জেরুসালেমের সাবেক প্রধান মুফতি শায়খ ইকরিমা সাবরী এ ব্যাপারে বলেন,
জেরুসালেম হলো মুসলমানদের ঈমান-আকীদার প্রতীক। তাই এটি আমাদের নিকট এতো গুরুত্বপূর্ণ। মহানবীর (সা) রাত্রীকালীন ভ্রমণের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। এখান থেকেই ঊর্ধ্বারোহণ তথা মিরাজের ঘটনা ঘটে। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদকে (সা) প্রথমে মক্কা থেকে জেরুসালেমে পাঠিয়েছিলেন। তারপর এখান থেকে তিনি ঊর্ধ্বাকাশপানে রওয়ানা হয়েছিলেন।
মুসলিম সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই রাতে ফেরেশতা জিবরাইল এসে মহানবীকে (সা) জাগিয়ে তুলেন। তারপর বোরাক নামের একটি উড়ন্ত ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যান। এতে চড়ে তিনি অলৌকিকভাবে বিস্তৃত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে জেরুসালেমে পৌঁছেন। এখানে এসেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী ও অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতাটির শুরু হয়। এই ভ্রমণে তাঁর সাথে ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে মুসা (আ), ঈসা (আ) সহ অতীতের সকল নবী-রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সবাইকে নিয়ে সেখানে তিনি নামাজ আদায় করেন। তারপর তাঁকে পানি, মদ ও দুধ অফার করা হয়। তিনি সেখান থেকে শুধু দুধ পান করেন। তিনি সারাজীবন যে মধ্যপন্থার পক্ষে কথা বলেছেন, দুধ পান করে তিনি তাঁর সেই অবস্থানই পুনর্ব্যক্ত করলেন। তারপর একটি স্বর্গীয় সিঁড়ি দৃশ্যমান হয়ে ওঠলো এবং মোহাম্মদ (সা) এক আধ্যাত্মিক ঊর্ধারোহণ শুরু করেন। সপ্ত আসমান পেরিয়ে তিনি আরশে আজীমে পৌঁছেন এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলেন।
আধুনিক যুক্তি-প্রমাণের এই যুগে একে অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা মনে হলেও মুসলমানদের নিকট এটি হলো মোহাম্মদের (সা) জীবনে সংঘটিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য, এই ভ্রমণ কি স্বশরীরে ছিলো, নাকি এটি ছিলো নিছক একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা– তা নিয়ে অমুসলমানদের মধ্যে তো বটেই, মুসলিমদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। মুফতি শায়খ ইকরিমা সাবরী এ ব্যাপারে বলেন,
এটি ছিলো একটি অলৌকিক ব্যাপার। আর অলৌকিকতায় বিশ্বাস রাখা ঈমানেরই অংশ। এই ঘটনার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই এবং এটি স্বাভাবিকতার বিপরীতও বটে। তবুও কোরআন ও হাদীসে এ ঘটনার বর্ণনা থাকায় আমরা তা বিশ্বাস করি।
অধ্যাপক তারিক রমাদান বলেন,
আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এটি ছিলো একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবহ ভ্রমণ। অর্থাৎ, তিনি প্রথমে জেরুসালেম গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি মহান স্রষ্টা তথা এক আল্লাহর খুব সন্নিকটবর্তী হয়েছিলেন।
জেরুসালেমের ‘ডোম অব দ্যা রক’ খ্যাত সোনালী মসজিদটির ভেতরে একটি পবিত্র স্মারক রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, মেরাজের রাতে ঠিক সেখান থেকেই মহানবী (সা) ঊর্ধ্বারোহন শুরু করেন। অতীতকাল থেকে এখনো পর্যন্ত কেউ কেউ বলে থাকেন, মহানবী (সা) স্বশরীরেই ভ্রমণ করেছিলেন। তাদের মতে, তিনি চোখের পলকে মক্কা থেকে প্রায় আটশত মাইল দূরের জেরুসালেমে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবে অনেকে মনে করেন, রাত্রীকালীন ভ্রমণ একটি প্রতীকী ব্যাপার। আসলে সেটি ছিলো একটি আধ্যাত্মিক সফর, যে সফরে মহানবী (সা) এক নতুন স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আব্দুর রহীম গ্রীন এ ব্যাপারে বলেন,
এই ঘটনার প্রতীকী গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, সেই রাতে ইবরাহীম, নূহ, মুসা, ঈসা, ইয়াকুবসহ অতীতের সকল নবী-রাসূল মোহাম্মদের (সা) নেতৃত্বে নামাজ আদায় করেছেন। সেদিন স্বয়ং আল্লাহ মহানবীর (সা) সাথে কথা বলেছেন। সেই কথোপকথনেই আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।
বারনাবি রজারসন এ ব্যাপারে বলেন,
কোরআনে ঘটনাটির বর্ণনা খুঁজতে গেলে আপনি মাত্র তিনটি ছোট্ট রেফারেন্স পাবেন। কিন্তু ঘটনার বিস্তারিত অর্থাৎ, মহানবীর মেরাজে যাওয়া, বোরাকে চড়া, অতীতের নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ, জেরুসালেমে যাওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ লাভ, বেহেশত-দোজখ পরিদর্শন, আরশে আজীমে গমন– এই সমস্ত বর্ণনা মুসলিম বিশ্বে এক ধরনের বিস্ময়কর ও মহাজাগতিক আবহ তৈরির জন্য পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছে। কোরআনে এসবের কোনোটিরই উল্লেখ নেই।
ম্যারল ওয়েন ডেভিস এ ব্যাপারে বলেন,
ধর্মের ইতিহাস মাত্রেরই নানা রকম বাহুল্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে। তাই ব্যাপারটি কোরআনে কতবার রয়েছে, সেটি বড় কথা নয়। কোরআনে এ ঘটনার উল্লেখ থাকার মানেই হলো এটি তাৎপর্যপূর্ণ।
রাত্রীকালীন সফরে জেরুসালেম যাওয়া এবং বেহেশতে গিয়ে ইহুদী-খ্রিস্টানদের অতি পরিচিত নবী ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে অতীতের সকল নবী-রাসূলের সাথে সাক্ষাতের ঘটনা ছিলো মহানবীর (সা) জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলমানদের দৃষ্টিতে, এই ঘটনার মাধ্যমে অন্যান্য নবী-রাসূলগণও ঐশীবাণীর সর্বশেষ বাহক হিসেবে মোহাম্মদকে (সা) স্বীকার করে নিয়েছেন। এটি ছিলো আল্লাহরই হুকুম। ইসলাম ও তার অনুসারীরা যে সনাতন ইবরাহীমীয় ধারারই ধারাবাহিকতা মাত্র, এই সফরের মাধ্যমে সেই স্বীকৃতিও পাওয়া গেলো। এই ঘটনার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, মোহাম্মদ (সা) এখন তাঁর গোত্রীয় অতীতকে পেছনে ফেলে পুরো দুনিয়ার সামনে তাঁর বাণী তুলে ধরতে প্রস্তুত। ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
মহানবীর মেরাজের ঘটনার মাধ্যমে গোত্রবাদকে পেছনে ফেলে মানবতাকে আলিঙ্গন করা হয়েছে। বলা যায়, ঘটনাটি হলো গোত্র পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ওঠে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোর একটি উদ্যোগ। এটিই হলো এই ঘটনার ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপর্য।
মেরাজের ঘটনাটি ছিলো মহানবীর (সা) জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। একইসাথে তাঁর নবুয়তী মিশনের নতুন একটি ধাপের সূচনাও বটে। তবে এটি একটি নতুন পর্যায়ই শুধু নয়, এটি ছিলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর গোত্রীয় জীবন চিরতরে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মক্কা শহরে কোরাইশদেরকে পরাভূত করার পরিবর্তে তিনি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে নব উদ্যমে মিশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
ইয়াসরিববাসীর সাথে বৈঠক
একদিন মোহাম্মদ (সা) ইয়াসরিব থেকে আগত একদল লোকের সাথে এক ছোট্ট মরুদ্যানে একটি বৈঠক করেন। ইয়াসরিব হলো মক্কা থেকে উত্তরে ১৫ দিন উটের পিঠে করে সফরের দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ও হানাহানির কারণে তারা যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে কথা তারা মহানবীকে (সা) জানালো। মহানবী (সা) তাদের সব কথা শুনলেন। জবাবে তাঁর মিশন, আল্লাহর একত্ববাদ, সৎভাবে জীবনযাপনের গুরুত্ব এবং জান্নাতে পুরস্কার লাভের কথা তাদেরকে বললেন। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, তারা মহানবীর (সা) সব কথা শুনে অভিভূত হলো। মক্কার লোকেরা যেখানে এসব কথা শুনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতো, সেখানে এদের প্রতিক্রিয়া ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ইয়াসরিব থেকে আগত ছয়জনের এই দলটি সেদিন ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সেদিনের বৈঠক শেষ হয়। যাওয়ার আগে তারা মহানবীর (সা) সাথে আবারো দেখা করার কথা দিয়ে যায়।
ইতোমধ্যে মক্কার পরিস্থিতি মোহাম্মদের (সা) জন্য চরম প্রতিকূল হয়ে উঠছিলো। এক পর্যায়ে তিনি অনুভব করলেন, ইয়াসরিবে চলে যাওয়া ছাড়া তাঁর অনুসারীদের পক্ষে আর কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এটি ছিলো অকল্পনীয় ব্যাপার। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অর্থ হলো, তাদের আর কোনো গোত্রীয় নিরাপত্তা বজায় থাকছে না। একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়েই সেখানে তাদের বাস করতে হবে। ড. আমিরা বেনিসন এ ব্যাপারে বলেন,
বেশ কয়েকটি গোত্র মিলে ছিলো ইয়াসরিবের সমাজ। এদের কেউ ছিলো পৌত্তলিক, কেউ আওস গোত্রের, কেউবা খাযরাজ গোত্রের, আবার কেউ কেউ ছিলো ইহুদী। ইহুদীদের তিনটি প্রধান গোত্র ছিলো সেখানে। তবে কর্তৃত্ব নিয়ে তৎকালীন ইয়াসরিবে অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের জন্য তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকতো। এই পরিস্থিতিতে তারা একজন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন উপলব্ধি করলো। এরই মাঝে মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তারা জানতে পারলো। তিনি তখন মক্কায় দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আরব উপদ্বীপের এই অঞ্চলটাতে তাঁর নাম ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে তারা মনে করলো, এই ব্যক্তিই হয়তো তাদের চলমান বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারবেন, তিনিই হয়তো ন্যায়বিচারকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন, তাঁর পক্ষেই হয়তো ইয়াসরিবে এসে তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা সম্ভব হবে।
এক বছর পর ইয়াসরিব থেকে আরেকটি প্রতিনিধিদল মহানবীর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো। এই দলটি ছিলো আরো বড়। এবার তারা রাতের আঁধারে গোপনে দেখা করলো। এই বৈঠকে ইয়াসরিববাসী ও মোহাম্মদের (সা) মধ্যে একটি ঐক্যমত হয়। মহানবী (সা) তাদেরকে বললেন, ‘আমি তোমাদের জন্য, আর তোমরা আমার জন্য’। এই ঐক্যমতের ঘটনাটি ছিলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তখনকার সময়ে এ ধরনের চুক্তি ছিলো একেবারেই নতুন ব্যাপার। সে হিসেবে এটি দুঃসাহসী সিদ্ধান্তও ছিলো বটে। কারণ, এই চুক্তি কোনো গোত্রীয় মৈত্রী, পারিবারিক বন্ধন কিংবা উপজাতীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি। বরং জ্ঞাতিসম্পর্কের ঊর্ধ্বে ওঠে এমন এক গ্রাউন্ডে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, যা ছিলো সার্বজনীন। চুক্তিটির তাৎপর্য সম্পর্কে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
এক দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তটি ছিলো অসামান্য দুঃসাহস, হিম্মত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। নিজের গোত্র ও রক্তসম্পর্ক চিরতরে ত্যাগ করে অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা এর আগে আরবে মোটেও শোনা যায়নি। এ ধরনের কাজ ছিলো রীতিমতো ব্লাসফেমি। অলঙ্ঘণীয় গোত্রব্যবস্থার ধারণা ছিলো আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত মূল্যবোধ। মোহাম্মদ এই ব্যবস্থাকে ত্যাগ করে ‘উম্মাহ’ নামে নতুন এক সমাজব্যবস্থার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন, যা কোনো বংশ বা গোত্রীয় সম্পর্কের পরিবর্তে আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আরবদের কাছে এই পুরো ব্যাপারটি ছিলো একদম নতুন একটি বিষয়।
মহানবীকে হত্যার প্রচেষ্টা
মক্কার শাসকগোষ্ঠী মোহাম্মদের (সা) পরিকল্পনা টের পেয়ে গেলে ভয়াবহ পরিণতি ঘটে যেতে পারে। তাই কোরাইশরা সতর্ক হওয়ার আগেই মোহাম্মদ (সা) তাঁর সাথীদেরকে শহর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। পরবর্তী কয়েক মাস ধরে প্রতি রাতেই তাঁর অনুসারীদের কেউ না কেউ শহর ত্যাগ করতে লাগলো। মোহাম্মদ (সা), তাঁর ঘনিষ্ট সাথী আবু বকর (রা), তাঁর কিশোর চাচাতো ভাই আলীসহ (রা) গুটিকতক অনুসারী বাদে বাকিরা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কোনো রকম সন্দেহ করতে পারেনি।
ইতোমধ্যে কোরাইশরাও মোহাম্মদকে (সা) হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটলো। ঠিক করা হলো, তাঁকে হত্যার অভিযানে মক্কার প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে অংশ নেবে। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদের (সা) গোত্রের পক্ষে হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়বে, সেই চিন্তা থেকেই এই ব্যবস্থা।
এক রাতে তারা মোহাম্মদের (সা) বাড়ি ঘেরাও করে ফেললো। তাদের কাছে মনে হচ্ছিলো, তাঁর শোবার ঘরে কেউ একজন ঘুমিয়ে আছে। হত্যা করার উদ্দেশ্যে তারা খঞ্জর নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু তারা সেখানে মোহাম্মদের (সা) পরিবর্তে পেলো তাঁর চাচাতো ভাই আলীকে (রা)। মোহাম্মদ (সা) ততক্ষণে তাদের চোখের আড়ালে চলে গেছেন। বারনাবি রজারসন এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,
তিনি ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি। তারা তাঁকে হত্যা করতে গিয়েছিলো। এই হত্যা প্রচেষ্টা থেকে তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তারপর আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন। মক্কা ত্যাগের আগে তিনি প্রত্যেকের আমানত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সততার ব্যাপারে জনগণের সমর্থন আদায় এবং তাঁর বিরোধীদের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে এটি কাজ করেছিলো।
আবু বকরকে সাথে নিয়ে মোহাম্মদ (সা) গোপনে মক্কা ত্যাগ করে নতুন ঠিকানা ইয়াসরিবে যাত্রা করেন। মক্কার লোকেরা তাঁকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তারা তাঁর গমন পথের পায়ের তাজা ছাপও খুঁজে বের করে ফেললো। ধাওয়াকারীরা সাওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু পর্বতের চূড়ায় ওঠেও তারা মোহাম্মদকে (সা) খুঁজে পায়নি, এমনকি তাঁর পায়ের ছাপও চিহ্নিত করতে পায়নি। বাধ্য হয়ে তারা মক্কায় ফিরে যায়। কিন্তু মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথী আবু বকর (রা) তখনো সাওর পর্বতের একদম চূড়ায় একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। বিপদ কেটে যাওয়ার পর তাঁরা ইয়াসরিবের দিকে যাত্রা করেন।
মদীনায় হিজরত
এই ঘটনাটি ঘটে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে মোহাম্মদের (সা) বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তিনি একজন এতিম হিসেবে মক্কায় বেড়ে ওঠেছিলেন। চাচার বাণিজ্য কাফেলার সাথে অনেকবার সফরের কারণে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা ছিলো। তিনি ছিলেন বিবাহিত। তাঁর কাছে নিয়মিত আল্লাহর বাণী নাজিল হতো। কিন্তু নিজ গোত্রের কাছেই তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর প্রায় শ’দুয়েক অনুসারী মাতৃভূমিতে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চরম অবমাননা ও নির্যাতনের শিকার ছিলেন। সর্বশেষ, লোকেরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এমতাবস্থায় গৃহত্যাগ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি স্থানে তাঁকে চলে যেতে হয়। এই ঘটনাটি ‘হিজরত’ হিসেবে পরিচিত, যার আক্ষরিক অর্থ হলো অতীতের সাথে ‘সম্পর্কচ্ছেদ’। এ ঘটনার পর মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের আর পেছনে ফিরে তাকানোর কোনো সুযোগ ছিলো না। এ ব্যাপারে বারনাবি রজারসন বলেন,
তিনি সেখানে ধর্মপ্রচারক হিসেবে গিয়েছিলেন। বিজেতা হিসেবে যাননি। ইয়াসরিববাসীরাই তাঁকে বলেছিলো, ‘এখানে আসুন এবং আমাদের মাঝে মধ্যস্থতা করে দিন। আমরা আপনাকে একজন রাসূল ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করবো। আপনার কথার উপর আমরা আস্থা রাখি।’ তিনি সেখানে দখলদার সেনাবাহিনী নিয়ে যাননি। একজন শরনার্থী ও নির্বাসিত ব্যক্তি হিসেবে, একজন সম্মানিত ও মর্যাদাবান নেতা হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন।
তবে ‘নাউ দে কল মি ইনফিডাল’ গ্রন্থের লেখিকা ননী দারভীশ বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,
মোহাম্মদ মক্কায় ১৩ বছর ধরে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। সেখানে তার সর্বোচ্চ দেড়শ জনের মতো অনুসারী ছিলো। তিনি দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তিনি জানতেন, মক্কায় থেকে তাদের সাথে লড়তে গেলে তিনি হেরে যাবেন। এ জন্য যথাসময়েই তিনি মক্কা ত্যাগ করেন। কারণ, তিনি তার বাণীকে আরো বেশি ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। এ জন্য মক্কার বাইরে তিনি এমন একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলেন, যেখান থেকে সত্যিকার অর্থে মক্কার মানুষদেরকে আঘাত করতে পারবেন এবং মক্কা জয় করতে পারবেন।
ড. আমিরা বেনিসন বলেন,
হিজরত তথা মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়া ছিলো মোহাম্মদের (সা) জীবনের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।
মোহাম্মদের (সা) জীবনে হিজরতের ঘটনাটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবীর মক্কা ত্যাগের দিন থেকে ইসলামী ক্যালেন্ডারের যে সূচনা ঘটেছে, আজ পর্যন্ত সেই ক্যালেন্ডার মোতাবেকই ইসলামের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ পালিত হয়। এর তাৎপর্য সম্পর্কে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
খ্রিস্টানদের মতো নবীর জন্মদিনকে বিবেচনা না করে, নবীর হিজরতের দিনকে মুসলিম যুগের শুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। গোত্রীয় স্পিরিটের সাথে সম্পর্কচ্ছেদকে নতুন যুগের সূচনা হিসেবে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে অসাধারণ ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে বলে আমি মনে করি।
মদীনায় নতুন জীবন
মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা মক্কার সাথে ইয়াসরিবের কোনো মিলই খুঁজে পেলেন না। ইয়াসরিব ছিলো মূলত একটি বিশাল মরুদ্যান। অনেকগুলো বস্তি নিয়ে শহরটি গড়ে ওঠেছে। প্রত্যেক বস্তিতেই একেকটা গোত্রের প্রাধান্য ছিলো। সেখানে গোত্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং এর পরিণামে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটতো।
মহানবীর (সা) সম্মানে পরবর্তীতে ইয়াসরিবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মদীনাতুন নবী তথা নবীর শহর। সংক্ষেপে বলা হয় মদীনা। এ ব্যাপারে বারনাবি রজারসন বলেন,
মহানবীর সাথীরা এসেছিলেন একদম খালি হাতে। মক্কার অভিজাত ব্যবসায়ী থেকে তাঁরা হঠাৎ করেই গরীব ও নিঃস্ব মানুষে পরিণত হলেন। বিত্তশালী মরুদ্যানটিতে তাঁরা পুরনো ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতেন। নতুন পরিবেশে এসে রুটি-রুজির জন্য তাঁরা ভুট্টা চাষ করেছেন, মাদুর বুনেছেন। এভাবে তারা পরিস্থিতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন।
মদীনা মিউজিয়ামের কর্মকর্তা খালিদ আল খায়েরের সাথে এ বিষয়ে আমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়–
– মোহাম্মদ (সা) যখন মদীনায় আসেন, তখন মদীনার অবস্থা কেমন ছিলো?
– তখনো মদীনা পরিপূর্ণ শহর হিসেবে গড়ে ওঠেনি। বলতে পারেন, ছোট ছোট সম্প্রদায় মিলে…
– তারমানে, বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায় মিলে মদীনার সমাজ গড়ে ওঠেছিলো?
– হ্যাঁ, তাই। মদীনার কেন্দ্রস্থলে মহানবী (সা) ও আনসারদের মূল অংশটি বসবাস করতেন। কুবা ও কেবলাতাইন এলাকায় অনেকে বসবাস করতো। মদীনার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ছিলো ইহুদীদের বাস। অনেকগুলো গোত্র এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। সব মিলিয়ে পুরো অঞ্চলকে তখন মদীনা নামে ডাকা হতো।

মসজিদে নববী
স্বাধীন পরিবেশে মোহাম্মদ (সা) মদীনায় একটি নিজস্ব মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি ছিলো তাঁর ঘরের বর্ধিত অংশ। খালিদ আল খায়েরের সাথে এ প্রসঙ্গে আমার কথোপকথন–
– মদীনায় মহানবীর (সা) নির্মিত প্রথম মসজিদটি সম্পর্কে কিছু বলুন।
– মদীনার কেন্দ্রস্থলে তিনি একটি জায়গা পেয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।
– এই জাদুঘরে মসজিদটির তৎকালীন আকৃতির একটি রেপ্লিকা রয়েছে দেখেছি। মদীনায় এখন যে মসজিদে নববী, সেটি দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ ও প্রধানতম মসজিদ। অন্যদিকে রেপ্লিকাটি একদম সাদামাটা। এর সাথে তো বর্তমান মসজিদটির বিশাল পার্থক্য রয়েছে…।
– হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু দেখুন, আমরা ১৪’শ বছর আগের কথা বলছি। তখন মসজিদটি ছিলো খুবই সাদামাটা। দৈর্ঘ্যে ৫৫ মিটার, আর প্রস্থে ৩৫ মিটার। তৎকালীন মদীনার অন্যান্য আবাসস্থলের মতোই এটি নির্মিত হয়েছিলো কাদামাটি দিয়ে। ফাউন্ডেশনে ব্যবহার করা হয়েছিলো পাথর। ছাদে ব্যবহৃত হয়েছিলো খেজুর গাছ। মসজিদের পেছনের অংশের ছাদ খোলা রাখা হয়েছিলো।
সেই মসজিদটিই কালের বিবর্তনে আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে নববীতে একইসাথে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ নামাজ আদায় করতে পারে।
মোহাম্মদ (সা) মসজিদটিকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এখানে তিনি শুধু ধর্মীয় কাজই করতেন না, অফিস হিসেবেও মসজিদটিকে তিনি ব্যবহার করতেন। এখানে বসে তিনি লোকদের নানা রকম বিরোধ মিটিয়ে দিতেন, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, পাবলিক ডিবেটের আয়োজন করতেন। ইহুদী, খ্রিস্টান, কাফের, এমনকি দাস-দাসীসহ যে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারতো। সেখানে তাঁর সাথে বসে সবাই কথা বলতে পারতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, মসজিদটি প্রতিষ্ঠার ফলে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ এখানে এসে শান্তিপূর্ণভাবে ইবাদত করতে পারতেন।
আজানের প্রচলন
এবার তাঁরা নতুন এক সমস্যায় পড়লেন। নিরাপদে ইবাদত করার সুযোগ তো হলো, কিন্তু নামাজের সময় হলে লোকজনকে ডাকার জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা তখনো পর্যন্ত ছিলো না। প্রচলিত বর্ণনা অনুযায়ী, একদিন মহানবী (সা) সবাইকে মসজিদের আঙিনায় জড়ো করলেন। নামাজের জন্য ডাকার সবচেয়ে ভালো উপায় কী হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করা ছিলো উদ্দেশ্য। লোকজনকে খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হবে, নাকি ইহুদীদের মতো সাইরেন বাজিয়ে ডাকা হবে, নাকি অন্য কোনো পদ্ধতিতে, যেমন– আগুন জ্বালিয়ে নামাজের জন্য আহ্বান করা হবে, তা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। অবশেষে মানুষের কণ্ঠে নামাজের আহ্বান তথা আজান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হলো। এটি নতুন ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বিশেষায়িত করে।
আজান দেয়ার জন্য মোহাম্মদ (সা) প্রথমে যাকে মনোনীত করেন, সেটিও ছিলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন মুক্ত আফ্রিকান দাস। তাঁর নাম ছিলো বেলাল (রা)। তিনি মক্কায় নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তখন আরবের সর্বত্রই দাসব্যবস্থার প্রচলন ছিলো। মোহাম্মদ (সা) এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ না করলেও তিনি ও তাঁর সাহাবীরা বেলালের মতো আরো অনেক দাসকে মুক্ত করেছিলেন। নামাজের ওয়াক্তে মসজিদের ছাদে ওঠে বেলাল (রা) উচ্চস্বরে আজান দিতেন।
তখন থেকেই এটি মুসলমানদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। বিশ্বব্যাপী এখনো আজানের বাক্য হুবহু একইরকম। তবে স্থানভেদে এর সুরের পার্থক্য রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে মসজিদ ও এর স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মিনার ইসলামের অন্যতম প্রতীকী চিহ্নে পরিণত হয়েছে। ইসলামে মসজিদের তাৎপর্য সম্পর্কে ম্যারল ওয়েন ডেভিস বলেন,
মসজিদ নিছক ইবাদতের স্থান নয়। মসজিদ হলো সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ, ইসলামের মিশন হলো মানুষকে সংশোধন করা। এই মিশন বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই মসজিদকে কেন্দ্র করে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। বিশেষ করে, অভাবী মানুষের জন্য সামাজিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদ একইসাথে একটি শিক্ষাকেন্দ্রও বটে। মসজিদগুলো এ রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইসলামের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্যই এটি সহায়ক। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে এসব মোটেও দেখা যায় না। তাছাড়া মসজিদ শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য উন্মুক্ত হতে হবে। সবাই এখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করবে। কেননা, ইসলামের সামাজিক উদ্দেশ্য এবং সংস্কারমূলক মিশন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং এটি সকলের জন্য।
মদীনা সনদ
মোহাম্মদ (সা) নিছক নতুন একটি ধর্মের নবীমাত্র ছিলেন না। তিনি মদীনার শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মসজিদের আঙিনায় বসেই তিনি যুগপৎভাবে এই দুটি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ কারণে দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর মসজিদেই কাটতো। দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় তিনি এমন একটি চুক্তিতে আসার প্রয়োজন অনুভব করলেন, যা শুধু তাঁর শাসনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিই দিবে না, মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্কও এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এই চুক্তিটিই মদীনার সনদ হিসেবে পরিচিত। ধারণা করা হয়, এটি দুনিয়ার প্রাচীনতম লিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম।
আরবে গোত্রীয় সম্পর্কের পরিবর্তে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলার এটিই ছিলো প্রথম উদ্যোগ। পৌত্তলিক, ইহুদী ও মুসলমান– সবাই যেন পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে, সেই জন্য মোহাম্মদকে (সা) পৌত্তলিক ও ইহুদী গোত্রগুলোর আস্থা অর্জন করতে হয়েছিলো।
জর্দানীয় রাজপরিবারের যুবরাজ হাসান বিন তালাল মদিনা সনদের উপর একজন বিশেষজ্ঞ। এ ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো,
মুসলমান, ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় নিয়ে মদীনায় একটি নতুন বহুমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান রচনা ছিলো অপরিহার্য। এর উদ্দেশ্য ছিলো জীবন, সম্পত্তি, উপাসনালয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে আহলে কিতাবদের মধ্যে যেন পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সংবিধানে জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিলো। এই দৃষ্টিতে আপনি একে মুসলমানদের ‘ম্যাগনা কার্টা’ বলতে পারেন। তৎকালীন মদীনা কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিলো না। সেটি ছিলো একটি সিভিল স্টেট। শাসক ও জনগণ উভয়ই ছিলো অভিন্ন আইনের অধীন।
মদীনা সনদের প্রাথমিক ভাষ্যের সম্পূর্ণ অংশ এখন আর পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের লেখায় এর কয়েকটি সংস্করণ পাওয়া যায়। মহানবীর (সা) মৃত্যুর প্রায় শত বছর পর এগুলো লেখা হয়েছিলো। অন্যদিকে, মদীনা সনদ বলে আসলেই কিছু ছিলো কিনা, তা নিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি অব ব্যাকিংহামের পলিটিক্স অ্যান্ড কনটেম্পোরারি হিস্ট্রির অধ্যাপক জিউফ্রে অল্ডারম্যানের কথা হলো,
‘মদীনা সনদ’ বলে কি আসলেই কিছু ছিলো? আমরা তো কেবল একটি নির্দিষ্ট ঘরানার সূত্র থেকেই এ ব্যাপারে জানি, যাদের আবার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা নির্দিষ্ট এজেন্ডা রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, তখন মোটেও কোনো সংবিধান ছিলো না, কোনো চুক্তিও ছিলো না। এগুলো পরবর্তীকালে বানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের অবস্থান বিরোধপূর্ণ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, তখন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। নিশ্চিতভাবেই তখন একটি সংবিধানও ছিলো। মদীনা সনদটি যদি আপনি পড়ে ফেলেন, তাহলে দেখবেন তৎকালীন রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিবেচনায় তাতে চমৎকৃত হওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। এটি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।
তবে সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অ্যারাবিক স্টাডিজের অধ্যাপক হিউ কেনেডি মদীনা সনদের প্রামাণ্যতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন,
মদীনা সনদের যেসব নথিপত্র পাওয়া যায়, সেগুলো যে আসলেই তখনকার, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সনদে যে ধরনের আরবি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা বেশ প্রাচীন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এর মাধ্যমে যেসব বিষয়ের সমাধান করা হয়েছে, তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় সেগুলো ছিলো যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। মদীনার তৎকালীন গোত্রসমূহ, জনগণের সহায়-সম্পদ, বা এ জাতীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে মোহাম্মদের অবস্থান আসলে কী ছিলো, এটি খুবই… এটি নিশ্চয় কোনো সাম্রাজ্য গড়ে তোলার নীলনকশা ছিলো না।
মদীনা সনদ ইসলামী সরকারব্যবস্থার একদম প্রাথমিক মডেল হিসেবে পরিচিত। এতে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি শাসকের দায়দায়িত্বের কথাও স্পষ্টভাবে বলা আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই সনদের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণের গোত্রীয় প্রথা এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিপক্ষের বিচার করার রীতি ভেঙে দিয়ে সবাইকে আইনের শাসনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে খালিদ আল খায়েরের সাথে আমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়েছে–
– মদীনার সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেছিলো।
– ইহুদী ও পৌত্তলিকরাও?
– একদম সবাই। তারা সবাই স্বাক্ষর করেছিলো, যাদেরকে বলা হয়েছে উম্মাহ…
– উম্মাহ মানে কমিউনিটি?
– হ্যাঁ। এই চুক্তির ফলে মদীনার নিরাপত্তার দায় সকলের উপরেই ন্যস্ত ছিলো। আইনের দৃষ্টিতে সবাই ছিলো সমান। বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে তারা রাষ্ট্রটি পরিচালনা করেছিলেন। যেমন, দুজন ইহুদীর মধ্যে ঝগড়া হলে এর মীমাংসার জন্য তারা মহানবীর (সা) কাছে যেতো। তখন তিনি এর ফায়সালা করতেন ইহুদী আইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে তিনি ইসলামী আইন প্রয়োগ করতেন না। একটি পরিপূর্ণ আদালতব্যবস্থা সেখানে ছিলো। একটি রাষ্ট্র হতে গেলে যা যা লাগে, তার সবই সেখানে ছিলো। এই দৃষ্টিতে, তৎকালীন আরবে তিনি একটি পরিপূর্ণ সভ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।
বিশপ মাইকেল নাজির আলী বলেন,
মদীনা সনদের একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এতে আরব পৌত্তলিক, আনসার ও মুহাজির উভয় ধরনের মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিস্টানসহ নগরীর সবাইকে একই উম্মাহ তথা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য মুসলমানরা ‘উম্মাহ’ বলতে বিশ্ব মুসলিম সমাজকে বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধানে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তাই আমাকে যখন কেউ বলে, ‘আমরা একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই’, আমি তখন জিজ্ঞেস করি, ‘এটি কি মদীনা রাষ্ট্রের মতো হবে, নাকি হবে না? যদি না হয়, তাহলে এর কারণ কী?’
মোহাম্মদ (সা) যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই মদীনা সনদ পুরোপুরি কার্যকর ছিলো। তবে তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমবারের মতো এতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। আরো পরে পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকরা একে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন। ম্যারল ওয়েন ডেভিস এ ব্যাপারে বলেন,
এটি বর্তমানে আমাদের অন্যতম বড় সমস্যা। আমার কাছে মহানবীর (সা) জীবনী এবং কোরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, সহাবস্থান অর্থে বহুত্ববাদকে মেনে নেয়া। সমাজে নানান ধরনের বিশ্বাস, মত, পথ ইত্যাদি থাকবেই। সবাই মিলেই একটি সমাজ তথা একটি উম্মাহ হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে। মুসলমানরা এই শিক্ষাকে অবজ্ঞা করছে, দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে মুসলমানরা বহুত্ববাদকে সমাজ গঠনের প্রধান মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আসলে মহানবীর (সা) শিক্ষাকেই অগ্রাহ্য করেছে।
কোরাইশদের হুমকি
মোহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সাহাবীরা মদীনায় এসেছিলেন একদম নিঃস্ব অবস্থায়। তবে মক্কায় তাঁরা প্রতিনিয়ত যে ধরনের অত্যাচার সইতেন, এখানে তা ছিলো না। শত্রুরা তখনো তাদেরকে বিনাশ করার হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছিলো। গোত্রভিত্তিক আরব সমাজে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবল থাকায় এই হুমকিকে আমলে না নিয়ে উপায় ছিলো না।
ফলে মদীনায়ও মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সংকটে পড়ে গেলো। ক্ষমতাধর যে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে মোহাম্মদকে (সা) মক্কা ছাড়তে হয়েছিলো, যারা তাঁর অনুসারীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিলো, তাদের সম্পত্তি দখল করেছিলো, বেঁচে থাকার ন্যূনতম অবলম্বনটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলো, তারা তখনো মুসলমানদেরকে নির্মূল করার পরিকল্পনা করছিলো। এই বিপজ্জনক শত্রুকে মোকাবেলার একটা উপায় খুঁজে বের করা তখন মোহাম্মদের (সা) জন্য ছিলো জরুরি।
যুদ্ধের আয়াত
এই পরিস্থিতিতে তাঁর উপর ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু ওহী নাজিল হয়। যারা তাঁদেরকে বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। কোরআনের এই আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিতর্ক রয়ে গেছে। অনেকের মতে, এগুলো হলো আত্মরক্ষার সাময়িক প্রয়োজনে যুদ্ধের বৈধতার দলীল। অন্যদিকে, মহানবীর (সা) অনুসারী নয়, এমন যে কাউকে হত্যা করার বৈধতার দলীল হিসেবে কেউ কেউ এসব আয়াতকে ব্যবহার করে থাকে। রবার্ট স্পেনসার এ ব্যাপারে বলেন,
কোরআনে সূরা বাকারার ১৯১ ও ২১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ফেতনা-ফ্যাসাদ হলো হত্যার চেয়ে গুরুতর অপরাধ…। অন্যভাবে বললে, ‘কোরাইশরা যদি নির্যাতন করতে থাকে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করার পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে’– এ ধরনের অবস্থান ইসলামী নৈতিকতার এক ধরনের দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। কোনো নৈতিক অবস্থান ইসলামের পক্ষে হলেই কেবল তা ভালো, অন্যথায় তা না মানলেও চলে। এমন মনে করা হলে ইসলামী নৈতিকতার কোনো চূড়ান্ত ভিত্তি থাকে না। যুদ্ধ সংক্রান্ত এই মূলনীতি ছাড়াও অনেকগুলো হাদীসে বর্ণিত মোহাম্মদের আরেকটি বাণী রয়েছে। তিনি প্রায় সময় বলতেন– “যুদ্ধ হলো এক ধরনের প্রতারণা।” তার অনুসারীরা যে প্রতিবেশী এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে সাধারণত মারমুখী ও যুদ্ধন্মোখ হয়ে থাকে, দুঃখজনকভাবে এই মানসিকতার পেছনে রয়েছে ইসলামের যুদ্ধ সংক্রান্ত এই নীতি এবং মোহাম্মদের উল্লিখিত এই হাদীসটি।
তবে অধ্যাপক তারিক রমাদান এ ব্যাপারে বলেন,
নির্যাতনের শিকার হলেই কেবল যুদ্ধ সংক্রান্ত কোরআনের এই অনুমোদন কার্যকর হবে। কেউ আপনাকে আক্রমণ করতে থাকলে প্রতিরোধ করার অধিকার নিশ্চয় আপনার রয়েছে। এ কারণেই ক্লাসিকাল ফিকাহ শাস্ত্রের মূলধারায় একে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বলা হয়। অর্থাৎ, আপনি যদি নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে অধিকারের জায়গা থেকে আপনি এর প্রতিরোধ করতে পারবেন। এখন এ জাতীয় কিছু লোক এবং গুটিকতক মুসলিম গ্রুপ এই আয়াতকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তারা বলছে, ‘বিরোধীদের হত্যা করা আমাদের জন্য বৈধ এবং আমাদের যুদ্ধ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।’ বলাবাহুল্য, তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কোরআনের আয়াতে এ ধরনের কিছু বলা হয়নি। আয়াতে বলা হয়েছে– যদি তারা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহলে তা প্রতিরোধ করার অধিকার তোমার রয়েছে। কারণ, দিন শেষে এটি বাঁচামরার প্রশ্ন।
বদর যুদ্ধ
যা হোক, মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীগণ এক পর্যায়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লেন। কোরআনের এই আয়াতগুলোকে তিনি বড়জোর কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণের বৈধতা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মহানবী (সা) শুনতে পেলেন, কোরাইশদের একটি বিশাল বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। কাফেলাটিকে তিনি মরুভূমিতেই জব্দ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যে এ রকম কিছু করতে পারেন, কোরাইশরা তা আঁচ করতে পেরেছিলো। তাই তারা কাফেলাকে মদীনার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে মোহাম্মদের (সা) মোকাবেলায় একটি সেনাবাহিনী পাঠালো। উভয় বাহিনীই মরুভূমির মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন পানির কূপের কাছে বদর প্রান্তরে মুখোমুখি হলো। অধ্যাপক হিউ কেনেডি বলেন,
মক্কার কোরাইশ বাহিনী এবং মদীনার মোহাম্মদের বাহিনী বদর প্রান্তরে মুখোমুখি হলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধটি শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধে মোহাম্মদের সেনাসংখ্যা নিশ্চিতভাবেই এক হাজারের কম ছিলো। আনুমানিক ৩’শ থেকে ৪’শ জন হবে। আর কোরাইশদের সেনাসংখ্যা ছিলো আনুমানিক ৯’শ জনের মতো। আমরা যদিও সবসময় বলি, মক্কার বাহিনীর সেনাসংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিলো। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা আসলে কী ছিলো, তা জানার কোনো সত্যিকার পদ্ধতি আমাদের কাছে নেই।
‘জিহাদ: ফ্রম কোরআন টু বিন লাদেন’ গ্রন্থের লেখক, পাদরি এবং অধ্যাপক রিচার্ড বোনি বলেন,
মহানবী ছিলেন মদীনায় নির্বাসিত। তাই একদৃষ্টিতে মক্কা ও মদীনার মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধটি ছিলো একটি মতাদর্শিক যুদ্ধ। ব্যাপারটা যেহেতু ঘটেনি, তাই নিশ্চিতভাবে বলতে না পারছি না; তবে আমরা অনুমান করতে পারি– মক্কাবাসীরা জয়ী হলে তাদের চোখে যারা বিদ্রোহী, অর্থাৎ মুসলমানদেরকে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো। কারণ, মক্কাবাসীর জন্য তারা ছিলো বড় ধরনের হুমকি।
যুদ্ধে মক্কাবাসীরা পরাজিত হয়। এর ফলে মদীনাবাসীরা সাময়িকভাবে স্বস্তি লাভ করে। মক্কা ও মদীনার মধ্যে আধিপত্যের লড়াইয়ের প্রথম পর্বে মোহাম্মদ (সা) বিজয়ী হন। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার মানদণ্ডে একে যুদ্ধ বলা বেশ কঠিন। একে বরং খণ্ডযুদ্ধ বলাই ভালো। কিন্তু এর তাৎপর্য ছিলো ব্যাপক। এই প্রথমবারের মতো মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা আল্লাহর পথে কোনো যুদ্ধে শরীক হলেন। কোরাইশদের বিপক্ষে এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ে তাঁরা ছিলেন দারুণ উৎফুল্ল। সমগ্র আরব জুড়ে মোহাম্মদের (সা) ব্যাপক সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোরাইশদের জন্য এটি ছিলো অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। তাই বদর যুদ্ধের স্মৃতি ভুলে যাওয়া কিংবা মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো। এই অপমানের শোধ তোলার জন্য তারা ছিলো বদ্ধপরিকর। অধ্যাপক হিউ কেনেডি এ ব্যাপারে বলেন,
তাদের মনোভাবের সারকথা হলো, মদীনায় যাওয়ার কিছুদিনের মাঝেই মোহাম্মদ যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, অবশ্যই তা নষ্ট করতে হবে। এটাও ঠিক যে, মদীনায় তাঁর অনুসারীদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিলো দারুণ এক পুরস্কার। এই সম্পদ বণ্টন করে দেয়ায় তাঁদের কাছে মোহাম্মদের অবস্থান অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছিলো।
মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের কাছে বদর যুদ্ধে জয় লাভ করা ধর্মীয়ভাবে ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিলো ঈমানের সত্যতার প্রমাণ, যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি গত ১৪’শ বছর ধরে তাঁর অনুসারীদেরকেও এই বিজয় অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে। বনী ইসরাইলের মিশর ত্যাগ করে লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার ঘটনার মতো বদরের বিজয়কেও মুসলমানরা আজ অবধি সরাসরি আল্লাহর সাহায্য বলেই মনে করে।
কেবলা পরিবর্তন
বিজয়ের কিছুদিন পর মোহাম্মদ (সা) একদিন নামাজ আদায় করছিলেন। ঠিক তখন তিনি একটি ওহী লাভ করেন। এর মাধ্যমে তিনি ও তাঁর অনুসারীদের আরো সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র পরিচয় নির্ধারিত হয়। এতে মুসলমানদেরকে নামাজ আদায়ের দিক অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। এতদিন তিনি ও তাঁর সাহাবীরা ইহুদী-খ্রিস্টানদের মতোই মদীনা থেকে উত্তরে জেরুসালেমের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। ওহী নাজিলের সাথে সাথে তিনি জামায়াতে নামাজ আদায়কালেই দিক পরিবর্তন করে নতুন কেবলা মক্কার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীদের নিয়ে বাকি নামাজ আদায় করলেন। এ কারণে সেই মসজিদটিকে বলা হয় মসজিদে কেবলাতাইন অর্থাৎ দুই কেবলার মসজিদ।
এই পরিবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর তাৎপর্য বেশ গভীর। কারণ, এর মাধ্যমে একটি নতুন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়ের সূচনা ঘটে। সেটি হলো, মুসলমানদের ইবাদতের পদ্ধতি ইহুদী-খ্রিস্টানদের থেকে ভিন্ন। এছাড়া বর্তমানে এর তাৎপর্য হলো, মুসলমানরা দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেন, সবাই একই দিকে অর্থাৎ মক্কার দিকে ফিরে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। এটি ঐক্যের প্রতীক। এ প্রসঙ্গে বারনাবি রজারসন বলেন,
জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি বেশ দুবোর্ধ্য। ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন কিছু বিশ্লেষকের মতে, প্রথম দিকে ইসলামের অনেক উপাদান ইহুদী-খ্রিষ্টীয় ধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। যেমন– ইহুদী-খ্রিস্টানদের পবিত্র ভূমির প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ ইত্যাদি। তখন পবিত্র ভূমিকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্যা ছিলো, সেসব দূর করে একটি একক বিশ্বাসব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংস্কার আন্দোলন চলছিলো। এই আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে ইসলামের মতো নতুন একটি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে ঠিকই, তবে এটি পূর্ববর্তী ইহুদী-খ্রিস্টান ধারার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলো।
ইমেরিটাস অধ্যাপক জেরাল্ড হটিং বলেন,
ইসলাম স্বতন্ত্রভাবে নিজের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলতে চেয়েছিলো, এমনটি কেউ মনে করতেই পারে। ইসলাম যে নিজস্ব আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে মক্কাকে গড়ে তুলেছে, তাও তো সত্য। সুতরাং কেউ ভাবতেই পারে, ইসলামের পূর্বেকার ব্যবস্থাগুলো থেকে স্বতন্ত্র একটি বিশ্বাসব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে পৃথক রাখতে সচেতনভাবেই মক্কাকে কেবলা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।
ইহুদী-মুসলিম টানাপড়েন
তবে আরো বেশি করে মুসলিম পরিচয়ের দিকে ঝুঁকে পড়াকে মদীনার সবাই পছন্দ করেনি। বিশেষ করে কিছু ইহুদী গোত্র এর বিরোধী ছিলো। অধ্যাপক জিউফ্রে অল্ডারম্যান এ ব্যাপারে বলেন,
জেরুসালেমের পরিবর্তে অন্য কোনো দিকে ফিরে প্রার্থনা করা উচিত– এমন ধরনের চিন্তাভাবনার প্রেক্ষিতে তৎকালীন আরব উপদ্বীপের ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যে সন্দেহ জেগে ওঠা যে স্বাভাবিক ছিলো, তা আমি নিশ্চিতভাবেই অনুমান করতে পারি।
নামাজের নতুন কেবলা নির্ধারণের ব্যাপারটিকে ইহুদী গোত্রগুলো মোহাম্মদের (সা) সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ও তাদের অবাধ্যতার পরিণতি বলে ধারণা করলো। অধ্যাপক হিউ কেনেডি এ ব্যাপারে বলেন,
ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটি বেশ জটিল ছিলো। ইহুদী গোত্রগুলো মোহাম্মদকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে পারছিলো না। কারণ, এতে করে তাদের ধর্মগ্রন্থ, নিজস্ব ঐতিহ্য ইত্যাদির বিপক্ষে চলে যেতে হয়। ফলে তারা একটি মৌলিক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলো। অন্যদিকে বাণিজ্য ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ছিলো আরেকটি বড় ইস্যু। রুপার বাজার, মেটাল ওয়ার্ক ইত্যাদি সহ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তখন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা ছিলো। মক্কা থেকে সদ্য আগত মোহাম্মদের অনুসারীরা স্থানীয় অর্থনীতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলো।
ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে দিন দিন সম্পর্কের অবনতি ঘটার পাশাপাশি মোহাম্মদের (সা) সাফল্য ও ক্ষমতাও ক্রমে বাড়ছিলো। মক্কার সাথে বিরোধের বিষয়ে তিনি ইহুদীদের সমর্থন আশা করেছিলেন। কিন্তু তারা মক্কার কোরাইশদের সাথে লাভজনক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে রাজি ছিলো না। প্রচলিত মুসলিম বর্ণনা অনুযায়ী, ইহুদী গোত্রগুলো এক পর্যায়ে মোহাম্মদের (সা) শত্রুদের সাথে গোপন বৈঠক করতে থাকে। এছাড়া কিছু পৌত্তলিক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলেও মোহাম্মদের (সা) সাফল্যে তারা অসন্তুষ্ট ছিলো। ফলে তারাও তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেলো। মোহাম্মদ (সা) এবার ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকে সামগ্রিক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লেন।
বনু কাইনুকা অভিযান
বদর যুদ্ধের কিছুদিন পরই মদীনায় ইহুদীদের নিয়ে মোহাম্মদ (সা) প্রথমবারের মতো বড় ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়লেন। মক্কার কোরাইশদের সাথে ইহুদী গোত্রগুলোর একাধিক গোপন বৈঠকের তথ্য তিনি জানতে পারেন। তাঁর আশংকা ছিলো, কোরাইশরা আক্রমণ করে বসলে ইহুদী গোত্রগুলো হয়তো পুরোপুরিভাবে তাদের পক্ষে চলে যাবে এবং তাঁকে শেষ করার জন্য কোরাইশদেরকে সহায়তা করবে। তাই তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করলেন। একদিন তিনি মদীনার দক্ষিণে একটি ইহুদী গোত্রে (বনু কাইনুকা) গিয়ে তাদের দুর্গ অবরুদ্ধ করে রাখলেন। দুই সপ্তাহ ব্যাপী অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে। তারপর তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়। অধ্যাপক জন এসপোজিটো এই ঘটনা ব্যাখ্যা করে বলেন,
মদীনা সনদে বলা ছিলো, বিভিন্ন গোত্র এবং বিশ্বাসের লোকজন একসাথে মিলেমিশে মদীনায় বসবাস করতে পারবে। সে মোতাবেক ইহুদীদেরও নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মবিশ্বাস নিয়েই সমাজে বসবাসের অধিকার ছিলো। কিন্তু এর বিনিময়ে শর্ত ছিলো রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। কিন্তু তারা কী করেছিলো? তারা রাষ্ট্রের সাথে সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছিলো এবং মদীনার সমাজের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তুলেছিলো। ইহুদীদের সবাই এর সাথে নিশ্চয় ছিলো না। তাদের একটি গ্রুপ এর সাথে জড়িত ছিলো।
ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে মোহাম্মদের (সা) সম্পর্কের স্বরূপ কী ছিলো, তা বহুল আলোচিত একটি বিষয়। বেশিরভাগ মুসলিম স্কলার মনে করেন, মদীনার সংবিধান ছিলো উভয় পক্ষের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি। ফলে কিছু ইহুদী গোত্র মোহাম্মদের (সা) শত্রুদের সাথে হাত মেলানোর কারণে সেই চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন। এমনই একজন অধ্যাপক জিউফ্রে অল্ডারম্যান এ ব্যাপারে বলেন,
এটি এমন মতবিরোধপূর্ণ একটি বিষয়, যার সমাধান ঐতিহাসিকরা করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এ বিষয়ে স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য কোনো সমসাময়িক ইহুদী সূত্রের বর্ণনা আমাদের কাছে নেই। তাই তারা একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করেছিলো, এমনটি আপনি মনে করতে পারেন। আবার আপনি এমনটিও ভাবতে পারেন, ইহুদীদের সাথে তখন যে আচরণ করা হয়েছিলো, পরবর্তীতে তাকে ন্যায্যতা দেয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিম ঐতিহাসিকরা হয়তো মনগড়া চুক্তি সম্পাদনের কথা বলেছেন।
বারনাবি রজারসন এ ব্যাপারে বলেন,
এই ধনাঢ্য ইহুদী গোত্রগুলো প্রত্যেকটি ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলো। তাই তাদেরকে বহিষ্কার করাটা বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিলো। দেখুন, ইহুদীরা ছিলো মদীনায় প্রায় সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক। উর্বর উপত্যকাগুলোও ছিলো তাদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে, মহানবী একদম রিক্ত হস্তে, শরনার্থী হিসেবে মদীনায় এসেছিলেন। কিন্তু তারা নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করে শত্রুদের সাথে হাত মেলানোর মাধ্যমে মহানবীকে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়ার সুযোগ করে দিলো। এর মাধ্যমে তিনি মদীনার একচ্ছত্র নেতা হয়ে ওঠলেন।
তখন বিশ্বাসঘাতকতার প্রচলিত শাস্তি ছিলো মৃত্যুদণ্ড। তারপরও মোহাম্মদ (সা) তা বাস্তবায়ন না করে তাদেরকে শুধু মদীনা থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় তিনি তখনো অন্যদের সাথে এক ধরনের সমঝোতার প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু দুই পক্ষের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল রয়েই গিয়েছিলো।
উহুদ যুদ্ধ
আরেকটি ঘটনা মদীনার পরিস্থিতিকে তখন আরো উত্তপ্ত করে তোলে। বদর যুদ্ধের প্রায় এক বছর পর কোরাইশরা আগের প্রতিশোধ নিতে মদীনা আক্রমণ করতে আসে। এবার তাদের বাহিনী ছিলো মোহাম্মদের (সা) বাহিনীর প্রায় তিন গুণ বড়। এটি কোনো মামুলী গোত্রীয় বিবাদ ছিলো না। এটি ছিলো মুসলমানদেরকে চিরতরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ।
মোহাম্মদ (সা) আবারো তাদেরকে মদীনার বাইরে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্থানটি ছিলো উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। কিন্তু তাঁর সেনাসংখ্যা ছিলো খুবই কম। এর একটা কারণ ছিলো, ইহুদী গোত্রগুলো তাদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাতের অজুহাতে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। এছাড়া মোহাম্মদের (সা) একজন সেনাপতি (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই) প্রায় তিনশ সৈন্য নিয়ে তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে ময়দান ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে, মক্কাবাসীরা ছিলো প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত। এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই প্রতিপক্ষের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগেই যুদ্ধটি শেষ হয়ে যায়। অধ্যাপক হিউ কেনেডি এ ব্যাপারে বলেন,
যুদ্ধে দুই পক্ষই কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। যুদ্ধের ফলাফল ড্র ছিলো বলা যায়। তবে মদীনার মুসলিম সমাজ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলো। এটাই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।
বদর যুদ্ধের সাথে উহুদ যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, মক্কাবাসী এবার মদীনার অভ্যন্তরীণ সহায়তা পেয়েছিলো। প্রচলিত মুসলিম বর্ণনা মতে, মদীনার কয়েকটি ইহুদী গোত্র সক্রিয়ভাবে মোহাম্মদের (সা) শত্রুদেরকে সহায়তা করেছিলো।
খন্দকের যুদ্ধ
কোরাইশদের সাথে তৃতীয় এবং সর্বশেষ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে মদীনায় মোহাম্মদের (সা) আগমনের পাঁচ বছর পার হয়েছে। কোরাইশরা এবার ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে এসেছে। বিপরীতে মোহাম্মদ (সা) মাত্র তিন হাজার সেনা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে কোরাইশদের বিপরীতে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই তিনি কোরাইশদের মোকাবেলায় নতুন কৌশল গ্রহণ করলেন। মদীনার প্রতিরক্ষা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিলো। কারণ, শহরটি ছিলো পাথুরে পাহাড় বেষ্টিত। তবে উত্তর দিকটি উন্মুক্ত থাকায় মদীনা ছিলো অরক্ষিত। এই দিকটি সুরক্ষিত করতে মোহাম্মদ (সা) খুব সহজ একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি পুরো উত্তর দিক জুড়ে গভীর পরিখা খুঁড়লেন। কোরাইশদের এগিয়ে আসতে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে এই পরিখাই মূল ভূমিকা পালন করেছিলো। এই যুদ্ধকে তাই পরিখার যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।
খন্দকের যুদ্ধ যেখানে সংঘটিত হয়েছিলো, সেই অঞ্চলটি বর্তমানে আধুনিক মদীনা নগরীর অংশ। তখন যুদ্ধে দুই বাহিনীর মাঝখানে ছিলো পরিখা। মক্কার বাহিনী ছিলো বিশাল। দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত তাদের বাহিনী দেখা যেতো। পরিখার ফলে তারা অবধারিতভাবেই কঠিন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলো। তারা কার্যত কোনো কিছুই করতে পারছিলো না। মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর বাহিনী যে খন্দক তৈরি করে রেখেছেন, তা অতিক্রম করার কোনো প্রস্তুতি তাদের ছিলো না। অন্যদিকে, মোহাম্মদ (সা) ধীরেসুস্থে সময় কাটাচ্ছিলেন। মক্কার লোকেরা হতাশ হয়ে কখন এলাকা ত্যাগ করে, সেই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। অধ্যাপক হিউ কেনেডি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন,
পরিখার কারণে কোরাইশ বাহিনীর ঘোড়াগুলো শহরে প্রবেশ করতে পারছিলো না। খন্দকের এই ঘটনা মুসলমানদের কাছে মোহাম্মদের বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও কমান্ডিংয়ের নিদর্শন হিসেবে শত শত বছর ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই ব্যতিক্রমী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফলে মক্কার বাহিনী একদম অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এতে তাদের রণকৌশল অকার্যকর হয়ে পড়েছিলো।
বনু কোরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা
মুসলিম বর্ণনা মতে, দুই সপ্তাহ পর মক্কার সেনাবাহিনীর রসদ ফুরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে তারা তাদের এক গোপন মিত্রকে মদীনার ভেতর থেকে মুসলম বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে অনুরোধ করে। বলাবাহুল্য, মিত্রটি ছিলো ইহুদী গোত্র বনু কোরাইযা।
এতদিন পর্যন্ত ইহুদী গোত্রগুলো মোহাম্মদের (সা) শত্রুদের সাথে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করে এসেছিলো। অথবা, বড়জোর মোহাম্মদের (সা) পক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু এবার তারা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। এ ব্যাপারে রবার্ট স্পেনসার বলেন,
বনু কোরাইযা মোহাম্মদ ও মুসলমানাদের সাথে মদীনার ভেতরেই ছিলো। মোহাম্মদের সাথে তারা একটি চুক্তিতেও আবদ্ধ ছিলো। কিন্তু তারা মদীনার অপর দুই ইহুদী গোত্র বনু নাজীর ও বনু কাইনুকার সাথে কৃত আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণেই তারা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কোরাইশদেরকে তাদের সাথে চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমার ধারণা।
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদেল হালিম এ ব্যাপারে বলেন,
তারা ছিলো সেই লোক, যারা চুক্তিবদ্ধ মৈত্রী হওয়ার পরও মুসলিম সমাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য মদীনার সবচেয়ে বড় শত্রুর পক্ষে চলে গিয়েছিলো। এটি বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। অবস্থা কতটা সঙ্গীন ছিলো কোরআনের আয়াত থেকে তা বুঝা যায়। কোরআন আমাদেরকে বলেছে, সে সময় মুসলমানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিলো। তারা ভেবেছিলো, আজই বুঝি শেষ দিন।
মুসলিম পণ্ডিতদের মতে, কোরাইশদের সাথে সমঝোতা করে বনু কোরাইযা নিশ্চিতভাবেই মোহাম্মদের (সা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। তারা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিলো। এমনকি কোরাইশ ও তাদের মিত্রবাহিনী আক্রমণ থেকে সরে আসার আগেই ইহুদীদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিলো। জেরুসালেমে অবস্থিত হিব্রু ইউনিভার্সিটির ইসলামিক অ্যান্ড মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজের অধ্যাপক এলা ল্যানডাউ-টাসেরন এ ব্যাপারে বলেন,
এটা তো প্রচলিত ব্যাখ্যা। বরং মোহাম্মদই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন। ইহুদীরা নবীকে আক্রমণ করেছিলো, কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো ঘটনার কোনো প্রমাণ নেই। ওই অবরোধের সময় বনু কোরাইযা নবীকে অস্ত্র ধার দিয়েছিলো। অন্যদিকে, তারা সম্ভবত অবরোধকারীদের সাথে ব্যবসাও করতো। কারণ, তারা তো আসলে ব্যবসায়ী ছিলো।
অধ্যাপক জিউফ্রে অল্ডারম্যান এ ব্যাপারে বলেন,
বনু কোরাইযা সম্ভবত কোরাইশদের পক্ষ নিয়েছিলো। তবে আমার মতে, তারা যা করেছিলো সেটি করাই তাদের জন্য স্বাভাবিক ছিলো। ইহুদীরা সবসময় মিত্র খোঁজার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। ইহুদীদের রাজনৈতিক তত্ত্বের মূলকথা হলো, নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইহুদীরা সবার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে এবং যে কাউকে বন্ধু বানাতে পারে। আমি মনে করি, তখন তারা যা করেছিলো, সেটি ছিলো তাদের জন্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।
এই ষড়যন্ত্র সফল হলে কোরাইশরা মদীনায় ঢুকে পড়তে সক্ষম হতো। সেক্ষেত্রে তারা মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের সবাইকে হয়তো হত্যা করতো এবং তাঁর প্রবর্তিত নতুন ধর্মটির সেখানেই অবসান ঘটতে পারতো।
বনু কোরাইযা অভিযান
ইহুদীদের সর্বশেষ এই প্রতারণার বিরুদ্ধে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেটি তাঁর জীবনের অন্যতম বিতর্কিত একটি ঘটনা। মোহাম্মদ (সা) তাঁর বাহিনীকে ইহুদী গোত্রটির এলাকা ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর তারা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এবার তিনি দোটানায় পড়ে গেলেন। ইহুদীদেরকে মুক্ত করে দেয়া হলে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার লক্ষ্যে তারা মক্কার কোরাইশদের সাথে পুনরায় যোগ দেয়ার আশংকা প্রবল। এমতাবস্থায় তিনি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার পরিবর্তে একজন স্বতন্ত্র মধ্যস্ততাকারী নিয়োগের ব্যাপারে রাজি হন। তিনি ইহুদী গোত্র সর্দারদেরকে নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজনকে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে অধ্যাপক তারিক রমাদান বলেন,
তাদের সাথে আলোচনায় তিনি তিনবার জানতে চেয়েছিলেন, ‘তোমাদের বিচার করার জন্য আমি তৃতীয় কাউকে নিয়োগ করতে চাই। তোমরা কি এতে রাজি?’ তারপর তিনি সাদ ইবনে মুয়াজকে (সা) আসতে বললেন এবং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। তিনি পুরুষদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিলেন। মনে রাখা দরকার, এই সিদ্ধান্তের আগে মহানবী (সা) বলেছিলেন, “আমি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দেবো না, বরং সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য তৃতীয় কাউকে অনুরোধ করবো।” ফয়সালা অনুসারে পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু একই ধরনের অপরাধের জন্য এর আগে তিনি আরো দুইবার তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। সর্বশেষ বার এসে তিনি বলেছিলেন, “যথেষ্ট হয়েছে। তোমরা বার বার একই কাজ করছো। একই অপরাধে অতীতে তোমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দেয়ার পরও আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসাটা পরিস্কার বিশ্বাসঘাতকতা।”
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদেল হালিম এ ব্যাপারে বলেন,
বনু কোরাইযার যোদ্ধাদেরকে মৃত্যুদণ্ড এবং নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধবন্দী করার রায় দিয়েছিলেন তিনি। এই রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো।
‘নাউ দে কল মি ইনফিডাল’ গ্রন্থের লেখিকা ননী দারভীশ বলেন,
এটি ছিলো ইহুদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম গণহত্যা। ইহুদীরা তাকে হত্যা করতে চাওয়া সত্ত্বেও একজন নবী কীভাবে আট শতাধিক মানুষকে মেরে ফেলার আদেশ দিতে পারেন? এর পরিবর্তে তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করতে কিংবা নির্বাসন দিতে পারতেন।
ইসলাম ইহুদীবিদ্বেষ বিরোধী
আব্দুর রহীম গ্রীন বলেন,
এই ঘটনার সাথে তাদের ইহুদী হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা খ্রিস্টান বা অন্য কোনো গোত্রও হতে পারতো। এটি কোনো হলোকাস্ট ছিলো না। ধর্মের কারণে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হয়েছে, ব্যাপারটি তেমনও নয়। যদি তাই হতো, তাহলে ইহুদীদেরকে হত্যা করার নজির হিসেবে এটি মুসলিম ইতিহাসে থেকে যেতো এবং সেক্ষেত্রে ইহুদী এনলাইটেনমেন্টের সোনালি যুগের বিকাশ মুসলিম শাসনামলের স্পেনে ঘটতো না। এই দাবি সত্য হলে ইসলামের ইতিহাসে ইহুদীদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হতো।
অন্য যে কোনো ঘটনার চেয়ে বনু কোরাইযর ঘটনাটি সম্ভবত অনেক বেশি সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনা সামনে এনে মোহাম্মদকে (সা) এমন একজন নিষ্ঠুর ও নিপীড়ক শাসক হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যিনি নিজের শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য যে কোনো প্রকার সহিংস উপায় অবলম্বন করতেন। বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব জুড়ে ইহুদীদের প্রতি যে ধরনের তীব্র বৈরিতা বিদ্যমান, এই ঘটনাকে তার পেছনের কারণ হিসেবে সমালোচকরা মনে করে থাকে। হ্যাঁ, আমাদের বর্তমান মানদণ্ডের আলোকে এটি নিশ্চয় নিষ্ঠুর একটি ঘটনা ছিলো। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই তৎকালীন সময় ও প্রেক্ষাপটের আলোকে ঘটনাটিকে দেখতে হবে। বাস্তবতা হলো এই ঘটনায় তখন তেমন কেউই মর্মাহত হয়নি। এই না হওয়াটাও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা বৈকি! মোহাম্মদ (সা) এমনই এক সমাজ ও যুগে বেড়ে ওঠেছিলেন। অধ্যাপক জিউফ্রে অল্ডারম্যান এ ব্যাপারে বলেন,
আমি মনে করি, ইহুদীদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ থেকেই হত্যাযজ্ঞটি সংঘটিত হয়েছিলো। আমার মতে, একদিক থেকে দেখলে মুসলিম বিশ্ব শত শত বছর ধরে ইহুদীদের প্রতি বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছে। বর্তমানে ইহুদীদের প্রতি মুসলমানদের যে মনোভাব, তার পেছনে অবশ্য অনেক ধরনের কারণ রয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, এই ঘটনাটিও তেমনই একটি কারণ। এই ঘটনাটি বিষাক্ত ক্ষত হিসেবে মুসলিম মননে গেঁথে গেছে। এটি বাড়তে বাড়তে বর্তমানে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
মুসলিম বিশ্ব এবং পাশ্চাত্যের মুসলিম সমাজের কোথাও কোথাও নতুন এক ধরনের ইহুদীবিদ্বেষ দেখা যাচ্ছে। কোরআন থেকেই এর বৈধতা পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দেয়া বাগাড়ম্বরসর্বস্ব এ জাতীয় বক্তৃতামালা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষের কাছেই ভীষণ আপত্তিকর বলে মনে হবে। যেমন একটি টিভি চ্যানেলে একজন বয়োবৃদ্ধ মুসলিম নেতা বলছিলেন–
হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! তোমার তীব্র ক্রোধ এদের উপর প্রয়োগ করো। এদেরকে শাস্তি এবং নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করাও।
অধ্যাপক তারিক রমাদান এ সম্পর্কে বলেন,
কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় নিছক ইহুদী হওয়ার কারণেই কিছু মানুষ তাদের বিরোধিতা করে থাকে। কিন্তু এটি ইসলামী ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এটি অগ্রহণযোগ্য, বর্ণবাদী, ইহুদীবিদ্বেষী অবস্থান। এটি আমাদের ধর্মেরও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। একেশ্বরবাদী ধারার অনুসারী ইহুদীদেরকে ‘আহলে কিতাব’ হিসেবে বিবেচনা করার পর তাদের উদ্দেশ্যে আমরা এ ধরনের বর্ণবাদী বক্তব্য দিতে পারি না। অথচ মহানবী (সা) মদীনায় পদার্পণ করে একটি ইসলামী সমাজের সূচনার পাশাপাশি যখন মদীনার শাসনভারও গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি ‘আল-উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ’ তথা ইসলামী সমাজ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘তারা আমাদের উম্মাহর সদস্য।’ তারা কারা? ইহুদী ও খ্রিস্টানরা। এখন দেখুন, স্বয়ং মহানবী (সা) কী বলেছিলেন, আর আমরা কী বলছি! আমাদের এ ধরনের ইহুদীবিদ্বেষী মনোভাব ইসলামের দিক থেকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। ইহুদীদের ব্যাপারে কোনো রাষ্ট্র বা সরকার (যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের কথাই ধরা যাক) কী করবে, তা আমাদের আওতাধীন বিষয় নয়। তবে মানবতা ও বিশ্বাসের দিক থেকে ইহুদীরা আমাদের ভাইবোন।
মদীনার ইহুদী গোত্রগুলোর প্রতি মোহাম্মদ (সা) যে আচরণ করেছিলেন, এর ধারাবাহিকতা আমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। কিন্তু সে সময়ে এ ঘটনার পরিণতিতে তিনি আরবের একটি শক্তিশালী নতুন আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মোহাম্মদ (সা) কেমন ছিলেন, তা জানার জন্য এই ঘটনাই একমাত্র উদাহরণ নয়।
যা হোক, মহানবীর (সা) বয়স ততদিনে পঞ্চাশের কোটার শেষ দিকে। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এসেছেন। নিজ শহর থেকে তাঁকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। তারপর বলতে গেলে নিয়মিতভাবে তাঁকে রক্তাক্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। আরো বেশি করে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে শেষ হয়ে যাবেন, নাকি অনুসারীদের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন– এই প্রসঙ্গে, বিশেষ করে মক্কার সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের সমাধা করার জন্য তাঁকে একটি পথ খুঁজে বের করতে হয়েছিলো। এ বিষয়ে আলোচনার মূলকথা হলো, মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আপনি কী মনে করবেন? তিনি কি নিছক একজন আরববিজয়ী যোদ্ধা ও নেতা ছিলেন? নাকি তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য চিরন্তন ঐশীবাণী বাহক একজন নবী?
শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখাবো, মোহাম্মদ (সা) কীভাবে বার বার তাঁর শত্রুদের শান্তিপূর্ণভাবে মোকাবেলা করেছেন এবং জয়লাভ করেছেন। মক্কায় প্রদত্ত সর্বশেষ ভাষণে তিনি কী রূপরেখা দিয়ে গেছেন, তাও আমরা তুলে ধরবো।
তৃতীয় পর্ব: হলি পিস
ওহী লাভের শারীরিক কষ্ট
মোহাম্মদ (সা) সময়ে সময়ে যেসব ঐশীবাণী লাভ করেছিলেন, সেগুলোর সংকলনই হলো ‘আল কোরআন’। ওহী নাজিলের প্রতিটি ঘটনাই তাঁর জন্য ছিলো কষ্টকর ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা। এই জন্য তাঁকে প্রতিনিয়ত কঠোর সাধনা করতে হতো। কখনো ওহী নাজিল হতো সরাসরি কথা হিসেবে, আবার কখনো স্বপ্নযোগে। সেক্ষেত্রে ওহীর অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য রাসূলকে (সা) গভীর মনোযোগ সন্নিবেশ করতে হতো। এ প্রসঙ্গে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
তিনি প্রায় সময় বলতেন, ‘আমার উপর যখন ওহী নাজিল হয়, তখন মনে হয় যেন দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।’ ওহী নাজিলের পর তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেতো। তিনি তখন ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন। এমনকি শীতের দিনেও এর ব্যতিক্রম হতো না। আল্লাহর বাণী গ্রহণ করার জন্যই তাঁর এতো কষ্ট হতো।
বারনাবি রজারসন বলেন,
প্রচণ্ড কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মহানবী ওহী লাভ করতেন। তাঁর গোটা সত্তা জুড়ে প্রবাহিত এই বিশেষ অভিজ্ঞতাকে তিনি ভাষায় প্রকাশ করেছেন।
টম হল্যান্ড বলেন,
মোহাম্মদ এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন মনে করা হতো, ঐশ্বরিক রহস্যময় ব্যাপারগুলোর পর্দা উন্মোচন করা বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল সম্ভব। ইহুদী, খ্রিস্টান, জরাথ্রুস্ট– এই ধর্মগুলোতেও এ ধরনের পবিত্র ব্যক্তির ধারণা রয়েছে। এ কারণেই ঈশ্বরের কাছ থেকে মোহাম্মদের ঐশীবাণী লাভের দাবির প্রতি মানুষ তখন আস্থা রেখেছিলো।
আধ্যাত্মিকতার ইসলামী স্বরূপ
তবে বাস্তবতা হলো, এই ধরনের আধ্যাত্মিকতার ধারণা ইসলামের সাথে যায় না। যদিও মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের একটি গ্রুপ তথা সুফী ধারার প্রচলন রয়েছে। তাদের দাবি হলো– আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে অভিজ্ঞতা মোহাম্মদ (সা) লাভ করেছিলেন, তারাও গভীর ধ্যান, জিকির ও কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সে ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করছে। তুর্কি সুফীদের বিশেষ ধরনের ঘূর্ণি নৃত্যের একজন নৃত্যকার এমরি ইলদিরিম বলেন,
নবী মোহাম্মদ (সা) প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেন, তাঁর সাথে যোগাযোগ করতেন। তিনি সাধারণত তখনই ঐশী নির্দেশনাগুলো লাভ করতেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতেন। ঠিক এ কারণেই আমরাও আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি। এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সাথে বিলীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। নবী মোহাম্মদ (সা) নিজেই এর দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন কিংবা প্রার্থনার মাধ্যমে যা কিছু করেছেন, আমাদের জন্য সেগুলোই অনুসরণীয়।
এভাবে সুফীরা অনেক ধরনের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে গড়ে নিয়েছে। অথচ সুফীরা যাকে তাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করে, সেই মোহাম্মদ (সা) এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান কখনো করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক সাজ্জাদ রিজভী এ ব্যাপারে বলেন,
একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে মহানবী (সা) ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক ও সুফী উভয় ধারারই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর মাধ্যমেই কেবল কেউ আল্লাহকে জানতে পারে– এই সত্যের মাঝেই আসলে তাঁর পরিপূর্ণতা নিহিত রয়েছে।
সুফিদের এসব আচার-অনুষ্ঠানে জিকির করতে করতে একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় বলে মনে করা হয়। সুর করে জিকির করার সময় এক ধরনের মোহাবিষ্টতা তৈরি করতে তুর্কি সুফীরা নৃত্যেরও প্রবর্তন করেছে। জিয়াউদ্দীন সরদার এ ব্যাপারে বলেন,
প্রত্যেকটি ধর্মেই আধ্যাত্মিকতার নানা রকম নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদেরও বেশ কয়েক ধরনের আধ্যাত্মিক ধারা রয়েছে। সুফীবাদ এরমধ্যে একটি। হ্যাঁ, মহানবী (সা) প্রার্থনা করেছেন, ধ্যান করেছেন; কিন্তু তিনি তো এটিও বলেছেন– ‘দোয়া করো, তবে তোমার উটটি বেঁধেও রেখো।’ এর মানে হলো শুধু দোয়া-দরুদই যথেষ্ট নয়, ভালো কাজটাও করতে হবে। দোয়া করার সাথে সাথে আমাদেরকে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজও গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের আধ্যাত্মিকতা কেউ যদি মেনে চলে এবং বাস্তব জীবনে ভালো কাজ করে ও ভালো কাজ করার উপর জোর দেয়াকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তাহলেই সত্যিকার অর্থে মোহাম্মদের (সা) পথ অনুসরণ করা হয়।
মোহাম্মদের (সা) আধ্যাত্মিকতা ছিলো জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তিনি সন্ন্যাসী টাইপের কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। বরং আরব সমাজের সংস্কারের জন্য তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন। পরকালে বেহেশত লাভের অপেক্ষায় নিছক বসে থাকার পরিবর্তে তিনি একটি আদর্শ সমাজ গড়ার চেষ্টা করে গেছেন।
মহানবীর ব্যক্তিচরিত্র
৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই মদীনার একজন ক্ষমতাধর শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হলেও ব্যক্তিগত আচরণ ও জীবনযাপনে তিনি আগের মতোই পরিমিত ছিলেন। প্রাপ্ত সকল বর্ণনাই এ কথা সমর্থন করে। আগের মতোই তিনি তাঁর ছোট্ট মসজিদটির পাশের ঘরটিতে থাকতেন এবং মসজিদটিকে নামাজের স্থান ও তাঁর কাজকর্মের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। ইহুদী, খ্রিস্টান, কাফের, এমনকি দাসদাসীসহ সকলেরই তাঁর কাছে যাওয়া এবং কথা বলার অবাধ সুযোগ ছিলো। মহানবীর (সা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন সরদার বলেন,
তাঁর জীবনী পড়লে স্পষ্টতই বুঝা যায়, তিনি একজন অসাধারণ ক্যারেশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অসংখ্য লোক পরামর্শ নিতে তাঁর কাছে প্রতিনিয়ত আসতো। তিনি যে সব সময় একেবারে সর্বোত্তম পরামর্শটিই তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারতেন, তা কিন্তু নয়। তবে সবসময়ই তিনি লোকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবিক, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি।
ড. আমিরা বেনিসন বলেন,
আমি মনে করি, নানান দিক থেকেই মোহাম্মদ (সা) চমৎকার মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র। কারো দোষত্রুটি খুঁজতে যেতেন না। অত্যন্ত স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।
তিনি একদম সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন। স্বর্ণ, রেশমি পোশাক, কিংবা বিলাসবহুল কোনো দ্রব্য অপছন্দ করতেন। বিত্তবৈভবের ধার ধারতেন না। সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে দান-খয়রাত করতেন, উপহার দিতেন। ‘দ্য লিডারশিপ অব মোহাম্মদ’ গ্রন্থের লেখক জন আডায়ার মহানবী (সা) সম্পর্কে বলেন,
ক্ষমতার পেছনে ছুটে বেড়ানোর কোনো লক্ষণ আমি মোহাম্মদের মাঝে খুঁজে পাইনি। তাঁর সততার উপর কখনো কোনো কালি পড়েনি। যে কোনো আর্থিক বিষয় বা দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। একটি উদীয়মান সংগঠনের নেতার যেসব যোগ্যতা ও মোরাল ভিশন থাকা দরকার, আমার মতে, মোহাম্মদের ঠিক তাই ছিলো। এই দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।
বারনাবি রজারসন বলেন,
তিনি ছিলেন একজন অনুসন্ধায়ী। জীবনভর তিনি সত্য ও সঠিক উপলব্ধির সন্ধান করেছেন। তাঁর বাগ্মিতা ছিলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান আরব। তাঁর কর্ম মানবজাতির জন্য এমনই দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, যা কালক্রমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।
মক্কী ও মাদানী যুগের পার্থক্য
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মোহাম্মদ (সা) ধারাবাহিকভাবে ওহী লাভ করলেও মক্কী ও মাদানী যুগের ওহীর বিষয়বস্তুর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। মক্কী জীবনের ওহীগুলোতে ঈমান ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, মাদানী জীবনের ওহীগুলো ছিলো সে তুলনায় অনেক বেশি প্রায়োগিক, অর্থাৎ বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক বিষয়গুলো থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যাপার পর্যন্ত একজন মুসলমানের জীবনযাপন কেমন হওয়া উচিত, এই ওহীগুলোতে সেসব বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অনেক মুসলমান এসব নির্দেশনা মেনে চলার চেষ্টা করেন। ড. আমিরা বেনিসন এ ব্যাপারে বলেন,
মক্কায় তিনি মূলত একজন ধর্মীয় প্রচারক ছিলেন, এ কথা ঠিকই আছে। শেষবিচারের দিন, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার– এ জাতীয় বিষয়গুলো নিয়েই তিনি বেশি বলতেন। তবে মদীনায় হিজরতের পর তিনি সমাজের নেতা হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠলেন। তারপর দিন দিন সমাজ পরিচালনার সাথে তিনি অনেক বেশি জড়িয়ে পড়লেন। লোকেরা কীভাবে একে অপরের কাজে এগিয়ে আসবে, উত্তরাধিকার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কীভাবে করবে, এমনকি একে অপরকে কীভাবে সম্ভাষণ জানাবে, সেসব বিষয়ে পর্যন্ত তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।
কখনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে ওহী নাজিল হয়েছে। যেমন– অসুস্থ ও অভাবীদেরকে আর্থিক সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আবার ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে অন্য বিশ্বাসের লোকদের সাথে কী রকম আচরণ করতে হবে, এ সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা হিসেবেও কখনো কখনো ওহী নাজিল হয়েছে। মদীনার শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মোহাম্মদ (সা) এসবকে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে পরিণত করেছিলেন।
‘শরীয়াহ’ বলতে আসলে কী বুঝায়?
সময়ে সময়ে মোহাম্মদের (সা) উপর নাজিলকৃত ওহীগুলো সার্বজনীন সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা সংক্রান্ত একটি নৈতিক নীতিমালা তথা জীবনবিধানের রূপ লাভ করে। কোরআনে একে বলা হয়েছে ‘শরীয়াহ’ তথা ‘আল্লাহকে জানার পথ’। অধ্যাপক তারিক রমাদান এ সম্পর্কে বলেন,
শরীয়াহ সম্পর্কে আমরা তিনটি আয়াত পাই। এই আয়াতগুলোতে শরীয়াহ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ শরীয়াহ বলতে কী বুঝেছিলেন? তারা কী প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন? এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তারা আসলে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন– এই পথই হলো স্রষ্টার পথ তথা শরীয়াহ। তবে পরিভাষাটি নিয়ে আমরা সমস্যায় পড়েছি আরো পরে। কারণ, পরবর্তী স্কলারগণ শরীয়াহকে আল্লাহর আইন বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেহেতু তাঁরা মূলত ফিকাহবিদ ছিলেন, তাই তাঁদের কাছে শরীয়াহ নিছক একটি আইনী ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত ছিলো। কিন্তু মহানবী (সা) সমাজে প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়গুলোর প্রচলন ঘটিয়েছিলেন? আপনি জানেন, সেগুলো ছিলো ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। এগুলোই হলো শরীয়াহ।
ইসলামের পবিত্র বিধান তথা শরীয়াহ আইন হিসেবে যা এখন পরিচিত, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। এর প্রচলন ঘটেছে মহানবীর (সা) মৃত্যুর দুই শতাব্দী পর। ক্রমবিকাশমান ইসলামী খেলাফত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করতে তৎকালীন ফিকাহবিদগণ একটি আইনী কাঠামোর উদ্ভাবন করেন, যা আজকে শরীয়াহ আইন হিসেবে পরিচিত। তাঁরা কোরআনের শিক্ষা ও মহানবীর (সা) জীবনের দৃষ্টান্তগুলোর মাঝে সমন্বয় করেন। শরীয়াহর এই কাঠামোকেই অনেক মুসলমান এখন অপরিবর্তনীয় আল্লাহর আইন বলে মনে করেন। ড. আমিরা বেনিসন এ ব্যাপারে বলেন,
ইসলামী আইনের মূলনীতিগুলো কোরআনে বলা আছে। এমনকি সুনির্দিষ্ট কিছু বিধানের বিস্তারিত বর্ণনাও আপনি কোরআনে পাবেন। যেমন– উত্তরাধিকার আইন। কিন্তু ‘শরীয়াহ আইন’ সময়ের ব্যবধানে মানুষের হাতেই গড়ে ওঠেছে। এটি ছিলো আল্লাহর ইচ্ছাকে বুঝা ও তা বাস্তবায়ন করার একটি মানবীয় প্রচেষ্টা। শরীয়াহ ডিসকোর্সের ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সাংঘর্ষিক বিধান পর্যন্ত রয়েছে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো বিধান নয়। এটি অনেক বেশি নমনীয়, পরিবর্তনশীল এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার উপযোগী একটি ব্যবস্থা।
শরীয়াহ আইন নিয়ে বিতর্ক
মদীনায় মোহাম্মদ (সা) বহু অতীত গোত্রীয় রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। বংশ পরম্পরায় চলে আসা নৃশংস গোত্রীয় সংঘাতের বিলোপসাধন করেছিলেন। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীদের অংশিদারিত্ব এবং নারীদের স্বীয় সম্পত্তির উপর অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তবে কোরআনে কিছু সেকেলে শাস্তি আইনের কথাও বলা আছে। যেমন– চুরির শাস্তি হিসেবে অঙ্গ কেটে নেয়ার বিধান। অবশ্য মোহাম্মদ (সা) কখনো এই শাস্তির প্রয়োগ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।[3] এ জাতীয় কিছু শাস্তি এখন পর্যন্ত শরীয়াহ আইন কাঠামোর অংশ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। নিউইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটির ফিলোসফির টিচিং ফেলো ড. ডেভিড উড এ ব্যাপারে বলেন,
সপ্তম শতাব্দীর আরবে (কখনো কখনো) কন্যাশিশুকে মেরে ফেলার প্রচলন ছিলো। কেউ যদি নিজের কন্যাসন্তানকে বিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৪/১৫ বছর পর্যন্ত লালনপালনের ভার নিতে না চাইতো, তাহলে মেয়েটিকে মরুভূমিতে ফেলে আসতো। এক পর্যায়ে মেয়েটি মারা যেতো। মোহাম্মদ এই ব্যবস্থার অবসান ঘটান। এতিম ও বিধবাদেরকে সহায়তা করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এগুলোকে নিশ্চয় মহৎ শিক্ষা হিসেবে আমরা বিবেচেনা করতে পারি। কিন্তু এমন কিছু শিক্ষাও আমরা দেখতে পাই, যা বর্তমানের তুলনায় রীতিমতো বর্বর। ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা, চোরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়া– আমার বিবেচনায় এসব বিধান নিশ্চিতভাবেই পশ্চাৎপদতার নামান্তর।
তবে অধ্যাপক তারিক রমাদান বলেন,
আজকের দিনে আমরা পশ্চিমা বিশ্ব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে শরীয়াহর অত্যন্ত সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করছি। বিয়ে, শাস্তি আইন ইত্যাদি বিষয়কে সমর্থন বা বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে শরীয়াহর রক্ষণশীল ব্যাখ্যাকেই আমরা মুখ্য বিবেচনা করছি। এটি ঠিক নয়। শরীয়াহ নিয়ে আমার বক্তব্য হলো– আমি পাশ্চাত্যে বসবাস করি। এখানে আমার-আপনার-সবার জন্যই আইন রয়েছে। আমরা সবাই সমান অধিকার ভোগ করি। এটাই হলো আমার শরীয়াহ। এটি হলো শরীয়াহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।
সৌদি আরব ও ইরানের মতো কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের আইনী কাঠামোর মূলভিত্তি হলো শরীয়াহ আইন। সেসব দেশের শাস্তির বিধানগুলোকে অনেকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে মনে করে। ফলে ব্রিটেন ও ইউরোপে শরীয়াহ আইন চালুর যে দাবি মুসলিম চরমপন্থীরা করে থাকে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণা জোরদার হচ্ছে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এটি হলো ইসলামী প্রভাব ছড়িয়ে দেয়ার একটি প্রচেষ্টা। ‘নাউ দে কল মি ইনফিডাল’ গ্রন্থের লেখিকা ননী দারভীশ এ ব্যাপারে বলেন,
একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা এমন এক জাতি দেখছি, যারা মানুষের শিরচ্ছেদ করছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিচ্ছে, হাত-পা কেটে ফেলছে। এটি একটি বড় সমস্যা। এই যুগেও স্বয়ং সরকার পাথর মেরে নারীদের হত্যা করছে। অথচ এসব নারীরা কাউকে খুন করেনি। নিছক ‘যৌন অপরাধের’ অভিযোগে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একজন ব্যক্তির জীবন হরণ করার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হলো মৃত্যুদণ্ড প্রদানের এই অমানবিক প্রক্রিয়াটি।
অধ্যাপক তারিক রমাদান এ সম্পর্কে বলেন,
কেউ কেউ পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা, কিংবা শাস্তি প্রয়োগ শুরু করাকেই শরীয়াহর বাস্তবায়ন বলে মনে করে। আমি বলি– না, এটি শরীয়াহ নয়। এটি হলো নিজের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করার কৌশল। তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেটি হলো, আপনি কোন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন? নাকি আদৌ নির্বাচিতই হননি? আপনি কি সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন? এটি হলো প্রথম প্রশ্ন। যেহেতু আপনার কোনো বৈধতা নেই, সেহেতু ইসলামের নামে এই ধরনের শাস্তি প্রয়োগের কোনো অধিকার আপনার নেই। এই শাস্তি যারা প্রয়োগ করছে বা চালু করেছে, তাদের অধিকাংশই আসলে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ নয়। জনগণ তাদেরকে নির্বাচিত করেনি। নিজেদের গদি ঠিক রাখার স্বার্থেই তারা এগুলো করে থাকে। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করা যাক। শাস্তি প্রয়োগের পূর্বশর্ত হিসেবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমানাধিকার বাস্তবায়ন করবে কে? ইসলামের মর্মবাণী জনগণকে বুঝাবে কে? আপনি কি মানুষকে ইসলামে উদ্বুদ্ধ না করেই শাস্তি প্রয়োগ করতে চান? এটি কি ইসলাম? মোটেও না। ইসলাম শুরুই হয় মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে। শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি ব্যাপার। শাস্তি প্রয়োগ দিয়ে শুরু করা যাবে না। মানুষের আত্মমর্যাদা ও অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা ধর্মকে নিছক নিজেদের শাসনতান্ত্রিক বৈধতার স্বার্থে ব্যবহার করে।
এ ব্যাপারে জিয়াউদ্দীন সরদার বলেন,
অন্যান্য সকল আইনের মতো শরীয়াহ আইনও সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হওয়ার কথা। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হওয়ার কথা। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও এটি সত্য। কিন্তু শরীয়াহ আইনের নামে আমাদের হাতে এখন যা আছে, তা বহুকাল আগের ব্যাপার-স্যাপার। এগুলো মূলত অষ্টম ও নবম শতাব্দীর ফিকাহবিদদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা। এগুলোকেই আমরা এখন শরীয়াহ আইন বলে দাবি করছি। এ কারণেই যেখানে শরীয়াহ আইনের প্রয়োগ ঘটেছে, সেখানে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাই শরীয়াহ আইনকে মুসলমানদের নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এই কাজ ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যেতে হবে। কারণ, স্বয়ং শরীয়াহ শব্দের অর্থ হলো– ‘বহমান ঝরনাধারা’। আপনি কেন পানির উৎসের কাছে যান? পানি পান করার জন্যই তো। এটি এমন একটি দরকারী বিষয়, যা আমাদেরকে সবসময়ই করতে হয়। যার ফলে যুগে যুগে একে রিফ্রেশ করা, নতুনভাবে এ নিয়ে চিন্তা করা এবং নতুন নতুন ফর্মূলা বের করা অত্যাবশ্যক।
বহুবিবাহ ইস্যু
৬২৭ খ্রিস্টাব্দ। মোহাম্মদ (সা) ততদিনে মদীনায় একটি নিরাপদ ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। যদিও তাঁকে শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ কোরাইশদের সকল প্রচেষ্টাকেই তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, তারপরও তারা যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিলো। মক্কা নগরী তখনো তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো। আরবের সকল মানুষের কাছে তাঁর বাণী নিয়ে পৌঁছতে হলে তাঁকে এই বাধা অতিক্রম করার একটা পথ খুঁজে বের করা ছিলো জরুরি।
অতীতের যুদ্ধগুলো থেকে মোহাম্মদ (সা) একটি মৌলিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মক্কার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা বেশ কঠিন। তাই তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করতে হবে। এই ভাবনা থেকে তিনি গোটা আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে মৈত্রী গড়া শুরু করলেন। এই সম্পর্ক গড়ার কাজে অন্যতম একটি উপায় ছিলো বিবাহবন্ধন।
মোহাম্মদের (সা) সমালোচকরা সবসময়ই বহুবিবাহ ইস্যুটিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরেছে। অথচ তৎকালীন আরবে এটি ছিলো একটি সাধারণ সামাজিক প্রথা। এরচেয়ে বড় কথা হলো, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর কোনো বিয়ে করেননি। কারো কারো বর্ণনা মতে, তাঁর স্ত্রী ছিলেন নয় জন। অন্যদের মতে, ১১ কিংবা ১৩ জন। এঁদের কেউ ছিলেন বিধবা। কেউ ছিলেন যুদ্ধবন্দী, বিবাহের মাধ্যমে যিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন। এমনকি এঁদের একজন ছিলেন কপ্টিক খ্রিস্টান দাসী। মিশরের বাইজেন্টানীয় শাসক তাঁকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তবে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধুর কন্যা আয়েশার (রা) সাথে বিয়ের ঘটনাটিই সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত। কোনো কোনো সূত্র মতে, আয়েশার (রা) বয়স যখন ছয় কিংবা সাত, তখন বাগদান হয়েছিলো এবং নয় বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সমাধা হয়। অন্যান্য সূত্র মতে, তাঁর বয়স আরো বেশি ছিলো। ১৬ কিংবা ১৭ বছরের কাছাকাছি। বয়স নিয়ে পরিষ্কার তথ্য না থাকায় অনেক সমালোচক এ বিষয়ে মোহাম্মদের (সা) কঠোর সমালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ‘সোর্ড অব দ্য প্রফেট’ গ্রন্থের লেখক সার্জ ট্রিফকভিচ এ ব্যাপারে বলেন,
৫৩ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি নয় বছর বয়সী একজন মেয়েকে বিয়ে করবে এবং শয্যাসঙ্গী করবে, এটি মোটেও সঠিক কাজ নয়। শুধু পাশ্চাত্যের একবিংশ শতাব্দীর মানদণ্ড অনুযায়ীই নয়; বরং মানব ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ের, অধিকাংশ সমাজের সাধারণ নৈতিকতার সাথেও এটি যায় না।
অধ্যাপক তারিক রমাদান বলেন,
এ ব্যাপারে আমার অবস্থান হলো, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৬ কিংবা ৭ ছিলো না, বরং ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে ছিলো। ব্যাপারটা নিয়ে এতোদিন পর এসে বর্তমানকালের গবেষকরা (ঠিক বর্তমানকাল নয়, বরং গত শতাব্দী থেকে) কথাবার্তা বলছেন। আমরা বার বার বলে আসছি, আয়েশার (রা) বয়সের ব্যাপারে যা বলা হয়, সেটিই একমাত্র সত্য নয়। এটি কোরআনের কোনো আয়াত নয়। এটি বরং রাসূলের (সা) জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর প্রকৃত বয়স যাচাই করে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে আমি মনে করি, তাঁর বয়সের ব্যাপারে যা বলা হয়, সেই দাবির মধ্যে সমস্যা রয়েছে।
মোহাম্মদের (সা) মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে আয়েশার (রা) বিয়ের সম্পর্ক অটুট ছিলো। পরবর্তীতে আয়েশা (রা) তাঁর স্বীয় যোগ্যতাবলে অন্যতম শীর্ষ রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের দাবি অনুযায়ী, এটি ছিলো মহানবীর (সা) চাচাত ভাই ও জামাতা আলীর (রা) সাথে আয়েশার (রা) মতদ্বৈততার পরিণতি। এই বিরোধের জের ধরেই পরবর্তীতে শিয়া ও সুন্নী ধারার নামে ইসলামে সবচেয়ে বড় বিভাজনের সূত্রপাত ঘটে। ম্যারল ওয়েন ডেভিস আয়েশার (রা) ব্যাপারে বলেন,
প্রকৃতপক্ষে আয়েশা (রা) কে ছিলেন, কীভাবে তিনি গড়ে ওঠেছিলেন, এটিই হলো আসল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে বাকি সব যুক্তি খারিজ হয়ে যায়। একজন সত্যিকারের সাহসী, স্বাধীন, বুদ্ধিমতি, রাজনীতি সচেতন নারী হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেছিলেন। মহানবীর (সা) জীবন সম্পর্কে আমাদের জানার অন্যতম ভিত্তি হলেন তিনি। মহানবী (সা) সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি, আয়েশা (রা) ব্যতীত এর অন্তত অর্ধেক বিষয় আমাদের অজানাই থেকে যেতো।
পরবর্তীতে বেশকিছু আয়াত নাজিল করে ইসলামের বিবাহ ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে মুসলিম পুরুষরা সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে। তাও শর্ত হলো, ভরণপোষণ ও আচরণের ক্ষেত্রে কারো সাথে বৈষম্য করা যাবে না। অথচ, মোহাম্মদের (সা) সমালোচনার ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলোকেই জোড়ালো উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের অভিযোগ, অন্যদের জন্য এ ব্যবস্থা কার্যকর থাকলেও মোহাম্মদ (সা) স্বয়ং তাঁর সকল স্ত্রীকেই বহাল রাখার সুযোগ পেয়েছেন। আব্দুর রহীম গ্রীন ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বলেন,
আমাদেরকে তৎকালীন বাস্তবতা বুঝতে হবে। পৌত্তলিক আরবে বহুবিবাহের কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছিলো না। এটি অত্যন্ত সাধারণ একটি প্রথা ছিলো। ইসলাম এসে বিবাহের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুসলমানরা চারটির বেশি বিয়ে করতে পারবে না। মহানবীর (সা) যে নয় জন স্ত্রী ছিলেন, তাঁদেরকে তিনি এই বিধান নাজিলের পূর্বেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর জন্যও নতুন করে চারটির বেশি বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু ইতোমধ্যেই যাঁদেরকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁদেরকে রাখার অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। এর পেছনের কারণটা একদম পরিষ্কার। সেটি হলো, গোত্রীয় মৈত্রী বজায় রাখা। এটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তিনি তো আর নিছক একজন নবীই ছিলেন না, তিনি তাঁর জনগোষ্ঠীর প্রধান নেতাও ছিলেন। তাই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গোত্রের সাথে মৈত্রী বজায় রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।
ড. ডেভিড উড বলেন,
সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতের মাধ্যমে মোহাম্মদের অতিরিক্ত স্ত্রী রাখাকে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। এই আয়াতে যত খুশি তত নারীকে বিয়ে করার অনুমতি শুধু মোহাম্মদকে দেয়া হয়েছে। তাই ব্যাপারটি সন্দেহজনক। কারণ, যদি দেখা যায় অন্য যে কারো চেয়ে একজন নবীকে অধিক যৌনসঙ্গী গ্রহণ করার অনুমতি ঐশী প্রত্যাদেশ দেয়, তখন অনেকেই নিজেকে নবী দাবি করতে পারে। মোটকথা হলো, বিষয়টিকে সন্দেহ করার কিছু কারণ কিন্তু রয়েই যায়।
তবে এ যুক্তি খণ্ডন করে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
মহানবী অনৈতিকভাবে জাগতিক আনন্দলাভে মত্ত হওয়ার মতো স্থূল ব্যক্তি ছিলেন, এমনটা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। এই বিয়েগুলোর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো। আয়েশাকে বিয়ে করার কারণ ছিলো, তিনি আয়েশার পিতাকে আরো ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তখন এমন এক নয়া সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, গোত্র বা রক্ত সম্পর্ক যার ভিত্তি ছিলো না। বৈবাহিক সম্পর্ক থাকায় এই উত্তরণ পর্ব কিছুটা সহজ হয়েছিলো।
মুসলিম সূত্রগুলো থেকে আমরা জানি, মোহাম্মদের (সা) কয়েকটি বৈবাহিক সম্পর্ক জীবদ্দশায়ই তাঁকে সমস্যায় ফেলেছিলো। যেমন, তাঁর পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তিনি যখন বিয়ে করলেন, তখন তাঁর শত্রুরা মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গুজব ছড়িয়ে দিলো যে, তাঁদের মধ্যে আগে থেকেই অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। রবার্ট স্পেনসার এ ব্যাপারে বলেন,
সাবেক পুত্রবধূ জয়নব বিনতে জাহাশকে তিনি বিয়ে করার প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্টত বুঝা যায়, সমাজ এর বিরোধী ছিলো। লোকেরা এ ঘটনায় সংক্ষুব্ধ ছিলো। তারা মনে করেছিলো, তিনি এক প্রকার অসম্মানজনক কাজ করেছেন।
আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী, একবার এক সফরের সময় যখন আয়েশাকে (রা) খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন আরো একবার তিনি এ জাতীয় সংকটে পড়েন। পরে অবশ্য তাঁকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো। তিনি এমন এক ব্যক্তির সাথে করে মদীনায় ফিরছিলেন, মোহাম্মদের (সা) সাথে বিয়ের পূর্বে যার সাথে আয়েশার (রা) পরিচয় ছিলো। আবারো তাঁর শত্রুরা গুজব ছড়িয়ে দিলো, তাদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয় কোনো স্ক্যান্ডাল ঘটেছে। মুসলিম বর্ণনা মতে, কোন পক্ষের কথা বিশ্বাস করবেন, তা নিয়ে শুরুতে মোহাম্মদ (সা) নিজেই দ্বিধায় পড়ে যান। পরবর্তীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাজিল হলে তিনি আয়েশার (রা) নিষ্কলুষ থাকার দাবি মেনে নেন। তৎকালীন আরবে ব্যভিচারের প্রচলিত শাস্তি ছিলো পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আয়েশাকে (রা) নিয়ে নাজিলকৃত নতুন ওহীতে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ব্যাভিচারের অভিযোগের সমাধান কীভাবে করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এই সমাধানটি তালেবানের মতো কট্টর দৃষ্টিভঙ্গির গ্রুপগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গে আজমল মাসরুর বলেন,
পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার ব্যাপারটি ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপার। আমাদের জানা মতে, এটি ওল্ড টেস্টামেন্টের বিধান। কোরআনে বর্ণিত বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের শাস্তি হলো দেহের পেছন দিকে ১০০ বেত্রাঘাত। তবে এই শাস্তি কেবল তখনই প্রয়োগ করা যাবে, যদি চারজন ব্যক্তি অভিযুক্ত দুজনের যৌন সম্পর্কের বিষয়টি সরাসরি প্রত্যক্ষ করে সাক্ষ্য দেয়। এই শর্ত অক্ষুণ্ন রেখে শাস্তি প্রয়োগ করা সত্যিই বেশ কঠিন।
ইসলামে পর্দার বিধান
মসজিদে নববীর সাথে লাগোয়া নির্মিত কক্ষগুলোতে তাঁর স্ত্রীগণ বাস করতেন। সেখানে প্রায় সর্বদাই লোক সমাগম লেগে থাকতো। ফলে সেখানে খুব একটা প্রাইভেসি ছিলো না। অন্যদিকে, মোহাম্মদের (সা) শত্রুরা সবসময়ই মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন তৈরির প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো। এ ধরনের খোলামেলা পরিবেশ থাকায় ভবিষ্যতে নতুন করে স্ক্যান্ডাল বানিয়ে তা ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ তাঁর শত্রুদের ছিলো। এই প্রেক্ষাপটে একদিন মোহাম্মদ (সা) ওহীর মাধ্যমে নতুন একটি নির্দেশনা লাভ করলেন। তাঁর স্ত্রীদেরকে শালীনতা বজায় রাখার স্বার্থে আপদমস্তক ঢেকে চলাফেরা করার নির্দেশ দেয়া হলো। এই নির্দেশ মুসলিম নারীদের উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। নারীদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাইরের দুনিয়া সাধারণত এই জায়গা থেকেই দেখে থাকে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং এ ব্যাপারে বলেন,
কাপড় দিয়ে ঢেকে চলাফেরা করার একটি নিদের্শ মহানবীর স্ত্রীগণের প্রতি ছিলো। অবশ্য ঠিক কীভাবে ঢাকতে হবে, তা সুস্পষ্ট নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত, এর মাধ্যমে তাঁদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। মদীনার তৎকালীন নাজুক পরিস্থিতির কারণেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। কারণ, মদীনায় মোহাম্মদের (সা) শত্রুরা তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রীদের নানান ব্যক্তিগত বিষয়কে ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলো। তাই এক ধরনের পৃথকীকরণ প্রয়োজন ছিলো। বলাবাহুল্য, এই নির্দেশ অন্য নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ইসলামের সমালোচকদের দাবি, নারীদের প্রতি ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হলো এই ধরনের পর্দা ব্যবস্থা। ইসলাম যে নারীদেরকে দমিয়ে রাখতে চায়, এর মাধ্যমে সেই আকাঙ্খারই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মোহাম্মদের (সা) মৃত্যুর পর প্রায় শতাধিক বছর পর্যন্ত ইসলামী রীতি হিসেবে এই ধরনের সার্বজনীন পর্দাব্যবস্থার প্রচলন ছিলো না। প্রিন্সেস বাদিয়া বিনতে আল হাসান এই ব্যাপারে বলেন,
নারী-পুরুষ যেন শালীনতা বজায় রেখে চলাফেরা করে, সে ব্যাপারে ধর্ম কনসার্ন থাকে। কিন্তু ঠিক কতটুকু হলে শালীনতার শর্ত পূরণ হবে, তা উন্মুক্ত আলোচনার বিষয়। হিজাব পরিধান না করা সত্ত্বেও একজন মুসলিম হিসেবে আমি কম্প্রোমাইজ করে চলছি, এমনটি মনে করি না। এমনকি ভবিষ্যতেও আমি হিজাব পরবো না। কারণ আমি নিজেই বলি যে, আমি নিষ্ঠাবান মুসলমান নই। পোশাক-আশাক দেখে কারো ঈমানের নিষ্ঠা বা গভীরতা যাচাই করা যায় না।
ব্রিটেনসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশে গত প্রায় দুই দশক ধরে হিজাব হয়ে উঠেছে অধিকাংশ মুসলিম নারীর আত্মপরিচয়ের প্রতীক। কেউ হয়তো শুধু চুল ঢাকেন, অন্যরা পুরো মুখমণ্ডলই ঢাকেন। যা হোক, পাশ্চাত্যে হিজাব এখন একটি বিতর্কিত বিষয়। কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশ ইতোমধ্যে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করেছে। মুসলিম নারীদের নিয়ে লেখালেখি করেন ফাতিমা বরকতুল্লাহ। তাঁর সাথে হিজাব প্রসঙ্গে আমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়েছে –
– ফাতিমা, আপনি তো হিজাব পরিধান করেন। এটি কি আপনার পারিবারিক বাধ্যবাধকতা, নাকি নিজের ইচ্ছা থেকেই?
– সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা থেকে আমি হিজাব করি। আমার আধ্যাত্মিক পথচলার সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহর কাছে নৈতিক দিক থেকে নিজেকে উন্নততর হিসেবে তুলে ধরার ইচ্ছা থেকে আমি হিজাব করি। শরীর ঢাকার জন্য বোরকা পরাটা আমার কাছে সকালে বাইরে বেরুনোর প্রস্তুতি হিসেবে জিন্স বা অন্য কোনো পোশাক পরার মতোই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।
– এটি তো মূলত এক ধরনের গাউন। তাই না?
– হ্যাঁ, এটি একটি বাড়তি পোশাক। একে ‘আবায়া’ বা ‘জিলবাব’ বলা হয়। এটি পরিধানের পর আমি ‘খিমার’ তথা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকি। তারপর আমি একটি ছোট্ট নেকাব পরিধান করি। এভাবেই আমি বাইরে যাই।
– অনেক মুসলিম নারীই তো শুধু মাথা ঢাকার জন্য খিমার তথা স্কার্ফ পরিধান করেন। আপনি কেন তা না করে পুরো মুখমণ্ডল ঢাকেন?
– আমি মনে করি, আরো বেশি শালীনতা মেনে চলাফেরা করা আমার পক্ষে সম্ভব। এটি আরো বেশি সওয়াবের কাজ। তাই আমি আসলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এভাবে চলি।
– এই ব্যাপারটি কোত্থেকে এসেছে? এটি কি কোরআনে আছে? এটি কি…
– হ্যাঁ, এটি আপনি কোরআনে পাবেন। সূরা আহযাবের একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং বিশ্বাসী নারীদের বলুন! তারা যখন বাইরে যায়, তখন যেন তাদের পরিধেয় কাপড়ের উপর আরেকটি বাড়তি কাপড় পরিধান করে নেয়।” এই ব্যাপারটি বুঝানোর জন্য আরবীতে ‘জালাবীব’ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে…।
– একদম ঠিক বলেছেন। ব্যাখ্যার উপরই আসলে সবকিছু নির্ভর করছে। সাধারণ মুসলিম নারীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মুখ ঢাকতে হবে, এমন কোনো বিধান কোরআনের কোথাও বলা নেই। এ সংক্রান্ত প্রচলিত বিধানটি একটা ব্যাখ্যা মাত্র।
– হ্যাঁ, মুখমণ্ডল ঢাকার কথা যদি বলেন, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।
ম্যারল ওয়েন ডেভিস এ প্রসঙ্গে বলেন,
পোশাকের ব্যাপারে সুনিদ্ষ্টিভাবে মাত্র একটি আয়াত রয়েছে, যেখানে দেহের উন্মুক্ত অংশগুলো ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। কালো প্যাকেটে নিজেকে ঢেকে রাখার কথা সেখানে বলা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম নারীরা এই আয়াতকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। মুসলিম পুরুষরাও অন্যান্য সমাজের এ সংক্রান্ত প্রথাগুলোকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা আকারে সংযোজন করে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। এছাড়া আত্মপরিচয়ের রাজনীতিও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে। তবে আমার অবস্থান হলো, প্রচলিত পর্দাপ্রথার কোনো বাধ্যবাধকতা যদিও নেই, তারপরও এটি পরিধান করা বা না করার স্বাধীনতা নারীদের থাকা উচিত।
কোরাইশ নিয়ন্ত্রিত কাবায় হজ করার ঘোষণা
মোহাম্মদের (সা) বিরোধীরা বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে তাঁর মর্যাদাহানীর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি এই বিয়েগুলোকে আরবে তাঁর ক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং তা আরো বিস্তৃত করতে কাজে লাগিয়েছেন। এরপর তিনি পুনরায় মক্কার দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত পেলেন। ফলে তিনি বার্ষিক হজ পালনের জন্য মক্কায় অবস্থিত কাবাঘরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিলেন। এটি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকের ঘটনা।
মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের কাছে কাবা ছিলো ইবাদতের কেন্দ্র। কাবার দিকে ফিরেই তাঁরা নামাজ আদায় করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, সর্বপ্রথম কাবা তৈরি করেছিলেন নবী ইবরাহীম (আ)। তাঁদের কাছে এই ঘরটি আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদী বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু কাবা ঘরে প্রবেশের নিয়ন্ত্রণ ছিলো মক্কার শাসকগোষ্ঠী তথা মোহাম্মদের (সা) শত্রু কোরাইশদের হাতে। আরবের গোত্রগুলোর পূজনীয় শত শত দেবদেবীর মূর্তি কাবাঘরে রক্ষিত ছিলো। তিনি এবার সেই পবিত্র ঘরের উপর কোরাইশদের নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
মহানবী ঘোষণা করলেন, তিনি হজ করতে যাচ্ছেন। এই ঘোষণায় সবাই হতবিহ্ববল হয়ে পড়েছিলো। কারণ, হজে কোনো প্রকার অস্ত্র সাথে রাখা নিষিদ্ধ। আর এই নিরস্ত্র অবস্থায় তিনি যেতে চাচ্ছেন শত্রুর ডেরায়!
বারনাবি রজারসন এ ব্যাপারে বলেন,
এই ঘটনায় আপনি আবারো ব্যক্তি মোহাম্মদের জাদুকরি প্রতিভার ছোঁয়া পাবেন। এতোদিন তিনি যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। এবার তিনি বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, আমরা এবার আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করবো।

হোদায়বিয়ার সন্ধি
মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদের কাফেলা মক্কা থেকে আট মাইল দূরে হুদায়বিয়ায় থেমে যেতে বাধ্য হলো। কারণ, কোরাইশরা তাদের চিরাচরিত আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিলো। মুসলিম কাফেলার অগ্রগতি রুখতে তারা একদল অশ্বারোহীকে পাঠালো। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডার পর উভয় পক্ষ অবশেষে একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে। এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক এই ঘটনার স্মারক হিসেবে সেই স্থানটিতে বর্তমানে একটি মসজিদ রয়েছে।
আপাতদৃষ্টিতে সন্ধির বিষয়বস্তু মোহাম্মদের (সা) জন্য ছিলো অত্যন্ত অপমানজনক। কোরাইশদের শর্তানুযায়ী, মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে এবার হজ না করেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। মক্কার বাণিজ্য কাফেলাগুলোর উপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। এসব কিছুর বিনিময়ে মুসলমানরা মক্কায় গিয়ে হজ করতে পারবে। তবে এ বছর নয়, আগামী বছর। এ সকল কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করার জন্য যখন নিয়ে আসা হলো, তখন দেখা গেলো তাতে মোহাম্মদকে (সা) ‘আল্লাহর রাসূল’ হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে। কোরাইশ প্রতিনিধি এতে আপত্তি জানিয়ে বললো, তাদের কাছে তিনি শুধুই আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ। মোহাম্মদের (সা) অনুসারীদের কাছে এটি ছিলো চরম অপমান। মুসলিম বর্ণনা মতে, মোহাম্মদের (সা) তরুণ চাচাতো ভাই আলী (রা) ‘আল্লাহর রাসূল’ অংশটুকু কেটে দিতে অস্বীকার করলেন। উল্লেখ্য, সন্ধিপত্রের চূড়ান্ত সংস্করণ তিনিই লিখেছিলেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন,
তখন মোহাম্মদ বললেন, আমাকে একটা কলম দাও, আর কোথায় ‘আল্লাহর রাসূল’ লেখা রয়েছে, তা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি নিজে সে অংশটুকু কেটে দিলেন। আমি মনে করি, অধিকারের জায়গা থেকে নয়, বরং অহংকারবশতই কোরাইশরা এই অংশটুকু কেটে দিতে বাধ্য করেছে। তাছাড়া কোরআনে বলা হয়েছে, শত্রুপক্ষ যদি শান্তির আহ্বান জানায়, তাহলে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র সংবরণ করতে হবে। তারপর শান্তির স্বার্থে যে কোনো শর্তে রাজি হতে হবে, তা যতই অসুবিধাজনক হোক না কেন।
মোহাম্মদের (সা) অনুসারীদের দৃষ্টিতে চুক্তির শর্তাবলি এবং চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া ছিলো মুসলমানদের জন্য নিতান্তই অবমাননাকর। তবে মোহাম্মদের (সা) দৃঢ় মনোভাবের কারণেই তাঁরা কোনো প্রতিবাদ করেনি। যদিও মুসলমানদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক ছিলো। কারণ, তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সপ্তম শতাব্দীর আরবে এ ধরনের কিছু করার কথা আগে কেউ কখনো শুনেনি। আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য যুগের পর যুগ, বংশ পরম্পরায় লড়াই করে যাওয়াই ছিলো তখনকার সমাজের প্রচলিত প্রথা। কিন্তু কয়েক বছরের অমীমাংসিত রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলার পর মোহাম্মদ (সা) এবার তাঁর শত্রুদেরকে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির বার্তা দিয়ে বশ করতে চাইলেন। কোরাইশদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি শুধু কাবা ঘরে প্রবেশের সুযোগই লাভ করলেন, তা নয়; বরং তিনি যে তাদের সমমর্যাদার প্রতিপক্ষ, অতি গুরুত্বপূর্ণ এই স্বীকৃতিটাও আদায় করে নিলেন। অধ্যাপক সাজ্জাদ রিজভী এ ব্যাপারে বলেন,
এক দিক থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিলো অত্যন্ত সামান্য একটি অর্জন। কারণ, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী এখনই আমরা কাবায় যেতে পারছি না। তবে চুক্তিটি করলে ভবিষ্যতে সেখানে যেতে পারবো। জানা কথা হলো, যুদ্ধের চেয়ে সমঝোতা উত্তম। আমরা জানি, কোরআনেও বার বার বলা হয়েছে, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি উত্তম। সেই হিসেবে চুক্তিটি কোরআনের এই মূলনীতির সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে।
মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীরা মদীনায় ফিরে আসার পর পরই একটি নতুন ওহী নাজিল হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি যে কোনো অবমাননাকর পরাজয় নয়, ওহীর মাধ্যমে তা আশ্বস্ত করা হয়েছে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
তিনি বললেন, “মাত্রই একটি ওহী নাজিল হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে একে পরাজয় মনে হলেও এটি একটি সুস্পষ্ট বিজয়।” কোরাইশরা পুরানো গোত্রীয় ধ্যানধারণা তথা হিংস্রতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকার ইত্যাদির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো। অন্যদিকে, মুসলমানদের হৃদয় ছিলো শান্তির মর্মবাণীতে পরিপূর্ণ। যা প্রায় সময়ই আমরা ভুলে যাই। মোহাম্মদ কতগুলো যুদ্ধ করেছেন, আমরা সাধারণত এসব বিষয় শুনে থাকি। কিন্তু তাঁর এই অসামান্য, অহিংস আত্মরক্ষামূলক দিকটির কথা আমরা ভুলে যাই। হুদাইবিয়ার ঘটনার পর পরিস্থিতি তাঁর অহিংস আন্দোলনের অনুকূলে চলে আসে।
অধ্যাপক জন এসপোজিটো বলেন,
যুদ্ধংদেহী পরিবেশে থেকেও মোহাম্মদ কূটনীতিকে অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছেন, শীর্ষ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছেন, তাদের সাথে সমঝোতা চুক্তিতে আসার চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন মদীনার সমাজের দিকে খেয়াল করলে আপনি দেখবেন, ভিন্ন বিশ্বাস ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য সেখানে জায়গা ছিলো। তবে কোনো আগ্রাসন বা প্রতিরোধের মুখে পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে যা করণীয়, তিনি তা-ই করেছেন। আমার কাছে ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার। মহানবীর পক্ষ হতে বিরোধীদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করার আহ্বান জানানোর কোনো নজির আপনি খুঁজে পাবেন না।
পুরো আরব জুড়ে মোহাম্মদ (সা) তাঁর বাণী ছড়িয়ে দেয়ার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিলো এর একটি অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রতিপক্ষের চরম অপমান সহ্য করার প্রস্তুতিও যে তাঁর ছিলো, এ ঘটনা থেকে সেটি বুঝা যায়। অথচ বর্তমান দুনিয়ায় মোহাম্মদকে (সা) অনেকেই শান্তির শত্রু বিবেচনা করে। তারা মনে করে, ইসলাম হলো জিহাদের ধর্ম। এক্ষেত্রে জিহাদ বলতে তারা ধর্মযুদ্ধকেই বুঝে থাকে।
জিহাদ কি ধর্মযুদ্ধ?
জিহাদী বলে পরিচিত গোষ্ঠীগুলোর হাতে দুনিয়া জুড়ে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে। অথচ মোহাম্মদের (সা) সময় জিহাদী হিসেবে কেউ পরিচিত ছিলো না। জিহাদী গোষ্ঠীগুলো দাবি করে, কোরআন এবং স্বয়ং মোহাম্মদ (সা) তাদের কাজের বৈধতা ও অনুপ্রেরণার উৎস। যেমন, ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলাকারীদের অন্যতম মোহাম্মদ সিদ্দিক খান এক ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, “প্রিয় নবী এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীদের হৃদয়ে জিহাদ এবং শাহাদাতের তামান্না যে গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো, তা সহজেই বুঝা যায়।”
তথাকথিত জিহাদীদের বেশিরভাগই তাদের সহিংস কার্যক্রমের বৈধতার জন্য সাধারণত কোরআনের একটি আয়াত ব্যবহার করে, যা কারো কারো কাছে ‘তলোয়ারের আয়াত’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অধ্যাপক তারিক রমাদান এ সম্পর্কে বলেন,
হ্যাঁ, কোরআনে আপনি এ জাতীয় আয়াত পাবেন। এগুলো যে যুদ্ধ ও সংঘাত সম্পর্কিত আয়াত, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এই কালে এসে আমাদেরকে কোরআন নামক একটি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থকে পাঠ করতে হবে তৎকালীন ইতিহাসের আলোকে। এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিলো সুনির্দিষ্ট একটি সময়কালে। মুসলমানরা তখন নির্যাতন সহ্য করছিলো, প্রতিরোধের চেষ্টা করছিলো। টিকে থাকাটাই তখন একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো। এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিতে হবে। শিয়া-সুন্নী উভয় পক্ষের মূলধারার আলেমরা মনে করেন, নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করা এবং যুদ্ধ-সংঘাত উসকে দেয়ার জন্য এই আয়াতগুলো ব্যবহার করা যাবে না। এটি সম্পূর্ণ অন্যায়।
কোরআনের আয়াতের বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যা এ জাতীয় বিতর্কের মূল কারণ। জিহাদ পরিভাষাটির অর্থ যে ধর্মযুদ্ধ নয়, সে ব্যাপারে অধিকাংশ স্কলারই একমত। তাদের মতে, এর প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধ্যাপক রিচার্ড বোনি এ ব্যাপারে বলেন,
জিহাদের ধারণাটি কোরআন থেকেই এসেছে। মহানবী ওহীর নির্দেশ আকারে এটি লাভ করেছিলেন। কোরআনে ‘জিহাদ’ শব্দটি রয়েছে প্রায় ৩৫ বার। প্রায় সবক্ষেত্রেই এটি চূড়ান্ত কর্মপ্রচেষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কোনো ধরনের ইতিবাচক কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে পারে। হতে পারে তা ব্যক্তির আত্মসংশোধনের ব্যাপার। হতে পারে মন্দ পরিহার করে সৎকর্ম সাধনের চেষ্টা। যুদ্ধ বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে। যদিও জিহাদ আর যুদ্ধ সমার্থক নয়। যুদ্ধ বুঝানোর জন্য ভিন্ন আরেকটি পরিভাষা (‘কিতাল’) ব্যবহৃত হয়েছে।
মোহাম্মদ (সা) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এর প্রত্যেকটির পেছনেই সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছিলো। এতোগুলো যুদ্ধে জড়ানোর পরও বেসামরিক লোকদের উপর আক্রমণের কোনো নজির তাঁর জীবনে নেই। অধ্যাপক রিচার্ড বোনি বলেন,
জিহাদ সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, মহানবীর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্রমেই এটি একটি ন্যায়যুদ্ধের ধারণা হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। ন্যায়যুদ্ধ বলতে সেনাবাহিনীকে একটি নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য করা, যেমন– বেসামরিক লোকদের উপর আক্রমণ বা তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না, কোনোভাবেই অন্য ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা যাবে না ইত্যাদি।
যুদ্ধে অংশগ্রহণের এইসব মূলনীতি এখনকার মুসলিম চরমপন্থীদের মধ্যে দেখা যায় না। আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শুধু পাশ্চাত্যের নাগরিকদেরই হত্যা করছে না, মুসলিম বিশ্বের মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোতে পর্যন্ত হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। বর্তমানে ব্রিটেনের কোনো মুসলিম অ্যাক্টিভিস্ট বা গ্রুপই সহিংস পথে গিয়ে বিদ্যমান আইনকে অমান্য করতে চাইবে না। তৎসত্ত্বেও, গত ১০ বছরে দুই শতাধিক মুসলিম সন্ত্রাসমূলক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এমনই একজন হলেন ব্রিটিশ মুসলিম আব্দুল মুহিত। সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়নের অভিযোগে ২০০৮ সালে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে দুই বছরের জেল দেয়া হয়। আরেকজন হলেন মিজানুর রহমান। হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগে ২০০৬ সালে তার চার বছরের জেল হয়। দুজনই ইতোমধ্যে তাদের সাজা ভোগ করেছেন। এদের সাথে আমি কথা বলেছি। এখনো তারা বর্তমান দুনিয়ায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দৃঢ় মতামত পোষণ করেন।
– বর্তমানে জিহাদের ব্যাখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? কারণ, বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এখন জিহাদ মানে নিছক যুদ্ধ বা লড়াই-সংগ্রাম নয়। এর নানান অর্থ তাদের কাছে রয়েছে।
– মিজানুর রহমান: জিহাদ মানে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এ ব্যাপারে অতীতের আলেমদের সবাই একমত। হ্যাঁ, তাদেরকে নিছক জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর জন্য জিহাদ করা যাবে না। তবে শরীয়াহ কায়েমের পথে সকল বাধা দূর করে আল্লাহর বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য জিহাদ করতে হবে। দুনিয়া জুড়ে ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যও জিহাদ করতে হবে।
– জিহাদের নামে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালানো কি অনুমোদনযোগ্য? মহানবীর (সা) কর্মময় জীবন সম্পর্কে আপনার বুঝজ্ঞান এ সম্পর্কে কী বলে?
– আব্দুল মুহিত: একদম সোজা কথায় ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের যুক্তি হলো, আপনি যদি আপনার প্রতিনিধি হিসেবে একটি সরকারকে নির্বাচিত করেন এবং তারা যদি অন্য একটা দেশে বোমা হামলা কিংবা মানুষ মারার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার দায় আপনার কাঁধেই এসে পড়ে। এটি কাউকে খুন করার জন্য একজন খুনী ভাড়া করার মতোই একটি ব্যাপার। এই খুনের জন্য শুধু খুনি নিজেই দায়ী নয়, আমার উপরও এর দায় এসে পড়ে। অতএব, এইসব নিরস্ত্র লোকগুলোই কিন্তু এমন এক সরকারকে ভোট দিয়েছে, যারা অন্যায়-অপরাধ করে। ফলে এই ভোটদাতাদেরও দায় আছে। ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টিতে তারা অবশ্যই অপরাধী।
মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষ সবার নিকটই জিহাদের এই ধারণা ঘৃণ্য একটি ব্যাপার। জিহাদের এ ধরনের ব্যাখ্যা স্বয়ং মোহাম্মদেরও (সা) জানা ছিলো না। তাঁর কাছে জিহাদ মানে নিছক যুদ্ধ করে মানুষ মারার ব্যাপার ছিলো না। তখন জিহাদ ছিলো আল্লাহর কাছে নিজেকে উন্নত মানুষ হিসেবে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা। ইসলামে আছে ন্যায়যুদ্ধের ধারণা। মোহাম্মদ (সা) নিজেও অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই নিরপরাধ মানুষ হত্যার করার জন্য যুক্তি দাঁড় করাননি। আজমল মাসরুর এ প্রসঙ্গে বলেন,
যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা সংক্রান্ত কোরআনের যে আয়াত রয়েছে, সেগুলো আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে নিজেকে এবং অন্যান্যদেরকে হত্যা করার বৈধতা দেয় না। মনে রাখা দরকার, ইসলাম যুদ্ধের অযুহাতে বেসামরিক জানমাল ধ্বংস করাকে অনুমোদন করে না। চরমপন্থীরা হত্যার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু লোকের উপর পরিকল্পিতভাবে বোমা হামলা করে। কিন্তু এর ফলে শুধু তারাই নয়, টার্গেটের বাইরে অন্যান্য মানুষও নিহত হয়। একে বলা হয় কোল্যাটারাল ড্যামেজ। এর কোনোটাই ইসলামে মোটেও অনুমোদিত নয়।
মক্কায় প্রবেশ
যা হোক, মোহাম্মদের (সা) শান্তিপূর্ণ জিহাদ এতদিনে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সাত বছর আগে জীবন বাঁচাতে খালি হাতে যে শহর ত্যাগ করে তিনি অভিবাসী হয়েছিলেন, হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলে তিনি এবার সেই নগরীটিতে ফিরে যেতে পারছেন। একটি ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় সমাজের প্রধান এবং আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হিসেবে তিনি মক্কায় ফিরছেন।
কাবা পরিদর্শনের জন্য মক্কায় প্রবেশের ব্যাপারে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে কোরাইশরা মুসলমানদেরকে সম্মতি প্রদান করে। মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে তিনদিন অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়। তবে এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই মোহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মক্কার লোকেরা মুসলমানদেরকে কাবায় প্রবেশ করতে দেখেছে, তাদের চমৎকার ও আন্তরিক ব্যবহার খেয়াল করেছে। মুসলমানদের সুন্দর আচরণ মক্কায় কোরাইশদের দুঃসহ শাসনের ইতি ঘটাতে কিছুটা হলেও যে ভূমিকা রেখেছিলো, তা নিশ্চিত। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।
মক্কা বিজয়
এক বছর পর কোরাইশরা মোহাম্মদের (সা) মিত্র একটি গোত্রের উপর হামলা করার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করলো। এটা ছিলো কোরাইশদের চরম ভুল। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মহানবী (সা) ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে মার্চ করলেন। এই বাহিনী মোকাবেলার সাধ্য কোরাইশদের ছিলো না। তারা ধরেই নিয়েছিলো, মোহাম্মদ (সা) মক্কায় প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাবেন, বহু বছরের নির্যাতন ও যুদ্ধবিগ্রহের রক্তাক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। নগরীর উপর কোরাইশরা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারালো। তবে চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে মহানবীর (সা) ভূমিকায় মক্কার লোকেরা অভিভূত হয়ে পড়লো। মোহাম্মদ (সা) ঘোষণা করলেন, শত্রুদের সকলকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাউকেই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না বলে তাঁর সাথীদেরকেও সতর্ক করে দিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে তিনি সচেতনভাবেই বিরোধ মীমাংসার এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক সাজ্জাদ রিজভী বলেন,
মক্কা বিজয় ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, এ বিজয়ের পর অভাবনীয়ভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিলো। লোকদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা বা না করা, কিংবা অন্য কোথাও চলে যাওয়া, মোটকথা নিজের ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তাদের ছিলো। এই বিজয়ের আরেকটি তাৎপর্য রয়েছে। সেটা হলো, বিজয়ের পর মক্কা হয়ে ওঠলো নতুন বিশ্বাসব্যবস্থার কেন্দ্র। এর মাধ্যমে মহানবীর (সা) মিশনের প্রথম ধাপটি নিশ্চিতভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সংঘাতের আর কোনো প্রয়োজনই ছিলো না।
এই সময়টির জন্যই মোহাম্মদ (সা) অপেক্ষায় ছিলেন। কোরাইশদেরকে হত্যা করতে তিনি মক্কায় ফিরে আসেননি। এক আল্লাহর পবিত্র ঘর হিসেবে কাবার মর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতেই তিনি মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। মুসলিম বর্ণনা মতে, তিনি ও তাঁর হাজারো অনুসারী কাবায় কাবায় প্রবেশ করে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি-প্রতিমূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয় সম্পর্কে বারনাবি রজারসন বলেন,
তিনি শুধু তাদেরকে ক্ষমাই করেননি। তাদের প্রতি যথেষ্ট উদারতাও দেখিয়েছেন। শত্রুতার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে দিয়েছেন উপহার। এমনকি যেসব গোত্রীয় সর্দার তাঁর বিরোধিতাও করেনি, আবার তাঁর বাণী গ্রহণও করেনি; তারাও মোহাম্মদের (সা) কাছে উট, বিভিন্ন গবাধি পশু, রৌপ্য ইত্যাদি পাওয়ার আশা করছিলো। তিনিও তাদেরকে সেসব দিয়েছিলেন। এটি ছিলো ন্যায়ের অসাধারণ এক দৃষ্টান্ত।
ম্যারল ওয়েন ডেভিস এ ব্যাপারে বলেন,
আমার মনে হয়, এই ঘটনাটি মহানবীর (সা) জীবনের মূল শিক্ষা। মহানবীর (সা) জীবনকে আমি যতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি, সে আলোকে বলতে পারি, এটি ছিলো তাঁর সমগ্র জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না। প্রতিশোধ নয়, বরং ব্যাপক সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সকলকে নিয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলাই ছিলো তাঁর দাওয়াতের মূল কথা। তাই আমরা যে ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে চাই, সে ধরনের সমাজের মডেল হিসেবে তাঁর মক্কায় প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটিকেই আমার কাছে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হয়।
ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
অবশেষে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। তবে বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব বিষয় বাধ্যতামূলক বলে আমরা মনে করি, তেমন কোনো কিছুই তিনি সেখানে চাপিয়ে দেননি। এ কারণেই তখনকার মতাদর্শিক গোঁড়ামী নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। যে গোত্রবাদ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা তৈরি করে রেখেছিলো, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তার অবসান ঘটার প্রসঙ্গটিই বরং আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।
মক্কা নগরী মোহাম্মদের (সা) নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জন্মভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি বরং মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন। কোরাইশদের পরাজিত করার কিছুদিনের মধ্যেই আরবের বাদবাকি গোত্রগুলো তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলো।
রক্তপাতহীনভাবে মক্কা বিজয়ের ঘটনা থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছিলো, মোহাম্মদের (সা) আন্দোলন সফল হতে চলেছে। উপরন্তু, তাঁর ন্যায়বিচারের বাণী এবং এই বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে শান্তি ও বিরোধ মীমাংসাকে অগ্রাধিকার দেয়ায় অসংখ্য মানুষ তা গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনকি, পুরো গোত্র একসাথে ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও ঘটতে থাকে। ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে পৌত্তলিকদের সর্বশেষ ঘাঁটি তায়েফেরও পতন ঘটে। ফলে মোহাম্মদ (সা) এবার সত্যিকার অর্থে সমগ্র মুসলিম আরবের শাসক হয়ে ওঠলেন।
ইতোমধ্যে মহানবীর (সা) নবুয়তের ২০ বছর পার হয়ে গেছে। এক দশকেরও বেশি সময় তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ নিরাপত্তাহীন এক অনিশ্চিত জীবন পার করেছেন। দিনকে দিন তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদের (সা) আধ্যাত্মিক, সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসামান্য দক্ষতার কারণে খাদের কিনারা থেকে তাঁরা ফিরে আসতে পেরেছিলেন। অবশেষে আপাতদৃষ্টিতে অপমানজনক একটি চুক্তি স্বাক্ষরের (হুদাইবিয়ার সন্ধি) পর তাঁরা শত্রুদের উপর বিজয়ী হন। মহানবীর (সা) নেতৃতৃগুণ নিয়ে জন আডায়ার বলেন,
একজন ভালো নেতার মধ্যে আমরা এখন যেসব গুণাবলি দেখি, তার সবকটিই মোহাম্মদের মধ্যে ছিলো। তাই তিনি আজ পর্যন্ত উদাহরণ হয়ে আছেন। একজন ভালো নেতা মানে, কাজের প্রতি একাগ্রতা থাকবে, চারিত্রিক সুষমা বজায় থাকবে। যে কোনো নেতার মধ্যে কঠোরতা, একাগ্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সমন্বয় থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। মোহাম্মদের মধ্যে এইসবগুলো গুণই সুস্পষ্টভাবে ছিলো। আমার মতে, আন্তরিকতা, মানবতাবোধ ও দয়ামায়া থাকাটাও গুরুত্বপূর্ণ। মোহাম্মদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখবো, তিনি ছিলেন এইসব মানবিক গুণাবলির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
মোহাম্মদ (সা) যা যা চেয়েছিলেন, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তার প্রায় সবই তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি আরবে একটি পর্যায় পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। যা সেখানে খুবই দুর্লভ ব্যাপার ছিলো। তিনি ইসলামের ভিত্তি ও আইনকানুনগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। একটি নতুন মুসলিম সমাজের ভিত্তিও তিনি গড়ে গেছেন। এসব করতে করতে তিনি একজন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধে পরিণত হয়ে পড়লেন। ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। সে বছরই তিনি শেষবারের মতো মক্কায় আসেন এবং প্রথম ও শেষবারের মতো হজ পালন করেন। হজে আগত হাজীদের উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ‘বিদায় হজের ভাষণ’ হিসেবে পরিচিত।
বিদায় হজের ভাষণ
আরাফাতের ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে একটি উটের উপর বসে তিনি এই ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তাঁর কথাগুলো সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য পুরো ময়দান জুড়ে ঘোষক নিয়োজিত ছিলো। মহানবী (সা) নিজেই পরবর্তীতে বলেছেন, এটি ছিলো গভীর আবেগময়ী একটি ভাষণ। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ যা কিছু অর্জন করতে পেরেছেন বলে তিনি মনে করতেন, তার একটি সারসংক্ষেপ এই ভাষণে তিনি তুলে ধরেছিলেন।
হে জনমণ্ডলী! মনোযোগ দিয়ে শোনো। আগামীবার তোমাদের মাঝে ভাষণ দেয়ার জন্য আমি নাও থাকতে পারি। তাই যা বলছি, সতর্কতার সাথে তা শুনে রাখো। আজকে যারা এখানে উপস্থিত নেই, তাদের কাছে আমার কথাগুলো তোমরা পৌঁছে দিও।
– মহানবীর বিদায় হজের ভাষণ থেকে
এ ব্যাপারে আব্দুর রহীম গ্রীন বলেন,
বিদায় হজের ভাষণ পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, এটি ছিলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে মহানবীর (সা) হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানানো আহ্বান ও সতর্কবার্তা। মুসলমানদেরকে তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্নতা আপনার চোখে পড়ার কথা। এই ভাষণ মুসলমানদেরকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত এবং তা মেনে চলার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা উচিত। কারণ, এতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে।
নিজের দাসদাসীদের উপর অবিচার করো না। মনে রেখো, একদিন তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সতর্ক হও। আমার মৃত্যুর পর তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ো না।
– মহানবীর বিদায় হজের ভাষণ থেকে
অধ্যাপক জন এসপোজিটো বিদায় হজের ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দেন,
মনে করে দেখো– আদম, ইবরাহীম, মুসা, ঈসাসহ রাসূলগণের প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম বাণী কী ছিলো! একমাত্র পরম ও চূড়ান্ত সত্য হলো স্বয়ং এক আল্লাহ। তিনি হলেন সর্বস্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিচার দিবসের মালিক।
সকল মানুষ এসেছে আদম ও হাওয়া থেকে। তাই অনারবদের উপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবদের উপরও অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোদের উপর সাদাদের, কিংবা সাদাদের উপর কালোদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো খোদাভীরুতা ও সৎকর্ম।
– মহানবীর বিদায় হজের ভাষণ থেকে
ক্যারেন আর্মস্ট্রং বিদায় হজের ভাষণ সম্পর্কে বলেন,
তিনি বলেছেন, সকল মানুষ এক। আল্লাহ তোমাদেরকে পৌত্তলিক গোত্রতন্ত্র এবং বংশীয় গর্ব প্রদর্শনের পৌত্তলিক রীতি থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। স্মরণ রেখো, সকল মানুষ এসেছে আদম থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধূলিকণা থেকে। তারপর তিনি কোরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন, যা আমাদের সময়ের জন্য পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক – “হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। তারপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে ভাগ করে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।” পরস্পর যুদ্ধ-সংঘাত, নির্যাতন, দখলদারিত্ব, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ কিংবা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর জন্য এই বিভাজন করা হয়নি। একে অপরকে জানার জন্যই মানবজাতিকে এভাবে ভাগ করা হয়েছে।
তোমরা যারা আমার কথা শুনছো, তারা অন্যদের কাছে এই কথাগুলো পৌঁছে দেবে। তারা আবার পৌঁছে দেবে আরো যারা শুনেনি, তাদের কাছে। তোমরা যারা সরাসরি আমার কথা শুনছো, তাদের চেয়ে পরবর্তী কেউ হয়তোবা আমার কথা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। হে আল্লাহ! সাক্ষী থেকো, আমি তোমার বান্দাদের কাছে তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি।
– মহানবীর বিদায় হজের ভাষণ থেকে
ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন,
তারপর তিনি উপস্থিত জনসমুদ্রের কাছে জানতে চাইলেন, ‘হে লোকসকল! হে মুসলমানেরা! তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব কি আমি পালন করতে পেরেছি?’ লোকেরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, ‘নায়াম’, ‘হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।’ জনসমুদ্রের এই সাক্ষ্য ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তিনি লোকদেরকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি কি পেরেছি?’ প্রতিবারই তারা জবাব দিলো, ‘নায়াম’, ‘হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।’ আমার মতে, এটি ছিলো সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও আবেগময় একটি মুহূর্ত।
জিয়াউদ্দীন সরদার বলেন,
এই ভাষণ ছিলো তাঁর সমগ্র জীবনের একটি সারসক্ষেপ। বিগত ২৩ বছরে তিনি যেসব শিক্ষা দিয়েছেন, এই ভাষণে সেসব মূলনীতির উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আরব ও অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারপর বলেছেন, নিজ পরিবারের দেখাশোনা করো। এগুলোই ছিলো তাঁর জীবনের শিক্ষা। আর কিছু না পড়লেও শুধু বিদায় হজের ভাষণও যদি আপনি পড়ে থাকেন, তাহলে মোহাম্মদের (সা) জীবনের সারনির্যাস আপনি পেয়ে যাবেন।
ম্যারল ওয়েন ডেভিস বলেন,
মহানবীর (সা) বিদায় হজের ভাষণ আধুনিক ও সমসাময়িক মুসলিম সমাজের কর্তব্য ঠিক করে দিয়েছে। কী করলে আমরা ব্যর্থ হয়ে পড়বো, ব্যর্থতা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী, এই ভাষণে এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। এটি ছিলো মহানবীর (সা) সমাজ পরিবর্তনের মিশনের সারনির্যাস।
মহামানবের বিদায়
বিদায় হজের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত মোহাম্মদ (সা) মদীনায় তাঁর ছোট্ট বাড়িতে ফিরে গেলেন। তখন থেকেই তাঁর মাথাব্যথা ও শারীরিক দুর্বলতা শুরু হয়। তারপরও তিনি মসজিদে হাজির হওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দিন দিন তাঁর অসুস্থতা বেড়েই চলছিলো। ফলে তিনি প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকতেন। আয়েশা (রা) তাঁর সেবা করতেন। হঠাৎ একদিন তিনি কিছুটা সুস্থবোধ করলেন। মুহূর্তেই খবরটি মদীনা জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু খুব অল্প সময় পরই তিনি আবারো অসুস্থ্ হয়ে পড়েন।
তারপর একদিন তিনি আয়েশার (রা) ঘরে ইন্তেকাল করেন। দিনটি ছিলো ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন। খবরটি শুনে তাঁর সাহাবীরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ এই বাস্তবতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তারা ভেবেই পাচ্ছিলেন না, আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল কীভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন! মহানবীর (সা) সবচেয়ে ঘনিষ্ট সাথী আবু বকর (রা) তখন তাঁদেরকে শান্ত করেন। তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, আর দশজনের মতো মরনশীল মানুষের বাইরে মোহাম্মদ (সা) কখনোই নিজের ব্যাপারে ভিন্ন কিছু দাবি করেননি। আর মোহাম্মদের (সা) নয়, ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর– মহানবীর (সা) এই শিক্ষাও তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দেন। মসজিদে নববীর পাশেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। তাঁর মুখমণ্ডলকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। আজো মুসলমানরা মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রথাটি মেনে চলেন।
শেষ কথা
পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে মোহাম্মদের (সা) বাণী গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এর বিস্তৃতি ছিলো প্রাচ্যের চায়না-ইন্ডিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং পাশ্চাত্যের স্পেন-ফ্রান্স পর্যন্ত। কিন্তু নানান কারণে তাঁর শান্তিপূর্ণ জিহাদের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত বিচ্যুতির শিকার হয়। মোহাম্মদের (সা) মৃত্যুর এক প্রজন্মের মধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ট অনুসারী ও পরিবারের সদস্যরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাঁরা প্রকাশ্য ও রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই দ্বন্দ্ব মুসলমানদের মধ্যে গভীর ক্ষত তৈরি করে, যা আজো মুসলিম বিশ্বে শিয়া-সুন্নী বিভাজন হিসেবে রয়ে গেছে।
কিন্তু মোহাম্মদের (সা) বাণী আগে কখনোই এখনকার মতো এ ধরনের হুমকিতে পড়েনি। অনেক মুসলমান পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সামরিক প্রাধান্যকে নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে এবং তারা এর বিরোধিতা করে। অন্যদিকে, অনেক পাশ্চাত্যবাসীর কাছেও ইসলাম হলো দুনিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সহিংস ও অসহিষ্ণু ধর্ম। তর্কের খাতিরে তা ধরে নিলেও স্বয়ং মোহাম্মদকে (সা) এর জন্য কীভাবে দায়ী করা যায়?
মোহাম্মদ (সা) তিনটি জিনিস রেখে গেছেন– আল্লাহর উপর বিশ্বাস, তাঁর নিজের জীবনকর্ম এবং সর্বোপরি আল কোরআন।
কিন্তু অনেকে শুধু তাঁর জীবনের সেটুকুই তুলে ধরে, যেটুকু তার নিজের অবস্থানের পক্ষে যায়। ফলে তাঁর জীবনের বাকি অধ্যায় অজানাই থেকে যায়। কিন্তু আমরা তাঁর জীবনকে সামগ্রিকভাবে যাচাই করলে দেখবো, আরব বিশ্বকে তিনি চমৎকার একটি অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েও প্রতিরোধের পরিবর্তে তিনি তা সহ্য করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও, সম্ভব হলেই যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়েছেন। শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিলো। সেই বিজয়ের পর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে বিরোধ মীমাংসার পথই বেছে নিয়েছিলেন।
সর্বশেষ, বিদায় হজের ভাষণে মোহাম্মদ (সা) আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলো দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান। এই সার্বজনীন বক্তব্য সপ্তম শতকের আরবের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, একইভাবে বর্তমান সময়ের জন্যও প্রাসঙ্গিক। মোহাম্মদের (সা) জীবনের এই শিক্ষাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়।
[স্ক্রিপ্ট: জিয়াউদ্দীন সরদার, অনুবাদ: মাসউদুল আলম]
নোট:
[1] ইসলাম গ্রহণের জন্য দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের বিষয়টি প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।
[2] প্রকৃতপক্ষে ‘সালাম’ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এরমধ্যে একটি অর্থ হলো শান্তি।
[3] এ তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ, রাসূল (সা) কর্তৃক এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে –অনুবাদক।