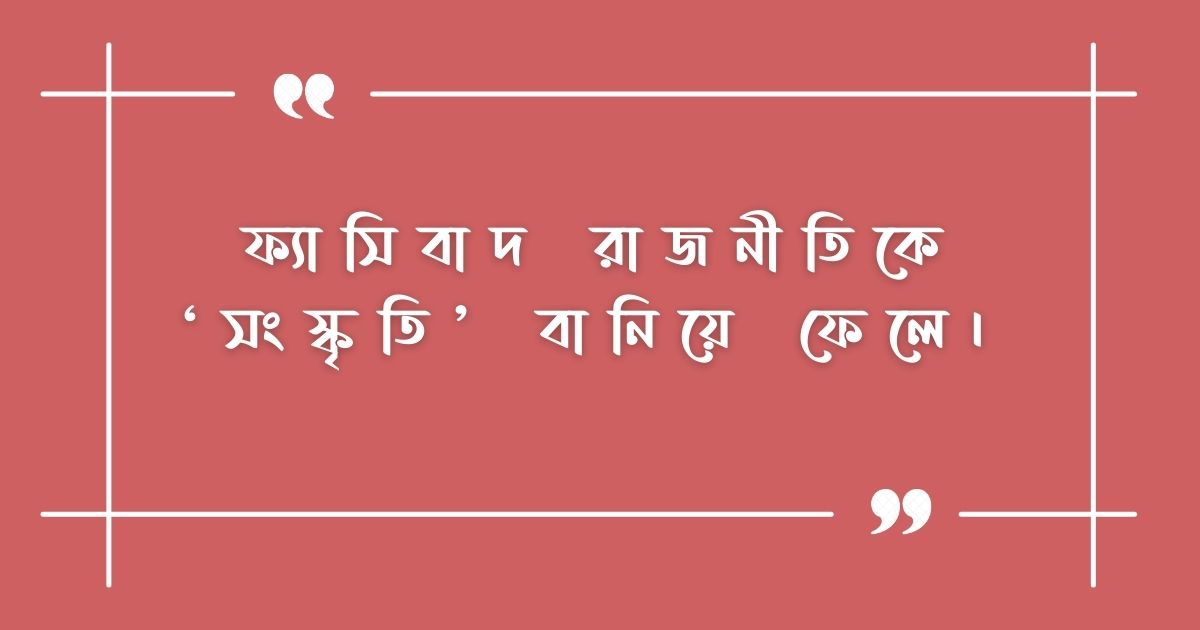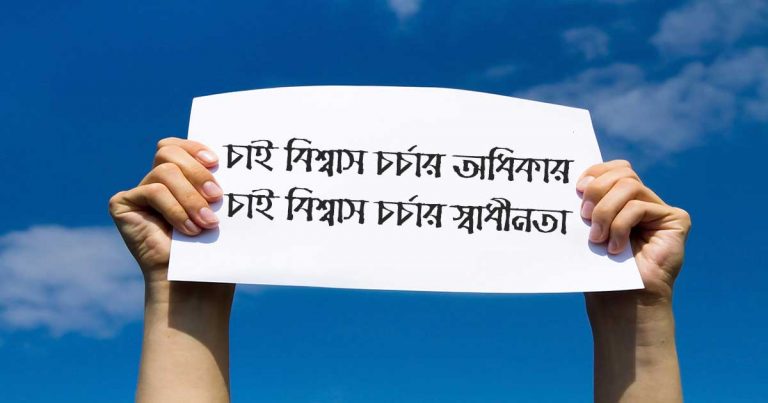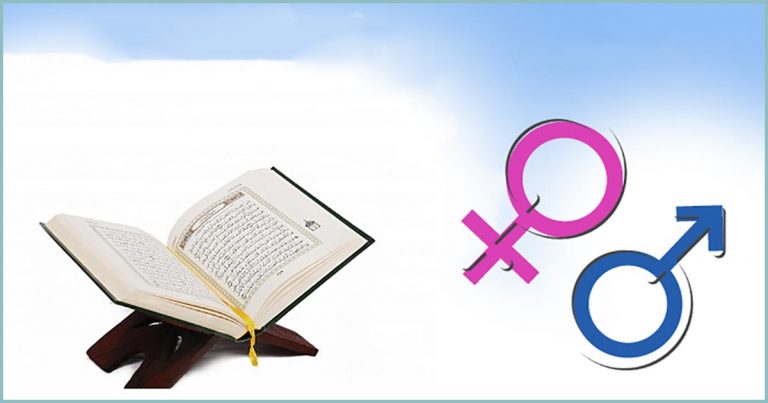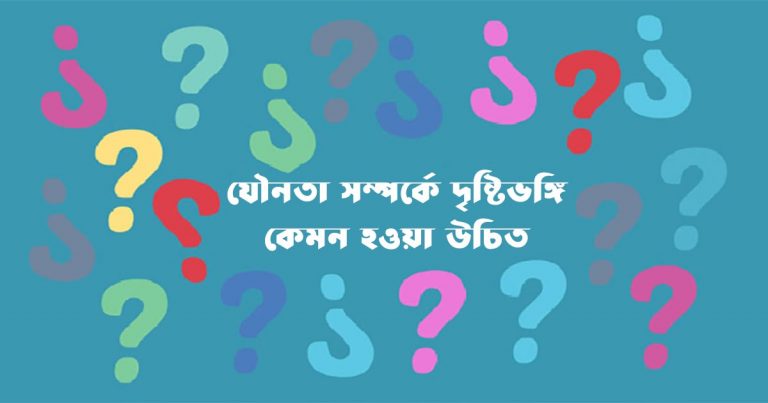হেজেমনি বা ভাবাধিপত্য: পরিচয় ও প্রকরণ
ফ্যাসিবাদ প্রায়শ নিজেকে শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হাজির করে। সেই শিল্পকেই পৃষ্ঠপোষকতা করে যা ফ্যাসিবাদী শাসকদের পক্ষে নিরবে সম্মতি যোগায়।
সাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চারুকলা বা ছায়ানটে লোকজন যতটা বলবে, গুম-খুন-হত্যা নিয়ে ততটা বলবে না। ফ্যাসিবাদী শাসন আলগোছে শিল্পের বিষয়বস্তুও নির্ধারণ করে দেয়, এবং এই নির্ধারণ সাধারণত কোনো কোয়ার্সিভ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয় না, বরং একধরনের কনসেন্টের মধ্য দিয়ে হয়।
“Ideology in effect”-কে হেজেমনি বলে। এটা সাধারণত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এটা একধরনের “Invisible system of transmission”। আইডিওলজি সাধারণত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বা লিগাল এপারেটাস দিয়ে সরাসরি ইম্পোজ করা যায় না। বন্দুকের নল বা জেলে পুরার ভয় না দেখিয়ে আইডিওলজিকে পুশ করার ব্যাপারটাই হেজেমনি বা ভাবাধিপত্য। আলথুসার দাবি করেন, সিভিল অর্গানাইজেশন, সিভিল সোসাইটি ও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আইডিওলজি বিস্তার লাভ করে। আওয়ামী আমলে বিএনপি বা জামায়াত করা কোনো লেখক বা শিল্পীকে বিটিভিতে ডাকা হবে না বা বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হবে না—এটা প্রায় সবাই মেনেই নিয়েছিল, এটাকে আর বিশেষ কিছু মনে করা হচ্ছিলো না। (ফ্যাসিবাদ যেকোনো অন্যায়কে নর্মালাইজ করে ফেলে।) হেজেমনিক কালচারাল ব্যবস্থায় লোকজন একটা blissful ignorance-এর মধ্যে থাকে।
কোনো মতাদর্শ বা কোনো কিছু যখন হেজেমনিক হয়, তখন সে তার বিশ্বাস, চিন্তা বা অনুমানকে এমনভাবে ট্রান্সমিট করে যেন এটাকে হেজেমনিক হিসেবে দেখা বা বোঝা না যায়। ধরা যাক, সেকুলার চিন্তার হেজেমনি বুঝার একটা উপায় হলো কাউকে সাহিত্যিক বলা হচ্ছে, কাউকে ইসলামি সাহিত্যিক বলা হচ্ছে, কোনোটাকে বলা হচ্ছে দর্শন, আর কোনোটা ইসলামী দর্শন। ইসলাম যদি হেজেমনিক হতো, তাহলে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য “ইসলামী” শব্দটা লিখতে হতো না।
আবার ধরেন, এলিটিজমের একটা হেজেমনিক ধারণা আছে। যেমন, প্রথম আলো বা ডেইলি স্টারে লেখা ছাপা হলে লোকজন নিজেদেরকে অত্যন্ত পশ মনে করে, এটা যেন এক প্রকার আভিজাত্য। আবার ধরেন, শামসুর রাহমানকে প্রধান কবি বলা হতো। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কাদের কাছে প্রধান কবি? প্রধানত আর্বান এডুকেইটেড মিডলক্লাসের কবি। নিম্নবিত্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন মানুষের কাছে শামসুর রাহমান মোটেই প্রধান কবি নন। হয়তো দেখা যাবে, বিজয় সরকার তাদের কাছে প্রধান কবি বা কবিয়াল। এই যে নিজেদেরকেই ‘সকল’ হিসেবে উপস্থাপন করা ও নিজেদের পছন্দকেই সকলের পছন্দ হিসেবে হাজির করতে পারা, এটা একই সাথে একটা হেজেমনিক পরিস্থিতির ফলাফল ও কারণ।
ফ্যাসিবাদ রাজনীতিকে ‘সংস্কৃতি’ বানিয়ে ফেলে।
সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, মঙ্গল শোভাযাত্রার বিশেষ রাজনীতি আমাদের সামনে সংস্কৃতি আকারে হাজির করা হয়। আওয়ামী ফ্যাসিবাদ কালচারাল ইন্ডাস্ট্রিকে মতাদর্শিক স্থিতির হাতিয়ার বানিয়েছিল। ফ্যাসিনাকে (ফ্যাসিস্ট+হাসিনা) ঘিরে চঞ্চল চৌধুরী, নুসরাত ফারিয়ারা “তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কী” গেয়ে যে মনোরঞ্জন করেছিল, সেটি কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যবহার। ওল্টার বেঞ্জামিন ফ্যাসিবাদকে “aestheticised politics” বলেছিলেন। আওয়ামী ফ্যাসিবাদে পদ্মাব্রিজের দৈর্ঘ্য ও বিশালতা, মেট্রোরেলের গতিময়তা ইত্যাদি উন্নয়নের বিভ্রম (developmental delusion) দিয়ে এস্থেটিসাইজড পলিটিক্সও করা হয়েছে। একধরনের এনচ্যান্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। ‘উন্নতি সুন্দর, গণতন্ত্র অসুন্দর’, ‘বিরাজনীতি শৃঙ্খলা, আর রাজনীতি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা’—এইসব বোধ চাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটাকে “Victory of the spectacle over public sphere”-ও বলা যাবে, যা ফ্যাসিবাদকে চাড়িয়ে দিতে কাজ করে।
ইসরাফিল আলম সম্পাদিত ‘শেখ হাসিনাকে নিবেদিত ১০০ কবির কবিতা’র মধ্যে বাংলাদেশের কাব্য জগতের এক বিপুল অংশের উপস্থিতি লক্ষ করি৷ আহমদ রেজা সম্পাদিত ও আনিস মোহাম্মদ অনূদিত ‘Peace and Harmony: seventy one poems dedicated to Sheikh Hasina’ সংকলনেও বেশ রথি-মহারথিদেরকে হাজির হতে দেখি। ক্ষমতার সাথে এসব সংস্কৃতিসেবিদের লিঁয়াজো ক্ষমতাকে সংহত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তিপূজার চরম পরাকাষ্ঠা দেখা যায় এই সংকলন দুটিতে। ফ্যাসিবাদের সাংস্কৃতিক জমিন এই কবিরা, এই সম্পাদকেরা, এবং এখানে যারা জায়গা পায় নাই, কিন্তু অন্যত্র নানা সুরতে ছিল ও আছে, নির্মাণ করেছে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাকশাল হচ্ছে আওয়ামী কালচারাল সিন্ডিকেটের অজ্ঞান বা আনকনশাস!
ফ্যাসিবাদ যেমন একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ, আবার এটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত প্রবণতা বা মানসিকতাও। ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক শক্তি যেমন, তেমন সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিও; এবং এরা একে অপরকে পুষ্ট করে।
প্রশ্ন হতে পারে, কোনো সমাজে সব সময়েই কোনো না কোনো আদর্শ বা মতাদর্শ আধিপত্য লাভ করে। তাহলে সমাজের ডমিনেন্ট আদর্শমাত্রকেই কি আমরা হেজিমনি বলব? হেজিমনি কথাটা কি নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে?
এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সমাজের ডমিন্যান্ট আদর্শ, যেটা আলোগোছে প্রায় সবাই মেনে নেয়, সেটাই হেজেমনি। হেজেমনি নন-কোয়ার্সিভ এবং কনসেনট-ভিত্তিক হয়। হেজেমনি নিজেকেই “Order of things” করে তোলে। আর, হেজেমনি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রকমই হতে পারে। তবে, যেকোনো মতাদর্শকে মনে-মননে গেঁথে দিতে হলে তা-কে হেজেমনিক হতেই হয়৷ হেজেমনি তৈরিতে আলথুসার কথিত আইডিওলজিকাল স্টেইট এপারেটাসসমূহ দরকার হয়৷ এটা “ভালো-খারাপ” সব মতাদর্শই ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লীগের শাসনকে আমাদের নিয়তি হিসেবেই প্রায় মেনে নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম কমপক্ষে ২০৪১ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় থাকবে। সব কিছুকে তারা তাদের গ্রিপে নিয়ে নিয়েছিল, পুলিশ-আর্মি-প্রশাসন-মিডিয়া সবাইকে। আওয়ামী লীগের শাসনকে একেবারেই নিয়তি নির্ধারিত ও কপালের ফের মনে হয়েছিল, যেনো এটার কবল থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় নেই। “বিকল্প কী, বিকল্প নাই, বিকল্প দেখান” ইত্যাদি উসকে দেওয়া প্রসঙ্গগুলোও এমন ভাবিয়েছিল লোকেদের। এই যে বাধ্য হয়ে, নিরুপায় হয়ে মেনে নেওয়া, এবং মেনে যে নিয়েছি এটাও প্রায় ভুলতে থাকা, এটাই হেজেমনি। আর, বল বা Coercion দিয়ে শাসন করলে তাকে বলে ডোমিনেন্স। কোনো শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এই দুইটাই লাগে।